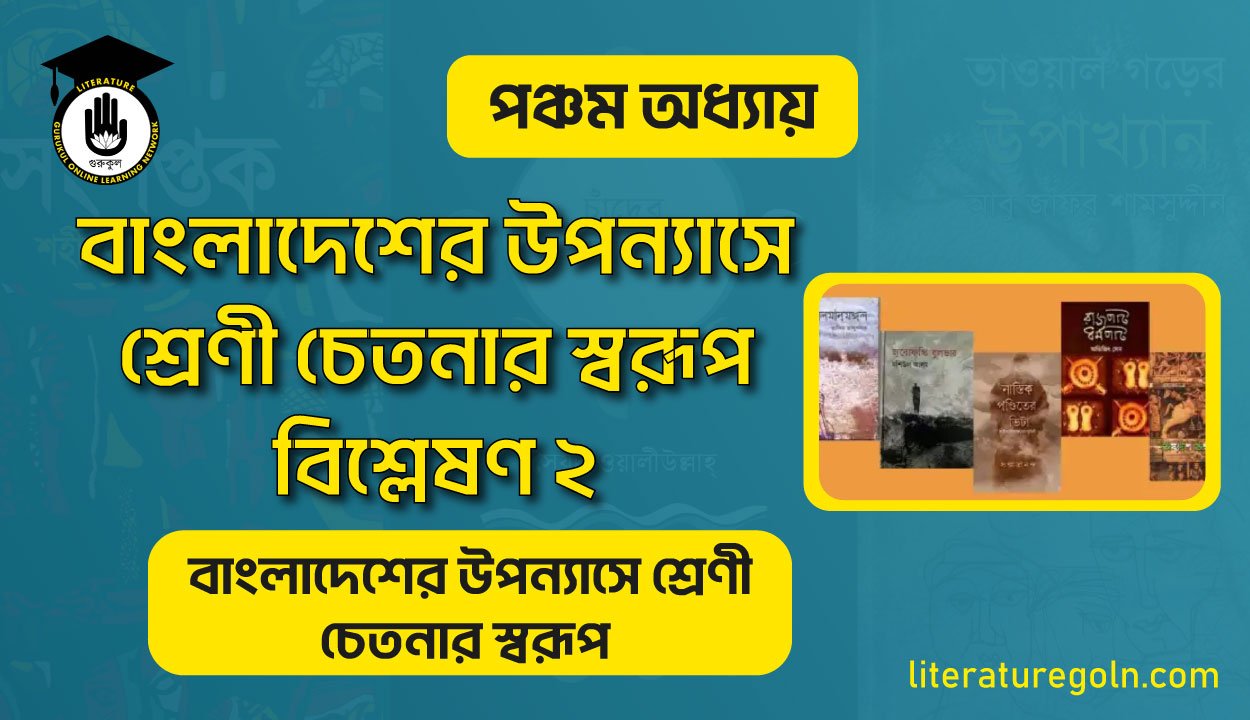আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়ঃ বাংলাদেশের উপন্যাসে শ্রেণী চেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণ ২। যা বাংলাদেশের উপন্যাসে শ্রেণী চেতনার স্বরূপ এর অন্তর্গত।

বাংলাদেশের উপন্যাসে শ্রেণী চেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণ ২
সরদার জয়েন উদ্দীন(১৯১৮-১৯৮৬)
চল্লিশের দশক থেকে ষাটের দশক বিভাগ পূর্ববর্তীকাল থেকে বিভাগ পরবর্তীকাল এ দু’দশক কালসীমায় গ্রামবাংলার জীবনভাষ্য নির্মাণ করেছেন সরদার জয়েন উদ্দীন। ১৯৪৭-৭১ কালপর্বে সরদার জয়েন উদ্দীনের দু’টি উপন্যাস ‘শ্রেণী চেতনা’ বিষয়কে প্রতিনিধিত্ব করে। উপন্যাস দু’টি হল- ‘আদিগন্ত’ (১৯৫৯) এবং ‘অনেক সূর্যের আশা’ (১৯৬৭)।
দেশ বিভাগ পরবর্তী বাংলার গ্রামীণ জীবননির্ভর ‘আদিগন্ত’ উপন্যাসটি সমকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটে সমাজিক বাস্তবতার এক নিরাভরণ শিল্পরূপ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আক্রান্ত ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাক্ষত সময় পরিসর, এ উপন্যাসের কাহিনীকে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের গতিশীল পটভূমিকায় বিন্যস্ত করেছে।
আলোচ্য উপন্যাসে শ্রেণী চেতনার পরিচয় থাকলেও শ্রেণী সংগ্রামের মীমাংসিত উত্তরণ এতে অনুপস্থিত। উপন্যাসটিতে লেখক সমাজদ্বন্দ্ব ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের বিচিত্র রূপ অংকনের পাশাপাশি ব্যক্তি মানুষের প্রেম, দুঃখভোগ ও প্রাপ্তির প্রতিও ঐকান্তিকতা প্রদর্শন করেছেন। ফলে শোষক ও শোষিতের চরিত্রবৈশিষ্ট্য নিরূপিত হলেও আলোচ্য উপন্যাসে শ্রেণী চেতনায় সমৃদ্ধ মীমাংসায় উপনীত হতে ব্যর্থ হয়েছেন সরদার জয়েন উদ্দীন।
পদ্মা তীরবর্তী গ্রাম নবীনগর ‘আদিগন্ত’ উপন্যাসের ঘটনাস্থল। প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রামরত মানব- মানবীরা ব্যক্তিক ও সামষ্টিক অস্তিত্বের প্রশ্নে সংগ্রামশীল। কিন্তু যুদ্ধ ও দাঙ্গার ভয়াবহ রূপ এই জনগোষ্ঠীকে অস্তিত্বের প্রান্তিক পরিস্থিতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। যুদ্ধ দাঙ্গার সেই রূপ ঔপন্যাসিক উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র স্কুল শিক্ষক ছামাদ মণ্ডলের ভাষ্যে তুলে ধরেছেন-
“সমাজ জীবনে যুদ্ধের পর থেকে যে অর্থনৈতিক দুষ্ট কীট প্রবেশ করেছে, তাকে যেন আর ওষুধ দিয়ে সারানো যাবে না। এ যে কী অনাসৃষ্টি, তা পাড়াগাঁয়ে ক’দিন বাস না করলে বুঝবার উপায় নাই। শোষণে, শাসনে আর দুর্নীতির অমানুষিক চাপে সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ন্যুব্জ হয়ে পড়েছে।
ছামাদ মণ্ডল যাকে ‘অর্থনৈতিক দুষ্ট কাঁটা বলছে, তা আসলে পদ্মা তীরবর্তী নবীনগর, কামারহাট প্রভৃতি গ্রামের বিপুল সংখ্যক মানুষের অর্থনৈতিক দুর্দশা। ‘মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ন্যুব্জ’ হওয়া গ্রামের এসব মানুষ মূলত কৃষিজীবী। আবার এমনও ব্যক্তি গ্রামে দেখা যায়, যাদের প্রচণ্ড ক্ষমতার কাছে এসব মানুষের জীবন তুচ্ছ। যুদ্ধ, দাঙ্গা, রাজনৈতিক আলোড়নের পথ ধরে গ্রাম সমাজে যে অনাসৃষ্টির সূচনা, তা সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষিজীবী মানুষের জীবনকে দুঃসহ করে তোলে; ক্ষমতাবান শ্রেণীর অবস্থান থেকে যায় অপরিবর্তিত। উপন্যাসের কালগত পটভূমি মোটামুটিভাবে পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিকে ।
উপন্যাসে কাহিনীর আবর্তন তিনটি পরিবারকে ঘিরে- মীর, মণ্ডল ও বৈরাগী পরিবার। ভূসম্পত্তির মালিকানার | মীর-পরিবার প্রতিষ্ঠিত গ্রাম-সমাজের সর্বোচ্চ স্থানে; মণ্ডল পরিবার কুসিদঞ্জীবী-ব্যবসায়ী সূত্রে শ্রেণী এবং বৈরাগীদের অবলম্বন ভিক্ষাবৃত্তি। মীর-পরিবারের প্রধান পুরুষ মীর খোরশেদ আলী পীর ‘দুই দুইবার মক্কা শরীফ’ ঘুরে এসেছে। ‘দোয়া-দরূদ আর কলমা-নামাজ’ এসব তার ধর্মপ্রবণতার লক্ষণ।
‘দেশের লোকের চাহিদা’য় সে লাভ করে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের পদ এবং গ্রামের সালিস- বিচারের ভার তার ওপর ন্যস্ত। ক্ষমতাসীন মীর খোরশেদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা মেনে চলতে হয় সবাইকে। এর ব্যত্যয় হলে সাধারণ মানুষের ওপর নেমে আসে বিপর্যয়। জোনাব মণ্ডলের ছেলে গান-পাগল মেহের বয়াতীর নরোত্তম বৈরাগীর বাড়ি যাতায়াত মীরের কাছে অত্যন্ত কলংকজনক ব্যাপার, সেটা হয়ে যায় “কওমের বদনাম’।

নরোত্তমের কন্যা সরলার সঙ্গে মেহেরের নাম জড়িয়ে সে মেহেরকে হেয় করার চেষ্টা করে, যাতে গ্রামের লোক তাকে দুশ্চরিত্র বলে ধরে নেয়। মেহেরের গান-বাজনাকে ধর্মবিরোধী বলে অভিহিত করে তার গর্হিত কাজের প্রায়শ্চিত্ত করার নির্দেশ জারি করে মীর খোরশেদ। প্রায়শ্চিত্তের উপায় কিছু অর্থ জরিমানা এবং ‘আল্লার নিকট… কান্নাকাটি। মীরের মুখে উচ্চারিত ‘হাদিসের কথা’, শরা- শরিয়ত-ফতোয়া’র প্রতিবাদ করার সাহস নেই গ্রামের বিত্তহীন ক্ষমতাশূন্য মানুষের।
মীরের ধর্মকেই যে গ্রামবাসীদের ভয় তা নয়; থানা-পুলিশের সঙ্গে মীরের যোগসাজশকেও তারা ভীতির চোখে দেখে। থানা-পুলিশের প্রকৃত কাজ যা-ই থাকুক, সমাজের চোখে তাদের ভূমিকা নেতিবাচক
“দারোগা-পুলিশের কাছে মারামারি খুনাখুনির খবর বড় খুশির খবর, দুটো কাঁচা পয়সার খবর। ২২
“দারোগা বাবুরা ওদেরি কথায় কাম কাজ করে”- গ্রামের লোকদের ধারণা, থানা-পুলিশের কাজ সমাজের বিত্তবান ক্ষমতাবানদের স্বার্থ-সংরক্ষণ করা। লোকদের এ ধারণা যে অমূলক নয়, নবীনগর গ্রামের মেহের বয়াতীর মামলা থেকে সেটা স্পষ্ট। সরলার আকর্ষণ এবং সংগীতোন্মুখতা থেকে মেহেরকে নিবৃত্ত করতে না পেরে নারীলিঙ্গু মীর বেছে নেয় ষড়যন্ত্রের পথ।
মীরের অপবাদ থেকে বাঁচতে আত্মমর্যাদা-সচেতন নরোত্তম সরলার জন্য বিয়ের পাত্র ঠিক করে ভিন্ন এক গ্রামের কুন্তল বৈরাগীকে। কুন্তলকে খুন করিয়ে মেহেরকে মিথ্যে মামলার ফাঁদে জড়ায় মীর খোরশেদ। মীরের সাজানো মামলায় থানার দারোগা অর্থের লোভে ‘মামলা আসামী’দের খালাস দেয়; সাক্ষী-সাবুদ তৈরি করে মামলা সাজাবার উপায় বাতলে দেয় মীর খোরশেদকে।
এভাবেই শুধু মেহের বয়াতীর মামলাই নয়, নবীনগর গ্রামের আরো বহু অসহায় মানুষের দুর্গতির উল্লেখ পাওয়া যায়। আদালতে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে মামলার অন্যতম সাক্ষী কেরামতের কথায় সেই দুঃসহ অবস্থার চিত্র-
“এই তো হুজুর মেহের গেল মিছা খুনির দায়, ছবেদ শেখ হুজুর, বেচারা বড় গরিব আমার মতই, সে গেল বছর মিছা চুরির দায়ে জেলে গেছে। ২০
কিন্তু এ অবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও গ্রামের মানুষ নিরুপায়। ক্ষমতাবান শ্রেণীর অন্যায় আচরণকে মেনে নিয়েই তারা গ্রামে বসবাস করে। ষড়যন্ত্রকারী মীরের বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য দেয়ার প্রেরণা তাদের দেয়নি সামজ। তাদের কণ্ঠে ব্যর্থতার স্বীকারোক্তি-
না বাপু, ও পীর সাহেবের মতের বিরুদ্ধি কোর্টে গিয়া দাড়াতি পারবো না।”
আদালতে প্রবল জেরার মুখে কুন্তল হত্যা মামলার প্রধান সাক্ষী এবং হত্যাকারী কেরামতের সাক্ষ্যে উন্মোচিত হয় ষড়যন্ত্রকারী নীর খোরশেদের স্বরূপ। পাশাপাশি গ্রামের নিম্নবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি কেরামতের অবস্থায় প্রতিফলিত সংখ্যাগরিষ্ঠের অক্ষম জীবনের বেদনা-
“আমি নিজের ইচ্ছায় এসব করি নাই, যা কিছু করছি সব-ই ঐ প্রিসিডিন্ট সাহেবের হুকুমে। তা না করলি দারোগা-পুলিশের সাথে ওনার যা খাতির কথা নাই বার্তা নাই, অবাধ্য হইছ কি দিবি এক চুরির কেসে ফাঁসায়া। যাও খাটে আস ছয় মাস, বচ্ছর। কী করবো হুজুর, গরিব মানুষ, জেলের বাইরে থাকতি হলি ওনার হুকুম তালিম করতিই হবি।
এমনি করেই ‘আদিগন্ত’ উপন্যাসে দেখা যায়, মানুষের অস্তিত্ব সংকট ও সংঘাতের প্রতিক্রিয়ায় শোষক ও শোষিত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে জনগোষ্ঠী। ছামাদ পাণ্ডিত, মেহের, সরলা, শহরে বসবাসকারী আইনজীবী বাদশা মিয়া হাসান শোষিত জনগণের পক্ষ অবলম্বন করে।
অন্যদিকে ভণ্ডপীর, ইউনিয়ন পরিষদের প্রেসিডেন্ট মীর খোরশেদ আলী ও লম্পট দারোগা লক্ষর আলী তালুকদার অত্যাচারী শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। সারদা নরোত্তমের আশ্রয়ে লালিত পিতৃমাতৃহারা সরলার প্রতি রিরংসায় মীর খোরশেদ প্রেমিক মেহের থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করে। মিথ্যা খুনের মামলার আসামী করে মেহেরকে দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। আদালত কক্ষে বিচারকের এজলাসে মেহেরের প্রত্যয়দীপ্ত উচ্চারণ-
“ধর্মাবতার, কোনকিছু বলে এ শাস্তির প্রতিকার হয় না, যেদিন আমার মত লোকেরা জোট বাঁধবে, সেদিন-ই এর প্রতিশোধ হাড়-মাংস দিয়ে দিতে হবে।
মেহেরের প্রতি ছামাদের অনুপ্রেরণা-
“গানের কথায় মানুষকে শিক্ষা দিয়ে যাবি, মানুষকে মানুষের মত বাঁচতে শেখাবি। বিদ্যে বুদ্ধি হোক মানুষের চোখ মেলে চেয়ে দেখুক নিজের অবস্থা, তাহলেই সব হবে। …. নইলে দেশ জাগবে না।
মেহের এবং ছামাদের বক্তব্যে প্রচারিত গণমুখী চিন্তা নিঃসন্দেহে সমাজের নিম্নবিত্তের মানুষের প্রতি ঔপন্যাসিকের শ্রেণী চেতনার পরিচয় তুলে ধরে।
উপন্যাসের সমাপ্তিতে দেখা যায়, সদ্য কারামুক্ত ছামাদ পণ্ডিত ও আইনজীবী বাদশা মিয়ার সহায়তায় মেহের জেল জীবন থেকে মুক্তি লাভ করে। এবং এক রোমান্টিক মীমাংসায় উপন্যাসের সমগ্র শ্রেণীদ্বন্দ্ব মুখ থুবড়ে পড়ে। যদিও উপন্যাসের সর্বত্র শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও শ্রেণী চেতনা সক্রিয় ছিল। যেমন আইনজীবী বাদশা মিয়ার নাগরিক মনে শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে উচ্চারিত আশাবাদে সেই পরিচয় প্রতিফলিত।
“একথা ভুললে চলবে কেন যে, অনাচার-অত্যাচার যারা করে তারা একজাত; আমরা একজাত । এ অনাচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ, সেটা সত্য প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ। সে সত্য প্রতিষ্ঠিত হবেই।
কিন্তু ‘আদিগন্ত’ উপন্যাসে গ্রামীণ জীবনের শ্রেণীবৈষম্যের রূপায়ণ থাকলেও এতে শ্রেণীদ্বন্দ্বের স্বরূপ ঔপন্যাসিকের গভীর জীবনবোধের আশ্রয় লাভে ব্যর্থ হয়েছে। কেবল শোষক-শোষিতের দু’টি স্পষ্ট পক্ষ চিহ্নিতকরণ এবং কিছু কিছু বক্তব্য প্রচারণায় সীমাবদ্ধ থেকে গেছে লেখকের শ্রেণী চেতনা। আহমদ কবির যথার্থই লিখেছেন-
“সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর পক্ষপাতও সুস্পষ্ট, যদিও একথা সত্য, শ্রেণী-দ্বন্দ্বের স্বরূপ ও সমস্যা তাঁর রচনায় বুদ্ধিদীপ্ত যৌক্তিক বিশ্লেষণে ব্যাখ্যাত হয়নি। সমাজ-অসঙ্গতি ও বৈষম্যকে তিনি বিচার-বুদ্ধি দিয়ে পর্যালোচনাও করেননি। অনেকটা আবেগী ও রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি মানুষের শোষণ মুক্তির কামনা করেছেন। সে জন্য ধনী-দরিদ্রের দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত দরিদ্র জনতার জয় সূচিত হবে- এ ধরনের স্বপ্নিল ভাব-কল্পনায় তিনি ছিলেন মুক্তকণ্ঠ । ২৯
তা সত্ত্বেও বলা যায়, সরদার জয়েন উদ্দীনের সৃষ্ট চরিত্রগুলো সমাজের উচ্চবর্গীয়দের নিয়ন্ত্রিত বৃত্তে মলিন জীবনের মধ্যেও চেতনার উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত। নিম্ন স্তরের মানুষ হয়েও তারা দীর্ঘকালের শোষণ- বঞ্চনার বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়িয়েছে প্রসন্ন ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে।
সরদার জয়েন উদ্দীনের ‘অনেক সূর্যের আশা’ উপন্যাস জীবনের সুবৃহৎ আয়তন-কল্পনায় বিশিষ্ট। উত্তম পুরুষে রচিত এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের ভাববাদী জীবনচেতনার প্রতিফলন ঘটেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে শুরু করে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত এ উপন্যাসের কাহিনী বিস্তৃত।
উল্লিখিত সময়কালের অসংখ্য ঘটনা- বিশ্বযুদ্ধ, সামাজিক অবক্ষয়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশ বিভাগ, দেশ বিভাগ-উত্তর বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি কবি রহমতের স্মৃতিকথনের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। উপকরণ নির্বাচনের দিক থেকে সংশপ্তক উপন্যাসের সঙ্গে ‘অনেক সূর্যের আশা’-এর সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। কিন্তু শহীদুল্লা কায়সারের বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টি এবং সমাজ রূপান্তরের স্বরূপনির্দেশনা এ উপন্যাসে অনুপস্থিত।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-আক্রান্ত বাঙালি জীবনের সামগ্রিক ভাঙা-গাড়ার কাহিনীই এ উপন্যাসের প্রধান প্রবাহ। উপন্যাসে কাহিনীর উন্মোচন ঘটেছে দেশ বিভাগোত্তর ঢাকার পটভূমিকায়। স্বপ্নের ভূখণ্ড পাকিস্তান সৃষ্টির পরে পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম সমর্থক হায়াত বা টঙ্গী জুট মিলে শ্রমিক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ কালে পাকিস্তানি পুলিশের গুলিতে নিহত হয়।
অনেক সূর্যের প্রত্যাশায় লালিত ভূখণ্ডের এই ট্রাজিক স্বরূপ নির্দেশের মধ্য দিয়েই উপন্যাসের সূচনা। ‘ভূমিকা’য় ঔপন্যাসিক যে স্বীকারোক্তি প্রদান করেছেন, তাতে আত্মজৈবনিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে সমাজজিজ্ঞাসা ও শিল্পপ্রেরণার সমন্বয় ঘটেছে।
“ইউরোপীয় স্বার্থের দ্বন্দ্বে সৃষ্ট দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে’র লেলিহান অগ্নিশিখায় এশিয়ার অসংখ্য প্রাণ হয়েছিল খড়কুটোর মতো ভস্মীভূত এবং যুদ্ধ-সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকট মানবাত্মাকে নিক্ষেপ করেছিল চরম বিপর্যয়ের মুখে। এর ফলে এক মুঠো খাদ্যের জন্য মানুষ বিসর্জন দিয়েছিল তাদের সম্ভ্রম, নীতি-ধর্ম। সে-সব দিনের অনেক চাক্ষুস ঘটনা দেখবার দুর্ভাগ্য আমার হয়েছে;
সেগুলো আঘাত করেছে আমার মানসপটে হৃদয়ে। এ উপন্যাস সেসব মনোবেদনারই জীবন্ত চেতনা বা ভাষারূপ ।৩০
“ঔপন্যাসিকের এই আত্ম-অভিজ্ঞতা কবি রহমতের স্মৃতিকথনের মধ্যদিয়ে অনেক সূর্যের আশায় শব্দরূপ পেয়েছে। ঔপন্যাসিক বিস্তৃত ক্যানভাসে অংকন করেছেন ‘যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, মানুষের নৈতিক অধঃপতন, আর্থিক সংকট, মানুষের জীবন যুদ্ধের বহুভুজ চিত্র। ৩১
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় উপমহাদেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে দ্বিজাতিতত্ত্বের যে বিষবৃক্ষ রোপিত হয়, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তার বাস্তবায়ন ঘটে। বাঙালি মুসলমানদের আত্যন্তিক স্বপ্নকল্পনা ও বস্তুসম্পর্ক বিরহিত ভাবাবেগ পাকিস্তান আন্দোলনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। সাম্রাজ্যবাদ ও তার এ দেশীয় অনুচরদের সক্রিয় ষড়যন্ত্রও এ ক্ষেত্রে অনেকাংশে দায়ী।
সেই বিষবৃক্ষের বিষফল ফলতে শুরু করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই। হায়াত যার মতো শ্রেণীসচেতন রাজনৈতিক কর্মীও পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল অনেক সূর্যের প্রত্যাশায়। কিন্তু স্বশ্রেণীর অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা রাখায় নব্য-ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী পাকিস্তানি পুলিশের গুলিতে তার মর্মগ্রন মৃত্যু ঘটে। উপন্যাসের সূচনায় ঔপন্যাসিক এই স্বপ্নভঙ্গের ট্রাজেডিকে সুকৌশলে উপস্থাপন করেছেন।
ট্রাজিক বেদনার এই শূন্যতার অনুষঙ্গে অতীতের অসংখ্য চরিত্রের অনুপ্রবেশ ঘটেছে উপন্যাসে। কবি রহমত, হায়াত খাঁ, ছমির মিয়া, সাজাহান চৌধুরী, কবি নিজাম, কমলকুমার রায়, হেনার মা, লুসি সাইপ্রিন, মিস রডারিক, কাজী গিয়াসুদ্দিন, আবদুল হামিদ, ফজলুল করিম, পান্ডে জী, মি: গাঙ্গুলী, সুলতান মিয়া, জামরুল, ভীমরুল প্রমুখ চরিত্রের অস্তিত্ব জিজ্ঞাসা ও জীবনযন্ত্রণা যুদ্ধ-আক্রান্ত সময় ও সমাজের পটে উন্মোচিত হয়েছে।
ঘটনা ও ক্রিয়ার কার্যকারণ-শৃঙ্খলা সর্বত্র রক্ষিত না হলেও একটা বিপর্যস্ত কালের অস্তর-বাইরের সমগ্রতা বিধৃত হয়েছে এ উপন্যাসে। যুদ্ধকালীন কলকাতার বেকারত্ব, দুর্নীতি, মেসে দুর্বিসহ অনিকেত জীবন, দুর্ভিক্ষ ও হতাশায় বেকার যুবসম্প্রদায় এই অন্যায় যুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধা হয়। একমাত্র ডক-শ্রমিক হায়াত খা ছাড়া এই মানবতাবিরোধী সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষাকারী যুদ্ধের স্বরূপ অনুধাবনে অনেকেই ব্যর্থ হয়।
নৈতিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় ভবিষ্যৎ অন্ধ যুবসম্প্রদায়কে স্কুল ভোগের স্রোতে নিক্ষেপ করে। সমাজদেহ ও মানবদেহ হয় পক্ষাঘাত ও সিফিলিসের মত জটিল রোগে আক্রান্ত। অস্থির ও বিকারগ্রস্ত সমাজ পটভূমিতে ভালবাসা অন্তর্হিত হয়ে ভোগ লালসার কারসাজি’তে পরিণত হয়। ব্লাক মার্কেটের প্রসার অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকেও করে তোলে কতিপয় সুবিধাভোগী লুটেরা শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণভুক্ত। যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া আবহমান গ্রামজীবনের শান্ত রূপকেও বিশৃঙ্খল করে তোলে। খাদ্য ও জীবিকা সন্ধানী মানুষেরা শহরের রাজপথে মান-সম্ভ্রম-নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে সবদিক দিয়েই ছিন্নমূল হয়ে পড়ে।
যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তরকালের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ এ উপন্যাসে বিন্যস্ত হয়েছে। সুভাষ বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্মতৎপরতার ও ব্যর্থতা, জার্মান-জাপান-ইটালির ফ্যাসিস্ট শক্তির পতন, কংগ্রেস-মুসলিম লীগের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কর্মতৎপরতা, দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান ও ভারত ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি প্রসঙ্গ উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহকে বৈচিত্র্যময় ও গতিশীল করেছে। উপন্যাসের শেষে আমরা দেখবো :
“সুবেহ সাদিকের আলোয় আলোয় পূর্ব আকাশ আলোর বন্যায় নেয়ে উঠছে, ঝলমল করে রেঙে উঠছে দিগন্ত! ঐ ওখানে আলোর পারে সে দেশ- স্বপ্নের দেশ। যেখানে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই, নেই অভুক্ত জনমানব। গরিব-কাঙ্গাল, রাজা-জমিদার সব সেখানে সমান, সব একই মানুষ।
এভাবেই শোষণহীন শ্রেণী বৈষম্যমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার আশাবাদ ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে আলোচ্য উপন্যাসে শ্রেণী চেতনার সদর্থক ভূমিকার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।
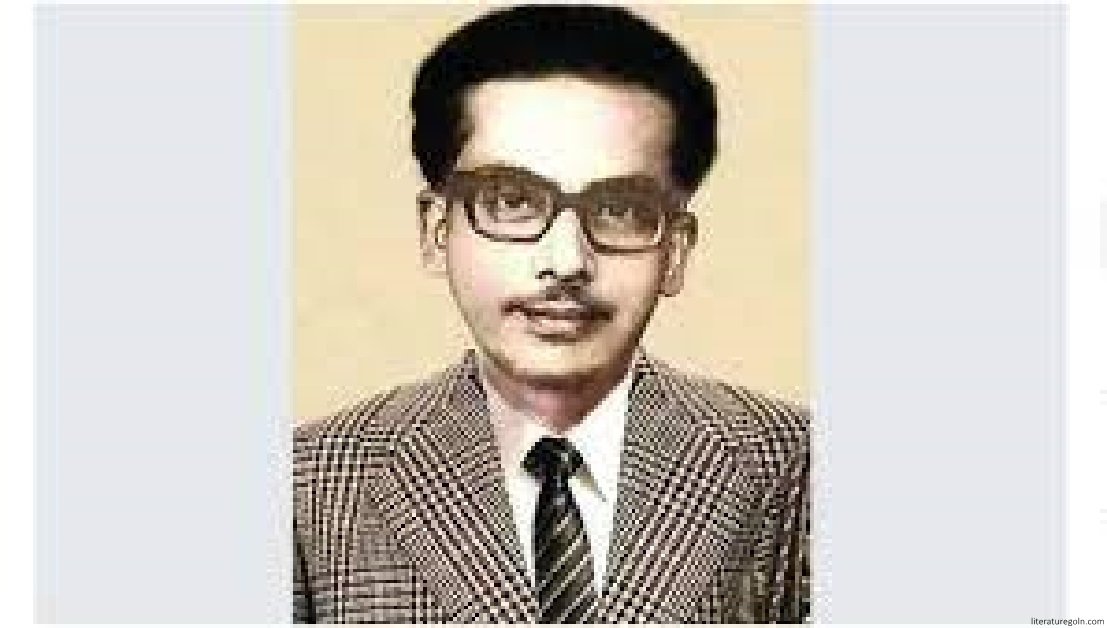
শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৬-১৯৭১)
বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারায় যে ক’জন ঔপন্যাসিক সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার বৈপ্লবিক অঙ্গীকারকে শিল্পরূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন, তাদের মধ্যে শহীদুল্লা কায়সার অন্যতম। আর এ কারণে প্রাসঙ্গিকভাবে শ্রেণী চেতনার পরিচয় তাঁর উপন্যাসে বর্তমান। ‘সারেং বৌ’ (১৯৬২) ও ‘সংশপ্তক’ (১৯৬৬)- এ দু’টি উপন্যাসের মধ্যে শ্রেণী চেতনা ও শ্রেণী সংগ্রামের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়।
‘সারেং বৌ’ (১৯৬২) রাষ্ট্রীয়-সামাজিক আলোড়ন থেকে দূরে এক নিভৃত গ্রামে শোষকশ্রেণীর নিপীড়ন- নির্যাতনের মধ্যে সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার কাহিনী। উপন্যাসে সমুদ্র উপকূলীয় গ্রামের জীবনযাত্রা স্থান পেলেও বৃহত্তর অর্থে তা পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ জীবনেরই মর্মকথা। ‘সংশপ্তক’-এ চিত্রিত ঔপনিবেশিককালে লেকু, কসির প্রভৃতি নিম্নবিত্ত মানুষ আবাসস্থল আম ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে জীবিকার খোঁজে! সেই অন্বেষণ থেমে পড়েনি; স্বাধীন দেশেও তা অব্যাহত।
‘সারেং বৌ’ এ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের উপকূলীয় গ্রামের কদম তেমনি এক যুবক। জীবিকার সংগ্রামে থাকে শুধু গ্রাম নয়, দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয় বিদেশে। কিন্তু কদমের জীবন-সংগ্রাম মূল বিষয় নয় উপন্যাসে। গ্রাম ছেড়ে কদমের বেরিয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে গ্রামেই সূচিত হয় আরেক জীবনের সংগ্রাম। বিদেশে কদমের দীর্ঘ কারাবাসজনিত অনুপস্থিতিতে কদমের স্ত্রী নবিতুনের ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোবার প্রয়োজন পড়ে জীবিকার তাগিদে।
অন্ত- ঃপুর থেকে বাইরে বেরিয়েই নবিতুন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ে এক কঠিন বাস্তবতার সঙ্গে। নবিতুনের ঘর- বাইরে দূরত্ব আক্ষরিক অর্থে কিছু নয়। কিন্তু রক্ষণশীল মুসলিম সমাজে তার নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা বহন করে বিরাট তাৎপর্য। জীবিকার সন্ধানে বাইরে বেরিয়েই সে সমাজের শোষকশ্রেণীর মানুষগুলোর প্রকৃত চেহারা কাছ থেকে দেখতে পেল। নবিতুনের বাইরে বেরোনোর আগেও গ্রাম-সমাজে শোষণ ছিল, কিন্তু তার সঙ্গে নবিতুনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার যোগ ছিল না।
উপকূলীয় জীবনে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে লড়াই করে টিকে থাকা সহায়-সম্বলহীন মানুষের জন্য নিদারুণ কষ্টকর। ঝড়-সাইক্লোন-বন্যার চাইতেও যে ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে মানুষ, নিজের অস্তিত্বের সংগ্রামশীলতা দিয়ে সেটা মর্মে মর্মে অনুভব করেছে নবিতুন। নবিতুনের অসহায়ত্বের মূল কারণ বামনছড়ি গ্রামের উঠতি ধনিক শ্রেণীর বিকৃত প্রতিচ্ছবি লুন্দর শেখ। তার ষড়যন্ত্রেই স্বামী প্রদত্ত টাকা ও চিঠি থেকে বঞ্চিত হয় নবিতুন। ফলে আরোপিত দারিদ্র্য নবিতুনের অস্তিত্বকে সীমাহীন অনিশ্চয়তায় নিক্ষেপ করে।
স্বামীর অনুপস্থিতিতে নবিতুনের অসহায়তার কথা দুর্বৃত্ত লুন্দর শেখ সামান্যতম বিবেচনায় আনেনি। নিষ্ঠুরতা-হিংস্রতার প্রতিমূর্তি জমিদার লুন্দরের কাছে নবিতুন অতি তুচ্ছ বস্তুর ন্যায়। নগদ অর্থ, সম্পত্তি, সংসারের আরাম-আয়েশ ইত্যাদি নানা প্রলোভনের বিনিময়ে তাকে করতলগত করতে চেয়েছে সে।
গ্রাম্য রমণী নবিতুনের করুণ কাহিনীর মধ্যে পূর্ববঙ্গের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনের বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটেছে, যারা সমস্ত প্রত্যাশা-স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার তৎপরতায় অহর্নিশ ব্যস্ত, যে সমাজে মানবিকতার বোধ হারিয়ে ক্ষমতাদর্পী মানুষ ক্রমশ ‘জানোয়ার’ হয়ে ওঠে; সেখানে প্রয়োজন প্রতিরোধ-চেতনার।
অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় থেকেও নবিতুন সেই কাজটাই করে গেছে শেষ পর্যন্ত। সে লুন্দরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। কন্যা আকৃকি’র মারফত পাঠানো লুন্দরের টাকা ছুঁড়ে দিয়ে এসেছে তার সামনে। নির্জনে ধর্ষণোদ্যত লুন্দরকে প্রতিরোধ করেছে শারীরিক শক্তি দিয়ে।
উপন্যাসের শেষে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদে চরাচরব্যাপী শূন্যতার প্রেক্ষাপটেও ঔপন্যাসিক সম্ভাবনার উৎস খুঁজে পান নবিতুনের মধ্যেই। ক্ষুৎপিপাসাকাতর মুমূর্ষু কদমকে সে বাঁচিয়ে তোলে অপূর্ব প্রাণের স্পর্শে। নবিতুনের অজেয় প্রাণশক্তি তাকে অন্তিম পর্যন্ত উজ্জীবিত করে রাখে। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের শ্রেণী নিপীড়ন, শোষণ, বঞ্চনা আর দারিদ্র্য পরতের পর পরত উন্মোচিত হয়েছে নবিতুনকে ঘিরে। সাধারণ গ্রাম্য রমণী নবীতুনই শেষ পর্যন্ত ঔপন্যাসিকের শ্রেণীসচেতন আশাবাদী জীবন-দর্শনের প্রেরণা। সমস্ত বিপর্যয়ের ভেতরেও সে বেঁচে থাকে জীবনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য।
‘সারেং বৌ’ উপন্যাসে প্রতিফলিত শ্ৰেণীচেতনা সংগঠিত শ্রেণী সংগ্রামে রূপান্তরিত না হলেও নবিতুন চরিত্রের অজেয় সংগ্রামশীলতার মধ্য দিয়ে শ্রেণী চেতনার আশাবাদী প্রত্যয়কে জাগিয়ে তোলে। আসলে যে প্রাণশক্তি গ্রাম্য সমাজে অবলা বলে কথিত নারীর মধ্যে দুর্মর হয়ে থাকতে পারে, তা সমাজের বিপুলসংখ্যক শোষিত মানুষের মধ্যেও থাকা সম্ভব।
‘নবিতুন’ সেই শোষিত মানুষদেরই একজন। কিন্তু লুন্দর শেখের মত নিপীড়কদের সঙ্গে লড়বার পক্ষে একা নবিতুন কিংবা কদম-নবিতুন একসঙ্গেও যথেষ্ট নয়। সমগ্র জনগোষ্ঠীর ঐক্যবদ্ধতার ফলেই তা সম্ভব হতে পারে। শ্রেণী সংগ্রামের সেই সম্ভাবনা সম্পর্কে কোন প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত না থাকলেও সারেং পরিবারের এক রমণীর জীবনযুদ্ধে যোদ্ধা হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে এ উপন্যাসে শ্ৰেণীচেতনার পরিচয় প্রতিফলিত হয়েছে।
শহীদুল্লা কায়সারের অপর উপন্যাস ‘সংশপ্তক’ (১৯৬৫)। শ্ৰেণীচেতনাপুষ্ট সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার বৈপ্লবিক অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে ‘সংশপ্তক’ উপন্যাসে। জীবনাদর্শ ও শিল্প নির্মিতি উভয় মানদণ্ডেই ‘সংশপ্তক’ বাংলা উপন্যাসের ধারায় এক অসামান্য সংযোজন।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তরকাল থেকে শুরু করে বিভগোত্তর কাল পর্যন্ত প্রায় এক যুগের বাঙালির জীবনসত্য এ উপন্যাসে বিন্যস্ত হয়েছে। জাতিসত্তার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের মুক্তিচেতনা ঔপন্যাসিকের জীবনাদর্শের মৌল প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। ১৯৩৮-১৯৫১ সময়পটে বিধৃত কাহিনীর মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হয়েছে এক যুগান্তরের ইতিকথা।
বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানকল্পে উপমহাদেশে যে মুক্তিসংগ্রাম চলছিল, তার দ্বন্দ্ব্বাত্মক গতিধারায় সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার জটিল প্রশ্নের উদ্ভব, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধাবসান ও কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশ বিভাগের পর মুক্তিসংগ্রামের পালাবদল এবং বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সূচনা— এই কয়েকটি পর্বের পটভূমিতে বাংলাদেশের দু’টি গ্রামের চরিত-কথা ‘সংশপ্তক’ উপন্যাসে উন্মোচিত হয়েছে।
‘সংশপ্তক’ উপন্যাসে কলকাতা-ঢাকার নাগরিক পরিবেশের এবং বাকুলিয়া, তালতলি নামক পারস্পর সংলগ্ন দু’টি গ্রামের বাস্তব চিত্রের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক প্রতিবেশটাকেই সামনে আনা হয়েছে। তবে নগরজীবন অপেক্ষা গ্রাম্যজীবনের বাস্তবতা রূপায়ণে লেখক আলোচ্য উপন্যাসে অধিকতর সফল হয়েছেন। জাহেদ, রাবু মালু, লেকু, হুরমতি প্রমুখ চরিত্র গ্রাম ও নগরজীবনের যোগসূত্র গড়ে তুলেছে।
হিন্দুপ্রধান তালতলি গ্রামে আধুনিক শিক্ষার প্রসার লক্ষ করা যায়। ব্যবসা-বাণিজ্য, সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রেও তালতলি গ্রাম অগ্রসর। অপরদিকে, পরাধীন ভারতবর্ষে প্রবল পরাক্রমশালী সামন্ত জমিদার শ্রেণী কর্তৃক শাসিত বাকুলিয়া গ্রাম। এই গ্রামের কাহিনীকে আশ্রয় করে প্রায় দেড় যুগের পরিসরে পূর্ববঙ্গের গ্রাম সমাজের ক্রমবিবর্তনের চিত্র আলোচ্য উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। বাকুলিয়া গ্রামে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দেড়শ’ বছর পরেও বৃটিশ সৃষ্ট জমিদার-শ্রেণীর উত্তরসূরীরাই সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী।
গ্রাম-সমাজে প্রচলিত ‘পঞ্চায়েৎ’ বা ‘মজলিস’ ব্যবস্থার তারা কর্ণধার। পাশাপাশি রয়েছে ধর্ম ও শরিয়ত এবং ধর্ম- শরিয়তের ব্যাখ্যাকারী ‘খতিব’ ও ‘কারী’। কোরান-হাদিসের মিশুর ওস্তাদ’ ‘মসজিদের খতিবের মুখনিঃসৃত বাক্য ‘কোরানের বয়ানের মতোই অভ্রান্ত, অবশ্য পালনীয়’। ‘হাফিজ-ই-কোরান’ ‘কারী সাহেব’ ‘শরা-শরিয়ত’ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।

গ্রাম পঞ্চায়েত ও ধর্ম-শরিয়তের বিধান হল, যাতে নারীরা সর্বদা ‘ঘোমটা’ রাখে মাথায়, অন্তঃপুরে থাকে এবং এমন স্বরে কথা বলে, যাতে বাড়ির পুরুষরাও শুনতে না পায় । গ্রাম-মধ্যে সংঘটিত অন্যায়ের শাস্তি বিধানকারী থানা-পুলিশ নয়, গ্রাম পঞ্চায়েৎ। শাস্তি হিসেবে রয়েছে ‘দোররা’, ‘পাথর ছুঁড়ে মারা’, ধাতব মুদ্রা পুড়িয়ে কপালে ছেঁকা দেয়া’ ইত্যাদি। সব ধরনের দণ্ডের রায় ঘোষণার প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তি গ্রামের জমিদার।
যে জমিদার শ্রেণী ভারতবর্ষে উদ্ভূত ও লালিত হয়েছিল বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং মোগল আমলের যারা ছিল ক্ষমতা-কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে, তাদের আভিজাত্যবোধ অহংকারের ধারক-বাহক আলোচ্য উপন্যাসের বাকুলিয়া গ্রামের ‘মিঞা বাড়ি’র জমিদার। অতীত গৌরবের মোহে অন্ধ জমিদার ফেলু মিঞা।
প্রজা তথা কৃষিজীবী মানুষ তার কাছে ছোট লোকের জাত। মিঞারা ভূমির কর্তৃত্বের সুযোগে কঠোর হস্তে প্রজা শাসন চালিয়ে গেছে যুগ পরম্পরায়। গ্রামের কৃষিজীবী নিম্নবর্গ আত্যন্তিকভাবে ভূমি-নির্ভর, কিন্তু তাদের চাষকৃত জমির প্রকৃত মালিক জমিদার। দরিদ্র গ্রামবাসীদের স্বীকারোক্তিতে সে সত্য প্রকাশিত :
“আপনি খাওয়ালে পর গরিব বাঁচে, না খাওয়ালে গরিব মরে। আপনি আছেন বলেই তো গ্রামটা টিকে আছে।
‘গরিব’ হচ্ছে গ্রামের কৃষিজীবী মানুষ, যাদের অধিকাংশ ভূমিহীন কিংবা স্বল্পভূমির অধিকারী; তাদের ভূমি ‘হাতের তালুর মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে ভাগ করা। বেঁচে থাকার জন্য তারা ‘বর্গা খাটে’- জমিদারের জমিতে; ফলে তারা জমিদারের প্রজা। আর জমিদার মিঞার বেটার কাছে তাদের পরিচয় ছোট লোক, কাঙালের জাত, ভিক্ষুকের জাত হিসেবে।
গ্রামীণ সমাজের জমিদার-শ্রেণীর সঙ্গে ক্ষমতা-কর্তৃত্বের অংশীদার মহাজনশ্রেণী। জমিদারের ক্ষমতার উৎস যেখানে প্রধানত ভূমি, মহাজনের সেখানে ভূমি ছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্য নগদ অর্থের মূলধনে চলে তাদের ‘সুদী কারবার, তেজারতি, চাষ’ এবং ‘ধান চাল-মশলার পাইকারি করবার। ক্ষেত্রবিশেষে ভৌত সম্পত্তির মালিক জমিদারের চাইতেও ক্ষমতাশালী বাণিজ্যলব্ধ নগদ অর্থের মালিক মহাজন।
জমিদার- মহাজন উভয়ের প্রভাব নিম্নবর্গ জীবনে একই। ভূমি এবং অর্থের জন্য ক্ষুদ্র কৃষক উভয়ের দ্বারস্থ। দেনা- খাজনার দায়ে কৃষক বন্ধকী জমি হারায় জমিদার-মহাজনের কাছে। আবার, জমিদারের দেনা পরিশোধের ক্ষেত্রে কৃষক মহাজনের ঋণের ওপর নির্ভরশীল। মহাজনের অর্থ যথাসময়ে ফেরত দিতে অক্ষম কৃষকের দেনা বাড়ে চক্রবৃদ্ধি হারে; শেষ পর্যন্ত তার পরিচয় দাঁড়ায় নিঃস্ব ভূমিহীন, দিনমজুর কিংবা গ্রামত্যাগী।
জমিদার-মহাজন ব্যতিরেকে রয়েছে মধ্যস্বত্বভোগী, যার অবস্থান জমিদার এবং সাধারণ কৃষকের মধ্যবর্তী রূপে। এ শ্রেণীর প্রতিনিধি রমযান। সে জমিদার ফেলু মিঞার কর্মচারী; তার কাজ জমির মালিক এবং প্রজাদের মধ্যে সংযোগ রক্ষা- “চাষী আর মিঞার মাঝে রমজান হল গিয়ে এক সেতু।” এ সুবিধাজনক অবস্থানকে সে কাজে লাগায় নিজের স্বার্থোদ্ধারে। অন্যায়, জুলুম, হয়রানির মাধ্যমে প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করে অতিরিক্ত অর্থ; প্রজারা তার ভয়ে প্রতি মুহূর্তে সন্ত্রস্ত।
প্রজা পীড়নকারী ভূমিকার কারণে সে জমিদারের প্রীতিভাজন। ভূমির প্রকৃত মালিক জমিদার হলেও প্রজার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। সেক্ষেত্রে সার্বিক তত্ত্বাবধানকারী তার বেতনভোগী কর্মচারী রমজান। ফলে বাকুলিয়া গ্রামে অলিখিতভাবে জমির মালিকের চেয়েও ক্ষমতাবান মধ্যস্বত্বভোগী।
কালক্রমে সে মধ্যবর্তী অবস্থান থেকে পৌঁছায় ভূনাধিকারীর পর্যায়ে। “মিঞা বাড়ির নায়েবি করে সে অর্জন করে সাত কানি জমি’ ও ‘পুকুরে অঢেল মাছ’। জমিদারের অজ্ঞাতে সে নিয়োজিত গোপন সুদী কারবারে। যখন যেভাবে সুবিধা, রমজান তার অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে লাভ করেছে অর্থ-সম্পত্তি। জমিদার-মহাজন মধ্যস্বত্বভোগী- এ তিন শ্রেণীর শোষণের সবটা চাপ পড়েছে কৃষিজীবী নিম্নবিত্তের ওপর।
বাকুলিয়া গ্রামের নিম্নজীবী মানুষের প্রতিফলন ঘটেছে লেকু, আম্বরি, কসির, হুরমতি, সেকন্দর প্রভৃতির মধ্যে। কৃষক লেকুর পিতা ছিল ‘নাম করা কামলা’। লেকু উত্তারাধিকার সূত্রে যে, ‘ছয় গন্ডা’ জমি লাভ করে, তা ‘বন্ধকি জমি। কার্যত সেই জমির মালিক, কিন্তু বাস্তবে তা জমিদারের হস্তাগত।
দৈহিক পরিশ্রমে অর্জিত অর্থে পিতার ঋণবন্ধকী জমি লেকু ফিরিয়ে আনে নিজের কাছে এবং কেনে আরো আট গণ্ডা জমি। জমিটুকু ছাড়া আর রয়েছে ‘ভিটি’; ভিটের চারপাশে কয়েক গণ্ডা শুপুরি গাছ, গোটা চার আম গাছ, একটা জাম গাছ’। সামান্য জমি, নিজের ও তার স্ত্রীর শারীরিক শ্রম-নির্ভর আয়ে লেকুর পাঁচ মাসের ব্যয় নির্বাহ হয়। বাকি সাত মাসের খোরাকের জন্য’ সে চেষ্টা চালায় নানাভাবে।
লেকুর বিশ্বাস, সে দৈহিক শ্রমে অর্জিত অর্থে ফিরিয়ে আনবে বন্ধকী জমি। প্রয়োজনে সে যাবে পাহাড়ি অঞ্চলে কিংবা বার্মার রাজধানী রেঙ্গুন। কার্যত লেকু সর্বস্ব হারিয়ে গ্রাম ছেড়ে শহরে যায় কাজের খোঁজে। কৃষক লেকুর নতুন পরিচয় দাঁড়ায় দিনমজুর রিকশাচালক। তার স্ত্রী আম্বরি অনাহার-অপুষ্টিজনিত ব্যাধিতে মৃত্যুবরণ করে কাঠির মত শীর্ণ শরীর নিয়ে।
লেকু ছাড়াও জমির খাজনা পরিশোধে ব্যর্থ কসির ‘বাপ- দাদার ভিটে ছেড়ে চলে যায় অজানার উদ্দেশ্যে। গ্রামত্যাগকারী কসিরের কণ্ঠে আশাবাদ, “মানুষ হয়ে লই, মানুষ হয়ে আবার ফিরে আসবো।” কসিরের ‘মানুষ’ হওয়ার অর্থ বিত্তবান হওয়া, ভূমির মালিক হওয়া। বাস্তবে লেকু, কসির চিরস্থায়ীভাবে উৎখাত হয় তাদের ভিটেমাটি-জমিন থেকে।
এভাবে লেকু-কসিরের মত ভূমি হারানো কৃষিজীবীরা চিরস্থায়ীভাবে উৎখাত হয় তাদের ভিটেমাটি জমি থেকে। এদের কেউ কেউ কৃষিজীবী জীবন ছেড়ে লেকুর মত শহরে অদক্ষ শ্রমিকে পরিণত হয়; কেউবা প্রতিবেশী দেশে পাড়ি জমায় শারীরিক শ্রমের ওপর নির্ভর করে বাঁচার প্রত্যাশায়। তাদের বেঁচে থাকার পথ অতি সংকীর্ণ। অল্প জমি, দারিদ্র্য, ঋণগ্রস্ততা লেকু-কসিরের মত বাংলাদেশের গ্রামের কৃষককে যুগ- পরস্পরায় প্রান্তিক অবস্থা থেকে একেবারে ভূমিহীনের কাতারে নিয়ে যায়।
অন্যদিকে প্রান্তিক কৃষকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমি মহাজন-জমিদারের দখলে চলে যায় চিরদিনের জন্য। এভাবে বাংলাদেশের গ্রামে নিম্নবিত্ত কৃষিজীবী মানুষদের জমি-হারানোর প্রক্রিয়া চলেছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে। ‘সংশপ্তক’ উপন্যাসে বাংলার গ্রামসমাজের এ বাস্তবতার প্রতিফলন লক্ষণীয়।
সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের প্রাক্কালে এসে ধারাবাহিক নিঃস্বতার শিকার গ্রামীণ নিম্নবিত্তের টিকে থাকার সমস্ত উপায় তাদের হাতছাড়া। তখনো গ্রামে উত্থান ঘটছে নতুন জমিদার-মহাজনের। নতুন চরিত্রে আবির্ভাব ঘটছে শোষণের। ‘সংশপ্তক’ উপন্যাসে ঐতিহ্যবাহী জমিদার ফেলু মিঞার পরিবর্তে গ্রাম-সমাজে আবির্ভাব ঘটে নব্য জমিদার রমজানের, যে কোনকালে সংশ্লিষ্ট ছিল না জমির মালিকানার সঙ্গে।
অতীতে সে বার্নার রাজধানী রেঙ্গুন যায় ভাগ্যান্বেষণে এবং সেখান থেকে পালিয়ে আসে খুনের আসামী হয়ে ফেলু মিঞার লেঠেল, নায়ের প্রভৃতি পেশায় থেকে সে চালায় প্রবল প্রজাপীড়ন। পুরনো জমিদার ফেলু মিঞার কাছে প্রজা শাসনের পাঠ নেয় ভাবি জমিদার রমজান। গোপন সুদ ব্যবসায়, কালোবাজারি, নারীপাচার ইত্যাদি অসৎ কারবারে গড়ে ওঠে তার অযুত সম্পদ। দেশ-বিভাগের পর রমজানের নতুন পরিচয় ‘কাজি মোহাম্মদ রমজান’।
হিন্দু জমিদারের রেখে যাওয়া ভূমি-সম্পত্তি দখল করে গ্রামে স্থায়ী প্রভাবের আসন নেয় সে। বাংলাদেশের গ্রাম-সমাজে রমজানের মত একজন দুর্বৃত্তের উত্থান ও বিকাশের মধ্য দিয়ে অসঙ্গতিপূর্ণ সমাজের একটা অবয়ব গড়ে ওঠে, যেখানে নিত্য অবমূল্যায়ন চলে মানুষের; যেখানে প্রতিনিয়ত শঠতা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, শোষণ-নিষ্পেষণে পীড়িত কৃষিজীবী মানুষ।
অপরদিকে সংশপ্তক উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র বাকুলিয়া গ্রামের সৈয়দ বাড়ির সন্তান আলীগড় শিক্ষিত জাহেদ পারিবারিক ঐতিহ্য সূত্রেই কলাকাতায় শিক্ষালাভ কালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভক্ত হয়ে পড়ে এবং সামন্ত স্বার্থের প্রতিভূ এবং বিত্রহীনদের এক কাতারে শামিল করে মুসলিম লীগ গঠনে আত্মনিয়োগ করে ।
পরে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় দাঙ্গা-বিরোধী ভূমিকায় এবং তারও পরে শ্রমিক-কর্মী হিসেবে সে আত্মপ্রকাশ করে। পাকিস্তান পরবর্তীকালে ঢাকায় শ্রমিক রাজনীতিতে লিপ্ত থাকার জন্য তার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হলে সে নতুনভাবে নিজ গ্রাম বাকুলিয়ায় ফিরে গ্রামের নিম্নমধ্যবিত্ত ও বিত্তহীনদেরকে শ্রেণী সংগ্রামের পতাকাতলে সমবেত করতে সফল হয়। বাস্তবের অভিঘাতেই ধর্মীয়- স্বাতন্ত্র্যবাদী জাহেদ সমাজতন্ত্রবাদী বিপ্লবীতে রূপান্তরিত হয়। সে শ্ৰেণীত্যাগেও সফল হয়।
ফলে পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের শোণদৃষ্টি জাহেদের উপর নিক্ষিপ্ত হয় এবং পরিণামে বাঙালি মুসলমানের ‘স্বপ্নের ভূখণ্ড’ পাকিস্তানের পুলিশ জাহেদকে গ্রেপ্তার করে।
উপন্যাসের কাহিনী পর্যবেক্ষণে আমরা দেখি, জাহেদের মনোভাবনা নিবেদিত সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধনায় এবং তার সমাজচিন্তা ক্রমবিবর্তনের পথে সমাজতান্ত্রিক জীবনাদর্শে উপনীত, যে জীবনাদর্শ আসলে ঔপন্যাসিকেরই। এমনকি আমরা দেখি, সমাজতান্ত্রিক দর্শনে বিশ্বাসী জাহেদ তার রাজনৈতিক বিশ্বাসের কারণে সরকারি রোষানলে পড়ে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার সময়েও এতটুকু হতাশ হয় না । বাকুলিয়ার গ্রামবাসীদের সে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যায়, “আবার আসবো আমি।
এভাবেই শ্রেণীশোষণ ও নিপীড়ন থেকে নির্বিশেষ মানবমুক্তির প্রত্যয় ধ্বনিত হয়েছে উপন্যাসের অন্তিমে জাহেদ চরিত্রের মধ্য দিয়ে।
উপন্যাসের অপর উল্লেখযোগ্য অন্যতম প্রধান চরিত্র শিক্ষিত গ্রামীণ মধ্যবিত্ত সেকান্দার মাস্টার চরিত্রটি। বাকুলিয়া তালতলি এলাকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিমূলক জীবনধারাকে সত্যিকার স্বাধীনতা ও মুক্তির দিগন্তে পৌঁছে দেবার ব্রতে কৃষকসন্তান সেকান্দারের ভূমিকা ব্যতিক্রমী। শ্রেণীসচেতন সেকান্দর সবসময়ই চেয়েছে দেশব্যাপী বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের ফলে মুক্তি আসুক-
“রোদে যাদের ক্ষেত পোড়ে, ক্ষিধেয় যাদের পেট জ্বলে, অকাল মৃত্যু যাদের কপালের লিখন, তাদের মুক্তি। ৩৬
এভাবে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে শোষিতের জন্য সহানুভূতি সেকান্দরের সংস্কারমুক্ত শ্রেণীসচেতন উদারচিত্তের পরিচয় দান করে। উপন্যাসের প্রথম পর্যায়ে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনার অনুসারী জাহেদের সঙ্গে কথোপকথনে সেকান্দর মাস্টারের আত্মস্বরূপ সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে।
“সহসা দু’হাত বাড়িয়ে সেকান্দরের পথটা আগলে দাঁড়ায় জাহেদ, হাতের মুঠোতে চেপে ধরে ওর জামার গলাটা, তারপর তীরের মত ছুঁড়ে মারে প্রশ্নটা, বল, তুমি মুসলমান কিনা?
হ্যাঁ।
তবে তুমি কি?
মানুষ।
অপমানবোধে মুখটা লাল হয়ে আসে জাহেদের। তুমি কি বলতে চাও আমি মানুষ নই?
না। তুমি মুসলমান।
আলবৎ। আমি প্রথমে মুসলমান তারপর মানুষ।….
ভুল করছ জাহেদ, ভুল করছ। প্রথমে মানুষ, তারপর ধর্ম। মানুষের জন্যই তো ধর্ম। ধর্মের জন্য মানুষ নয়।
উপন্যাসের মৌলপ্রবাহ সেকান্দর মাস্টারের অনুসৃত আদর্শের ধারায়ই যেন গতিশীল হয়ে উঠেছে।
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা প্রভৃতির মাধ্যমে নানা পরিবর্তনের ঢেউ বয়ে গেলেও সেকান্দর চরিত্রের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেনি। গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণকে ছেড়ে কোথাও পালিয়ে বাঁচতে আগ্রহী হয়নি। সে। সে শুধু অসাম্প্রদায়িকই নয়, শ্রেণীসচেতনও। সেকান্দরের চিন্তা-ভাবনা সুস্থ, যুগোপযোগী ও বিজ্ঞানভিত্তিক।
তার দৃষ্টিতে স্বাধীনতা অর্জনের অর্থ তাই কেবল ইংরেজ বিতাড়ন নয়। জাহেদের চিন্তার অসম্পূর্ণতাকে লক্ষ্য করে সেকান্দরের উক্তিতে সে সত্যই প্রকাশ পেয়েছে তোমার কাছে স্বাধীনতার অর্থ শুধু ইংরেজ বিতাড়ন। আমার কাছে তার অর্থ আরো ব্যাপক, ইংরেজ বিতাড়ন তো বটেই, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা, জার্ম, রুটি-রুজি, জীবনের নিরাপত্তা।
এ উপন্যাসের সত্যিকার সংশপ্তক যেন আর কেউ নয়, সেকান্দরই। সেকান্দর মাস্টারের মধ্যে যে শ্রেণী নিপীড়নমুক্ত বিপ্লবী গণচেতনার অংকুর তা ক্রমান্বয়ে রাবু মালু প্রমুখের রূপান্তরের মধ্য দিয়ে পরিণামে একটা সংঘবদ্ধ শ্রেণীচরিত্রে রূপ নেয়।
এভাবে ‘সংশপ্তক’ উপন্যাসে সমাজ এবং সময় চলমান ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। উপন্যাসটিতে কোন প্রকার স্থিতির ইঙ্গিত দিয়ে যতি টানেননি ঔপন্যাসিক উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র মুসলিম লীগের একনিষ্ঠ সমর্থক জাহেদের প্রত্যাশা যেখানে ছিল দেশ ভাগের মধ্যেই ঘটবে সকল সার্থকতা; তাতেও জাহেদ স্থিতি খুঁজে পায়নি। অবশেষে শোষিত মানুষের মুক্তির সংগ্রামে সে দীক্ষা নিয়েছে সমাজতন্ত্রে ।
উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতেও দেখা যায়, আরেক অনাগত জীবনপ্রবাহের আভাস। বাকুলিয়া গ্রামের মালু (মালেক), যার স্বপ্ন ছিল গায়ক হওয়ার, নতুন রাষ্ট্রের রাজধানী শহরে মানুষের ওপরে ওঠার বিকারগ্রস্ততা দেখে সে ফিরে আসে গ্রামে। একদিন কিশোর বয়সে যে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের মঞ্চে গেয়েছিল নজরুলের বিপ্লবী গান, সে দেখল তার আশা পূরণ হয়নি। সে নতুনভাবে প্রেরণা অর্জন করে জাহেদের কাছে।
সৈয়দ বাড়ির অন্তঃপুরের মহিলা সদস্য রাবু যে পরাধীন ভারতেই পিতা-পরিবারশাসিত ধর্মের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে, সেও এবার তার জ্ঞান-শিক্ষাকে কাজে লাগাতে চায় সমাজের শোষিত মানুষের জন্য কাজ করার মাধ্যমে। তার সামনেও আশার আলোকবর্তিকারূপী জাহেদ, জাহেদের রাজনীতিতে শরিক হয়ে সেও বামপন্থী চেতনার অধিকারী হয়েছে এবং আগ্রহভরে জাহেদের মানসসঙ্গিনী ও কর্মসঙ্গিনীতে পরিণত হয়েছে।
রাবু আসলে নতুন যুগের নারী কিন্তু সে যুগ তখনো যেন নির্মিতির অপেক্ষায়। উপন্যাসের শেষে পুলিশ কর্তৃক সমাজতন্ত্রী নেতা জাহেদের গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়ে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু জাহেদ গোপনে রেখে যায় আরো অনেক সংগ্রামী কর্মী, যারা বিশ্বাস করে, সংগ্রামের কেবল শুরু হয়েছে।
‘আমি আসব’ প্রতিশ্রুতিতে জাহেদ তাদের ভবিষ্যত সংগ্রামের আশাকেই বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে। এভাবেই সমাজ সময়ের প্রতিরূপে বামপন্থী আদর্শের অঙ্গীকার ও শ্রেণী চেতনা বিষয়টি ‘সংশপ্তক’ উপন্যাসে মহাকাব্যিক অবয়ব লাভ করেছে। মার্কসবাদের শ্রেণী সংগ্রাম ও গণমানুষের মুক্তির বাণী শহীদুল্লা কায়সারের উক্ত উপন্যাসে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

শামসুদ্দীন আবুল কালাম (১৯২৬-১৯৯৮)
আলোচ্য কালপর্বে শ্ৰেণীচেতনার পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে শামসুদ্দীন আবুল কালামের ‘কাশবনের কন্যা’ (১৯৫৪) এবং ‘আলমনগরের উপকথা’ (১৯৫৫) উপন্যাস দু’টিতে।
গ্রন্থ প্রকাশের ক্রম হিসেবে শামসুদদীন আবুল কালাম-ই বাংলাদেশের উপন্যাসের প্রথম সমাজতান্ত্রিক জীবনধারার ঔপন্যাসিক। তাঁর ‘কাশবনের কন্যা’ (১৯৫৪) এবং ‘আলমনগরের উপকথা’ (১৯৫৫) উপন্যাস দু’টিতে বিষয়বস্তু ও চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে সমাজ-ভাবনা অনেক ক্ষেত্রেই সমাজ-অন্বেষায় রূপ নিয়েছে। এ সমাজান্বেষায় সর্বাধিক অনুপ্রেরণা তিনি লাভ করেন সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্কসের সমাজতাত্ত্বিক জীবনদর্শন থেকে।
দুটো উপন্যাসেই গ্রামীণ নিম্নবর্গের দুঃসহ বাস্তবতা গেঁথে উঠেছে অকৃত্রিম জীবন-দৃষ্টিতে। ঔপন্যাসিক কৃষিজীবী এবং সাধারণ সহায়-সম্বলহীন মানুষদের করুণ কাহিনী বর্ণনা করেন; পাশাপাশি তাদের জন্য অন্তরে পোষণ করেন আশাবাদ। তাঁর উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলো ভবিতব্যের আশাবাদী স্বপ্নের লালনকারী। প্রবল হতাশার মধ্যেও তাই তারা উজ্জীবিত। সন্দেহ নেই, শামসুদ্দীন আবুল কালামের সমাজ- অন্বেষাই তাঁকে জোগায় নতুনতর প্রেরণা। বিশ শতকের যুদ্ধ-পরবর্তী বৈশ্বিক বাস্তবতায় মার্কসবাদ মানুষকে বিকল্প সমাজ বিনির্মাণের যে প্রতিশ্রুতি দেয়, ভারতবর্ষেও তা স্বাগত হয় বিশেষ মর্যাদায় ।
শামসুদ্দীন আবুল কালামের ‘কাশবনের কন্যা’য় সমাজতান্ত্রিক দর্শনের দুটো মাত্রা লক্ষ করা যায়। প্রথমত নতুন সমাজ-দর্শন হিসেবে মার্কসবাদকে তিনি গ্রহণ করেন এর প্রায়োগিক দিকটিসহ। তাই উপন্যাসে এসেছে রুশ বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর রাষ্ট্রের পটভূমি। আবার বাংলা সাহিত্যেরই আরেক দিকপাল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের সমাজ-ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন তিনি।
বস্তুত সেটাও আসে সাম্যবাদী চেতনার সাহিত্যিক রূপান্তর হিসেবে। ‘কাশবনের কন্যা’য় ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে শিকদার চরিত্রটি যে অবস্থানে পৌঁছায়, তাতে শামসুদ্দীন আবুল কালামের মানসস্বরূপ বিধৃত। জীবনের নিঃস্বতা শিকদারের মধ্যে জাগায় প্রবল হতাশা এবং এক পর্যায়ে তাকে তা গ্রাস করে চরমভাবে। কিন্তু ধীরে ধীরে হতাশার কবল থেকে সে মুক্তি পায়। সে উজ্জীবিত হয় ভবিষ্যতের স্বপ্নে।
লেখক তার এ উত্তরণটিকে প্রকাশ করেছেন নিপুণভাবে। প্রেমে ব্যর্থ শিকদার জীবনের ওপর আস্থা হারায়, জীবন তাকে বেঁচে থাকার প্রেরণা যোগাতে ব্যর্থ হয়। তার প্রেমের ব্যর্থতার মূলে রয়েছে দারিদ্র্য-অভাব। কিন্তু তাকে আশার প্রেরণা জোগায় জাহাজঘাটের ঘাট-মাস্টার। ঘাট-মাস্টার তাকে নতুন জীবনের গান রচনা করতে অনুপ্রেরণা জোগায়, যে-গানে থাকবে সাধারণ মানুষকে হতাশা থেকে জাগরণের ইঙ্গিত, যে-গানে মানুষ খুঁজে পাবে জীবনের তাৎপর্য এবং যে-গান তাদের সামনে উন্মুক্ত করে দেবে জীবনের প্রকৃত রূপ।
এভাবেই ঘাট- মাস্টারের প্রেরণায় হতাশ অবস্থা থেকে শিকদার ক্রমশ এগোতে থাকে আশাবাদের দিকে। ঔপন্যাসিক ঘাট-মাস্টার চরিত্রটিকে ব্যবহার করেছেন তার দর্শন প্রচারের বাহকরূপে। ঘাট-মাস্টার শিকদারকে যে ‘নতুন গান’ এবং ‘নতুন জীবনের’ কথা বলে তা প্রকারান্তরে লেখকের সমাজতান্ত্রিক সমাজ চেতনার প্রকাশ।
হতাশ শিকদারকে প্রথমে সে স্মরণ করিয়ে দেয় সমাজের কঠিন দুর্দশার কথা। কারণ, নিঃস্ব শিকদার একা নয়, তার মত অনেকেই রয়েছে সমাজে। কেবলই ভেঙ্গে না পড়ে ওঠে দাঁড়াবার মন্ত্র শিকদার লাভ করে ঘাট-মাস্টারের কাছে
“আপসোস নয় কেবল, আহাজারি নয় কেবল, কেবলই ফরিয়াদ কোরো না আসমানের দিকে হাত তুলে মনে জোর আনো, দেখো, কারা দিচ্ছে দুঃখ। তারপর লক্ষ লক্ষ দুঃখীজন মিলে যদি পারো সেই লুটের কৌশল ভেঙ্গে ফেলতে- যদি পারো সব ভণ্ডামীর শেষ করে দিতে, তাহলে আর তোমার মতো কোন মানুষ মনে মনে দুঃখ বয়ে বেড়াবে না। আত্মহত্যা করবে না ক্ষুধার জ্বালায়। তোমার ঘরের মা-বোন ঐ চালাক মানুষদের দেহের ক্ষুধা মেটাবার জন্য বলি যাবে না।
শ্রেণী সচেতন সমাজ সম্পর্কে ঘাট মাস্টারের এই উক্তির মধ্য দিয়ে শ্রেণী চেতনার প্রতিফলন ও উত্তরণের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ ধরনের প্রত্যক্ষ বক্তব্য শামসুদ্দীন আবুল কালামের উপন্যাসেই প্রথম দেখা যায়।
সমাজতান্ত্রিক ধারার লেখকদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে হতাশাগ্রস্ততা, আত্মহত্যার উল্লেখ তেমন একটা নেই। শামসুদ্দীন আবুল কালামের উপন্যাসেও দেখা যায়, জীবন যার কাছে একেবারে অর্থহীন, তাকেও জোগানো হচ্ছে বেঁচে থাকার প্রেরণা। ‘কাশবনের কন্যা’য় স্বামীর নির্যাতনে অতিষ্ঠ গৃহবধূ জোবেদা রাতের অন্ধকারে আত্মহত্যা করতে গিয়েও ফিরে আসে জীবনের প্রতি ভালবাসার টানে।
প্রচলিত সমাজ, সামাজিক শোষণকে হটিয়ে নতুন সমাজ গড়ার মার্কসবাদী দর্শনে বিশ্বাসই হতাশার পরিবর্তে ঔপন্যাসিকের আশাবাদের হেতু এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেই গড়ে উঠেছে তাঁর চরিত্রেরা। শিকদার যে-গানের অনুপ্রেরণা পায় ঘাট-মাস্টারের কাছে, তা-ও বিশেষ উদ্দেশ্যের দিকে নির্দিষ্ট। এ-গান ‘নতুন রকম গান’। তাকে এ গান গাইতে হবে ‘দেশে দেশে মাঠে মাঠে, ঘাটে ঘাটে।
এ গান ‘দুঃখী মানুষদের জাগাবে- তাদের বল দেবে, ভরসা দেবে। যে বিশেষ উদ্দেশ্যে লেখক এ গানের প্রতীককে ব্যবহার করেন, তা আসলে সমাজকে আমূল বদলে দিয়ে এক নতুন পরিচয়ে দাঁড় করানোর উদ্দেশ্য। ঘাট-মাস্টারের মাধ্যমে লব্ধ প্রেরণার ফলে শিকদার ‘এক নতুন মানুষে রূপান্তরিত; হতাশার মধ্যেও যে ‘ভগ্নপ্রাণ, বক্রমেরু’ নয়। স্বভাবজাত কাব্য-প্রতিভার অধিকারী শিকদারের কণ্ঠে গান স্বাভাবিক। কিন্তু শিকদারের প্রতি ঘাট- মাস্টারের ‘লক্ষ মানুষকে লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা যোগাবে তোমার গান’- এ সংলাপে লেখকের উদ্দেশ্য আরো স্পষ্ট।
গানকে সরাসরি লড়াইয়ের সঙ্গে যুক্ত করার মধ্যেই শামসুদদীন আবুল কালামের সমাজদর্শনের বিশেষত্ব ধরা পড়ে। আর এ লড়াইয়ে প্রতিপক্ষ কারা, সেটাও পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছেন লেখক, ঘাট-মাস্টারের জবানিতেই :
“যে মিথ্যা অজুহাতে জমি কাড়ে, ফসল নেয় ছিনাইয়া, ঝি-বউদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি লইয়া যাহারা ঘুরিয়া বেড়ায়।’
আমাদের আলোচ্য অন্যান্য ঔপন্যাসিকের উপন্যাসেও আমরা কৃষিজীবী মানুষদের শোষণকারী, নারী নিপীড়ক ব্যক্তিদের চিত্রায়ণ দেখতে পাই। তবে তাদের সম্পর্কে কোন উচ্চকিত বক্তব্য তাঁরা দেন না। কিন্তু একমাত্র শামসুদ্দীন আবুল কালামের উপন্যাসেই সমাজের সেসব অপকর্মকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মাধ্যমে সমাজটাকে পাল্টে দেয়ার আহ্বান লক্ষণীয়। লড়াইয়ে লেখক সমাজের অধিকার- বঞ্চিত সাধারণ মানুষের পক্ষে।
লেখকের অপর উপন্যাস ‘আলমনগরের উপকথা’য় সেটাই বিশদতর হয়েছে লেখকের সুস্পষ্ট রাজনৈতিক বক্তব্যের উপস্থাপনায়। বাংলাদেশের যে আর্থ-সামাজিক পটভূমিকে আশ্রয় করে ‘আলমনগরের উপকথা’ (১৯৫৪) উপন্যাসটির কাহিনী গড়ে উঠেছে, তার পরিচয় নিম্নরূপ :
“ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই মূলত বাংলাদেশে মধ্যপ্রাচ্য কিংবা অন্যান্য মুসলমান প্রধান অঞ্চল থেকে পীর-দরবেশদের আগমন ঘটে। এ দেশের প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর রূপ, সহজ-সরল মানুষ ও তাদের আতিথেয়তা, শ্রদ্ধা তাদেরকে আকর্ষণ করেছে প্রবলভাবে। তারা লাভ করেছে অতুলনীয় মাহাত্ম্য, ধন-সম্পদ ও প্রতিপত্তি। পীরের বংশধরেরা এই ঐশ্বর্যকে মূলধন করে এ দেশের শাসনক্ষমতা দখল করেছে। আধুনিক শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিঘাতে তাদের সামন্ততান্ত্রিক গৌরবে ফাটল ধরেছে। এদেশে নতুন উৎকেন্দ্রিক বিত্তবান অসাধু শিল্পপতিরা জন্ম নিয়েছে। এই দু’শ্রেণীর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রবল হয়েছে। এই দ্বন্দ্বের ফলে এদেশের গণচেতনা সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে এবং শেষ পর্যন্ত গণশক্তির জয় ঘোষিত হয়েছে।”
সমাজ বিবর্তনের উক্ত ঐতিহাসিক ধারার উপর ভিত্তি করে আলমনগরের উপকথা’ উপন্যাসের কাহিনী নির্মিত হয়েছে। আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনীর বিবরণে আমরা দেখি, মধ্য ভারতের মোগল দরবারের পীর হযরত জামালুদ্দীন তার শিশুপুত্র ও পরিবার-পরিজন এবং বহু লোক-লস্কর ও ভৃত্যসহ ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশে আগমন করেন।
সামন্তপ্রভু অরাতিদমন দেবের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জয়ী হয়ে আলমনগরে ধর্মের কল্যাণময় আদর্শের প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করে পীর জামালুদ্দীন। তাঁর পুত্র আলমউদ্দীন পিতার মৃত্যুর পর আদর্শচ্যুত হয়ে শাসক-শোষকে রূপান্তরিত হয়। বিলাসে-ভোগে- অত্যাচারে নিজ জীবন ও জনজীবনকে বিপর্যয়ের চরম অবস্থায় নিক্ষেপ করে আলমউদ্দীন।
একমাত্র পুত্র আলমগীরকে বিলেতে পাঠিয়ে তিনি বাঈজি ও সংগীতে আত্মমগ্ন জীবনযাপনে অভ্যস্ত হন। সামন্ত শাসকশক্তির এই পতনোন্মুখ অবস্থায় সমাজে জন্ম নিলো মীর খাঁর মতো অসৎ শিল্পপতিরা। কৌশলে ও ষড়যন্ত্রে এই বিকাশমান শ্রেণী সামন্ততন্ত্রের আভিজাত্য ও অর্থশক্তিকে বিপর্যস্ত করতে সক্ষম হল। ইতোমধ্যে মানবতা, প্রেম ও সাম্যবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে আলমগীর।
ধ্বংসোন্মুথ সামন্ততন্ত্র ও উদ্ভিন্নমান শিল্পপতিশ্রেণীর দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রতিক্রিয়ায় আলমনগরের গণজাগরণে নবাবপুত্র আলমগীর অবতীর্ণ হয় মৌল ভূমিকায়। নবাবের মৃত্যুজনিত শূন্যতার সুযোগে মীর খা আলমগীরকে অধিকার করতে উৎসাহী হয় উচ্ছৃঙ্খল কন্যা শ্যালীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে। কিন্তু প্রেম ও মনুষ্যত্বের আদর্শে আস্থাশীল আলমগীর বাঈজি কন্যা হওয়া সত্ত্বেও রোশন বাঈকে ভালবাসে।
মীর যার রুদ্ররোষ নিক্ষিপ্ত হয় রোশন বাঈ-এর প্রতি। তার হিংসা ও রিরংসা চরম রূপ ধারণ করলে অস্ত্র- রালবাসী পাগলা ময়েজের অস্ত্রাঘাতে মীর খাঁ মৃত্যুবরণ করে। হিংস্র-ক্ষিপ্ত শ্যালী নবাবপুরীতে অগ্নিসংযোগ করলে সবকিছু ভস্মীভূত হয়ে যায় ।
এমনিভাবে ‘আলমনগরের উপকথা’ উপন্যাসের পটে সামন্তবাদী ও উঠতি বিত্তবানদের দ্বন্দ্বের ফলে এদেশের গণচেতনার জাগরণ ও গণশক্তির বিজয়ের কথা বিন্যস্ত হয়েছে। আলমনগরের সামন্ত জমিদারির সমান্তরালে রয়েছে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র। তারা ‘পীরসাহেবের বার্ষিক ওরসের সময় দলে দলে মাজারে ভিড় করে জীবনের কষ্ট-যন্ত্রণা থেকে ত্রাণলাভের আশায় :
“সযত্ন-সঞ্চিত সম্পদ তাহার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া দোয়া মাঙে, আল্লার উদ্দেশ্যে কাঁদিয়া প্রাণের প্রার্থনা পৌঁছায়; কিন্তু দুঃখ-নিশার প্রভাত হয় না।’
বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের সোভিয়েত ইউনিয়নের সাম্যবাদী বিপ্লবের বার্তা এসে পৌঁছায় আলমনগরের গ্রামেও। উচ্চশিক্ষার্থে বিলাতগামী জমিদার বংশের সন্তান আলমগীর দীক্ষা নেয় সমাজতান্ত্রিক আদর্শে। বিশ্বের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চিন্তায় আলোড়িত তার মানস-জগৎ। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে রুশ বিপ্লবের পটভূমিতে সমাজের গতি-প্রকৃতি ধরা দেয় আলমগীরের দৃষ্টিতে, তাতে রয়েছে সমাজ পরিবর্তনের ইঙ্গিত :
“সামন্ততন্ত্র ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, কল বসিয়াছে, ধনতন্ত্র আজ নতুন পথে শোষণের ব্যবস্থা কায়েম করিতেছে।’ বিশ্বে সামন্ততন্ত্রের ভাঙ্গনের প্রেক্ষাপটে ধনতন্ত্রের উত্থান ঘটেছিল। তেমনি ভারতবর্ষের সমাজেও চলছিল পরিবর্তনের কাল। ব্রিটিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভূমির গুরুত্ব অত্যন্ত বেড়ে যাওয়ায় এবং ভূমি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হওয়ায় পুরো সমাজই যে ভূমিকেন্দ্রিকতার পথ ধরে বিকশিত হচ্ছিল, সেটি আমরা গবেষণাকর্মেরদ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করেছি।
ধনতন্ত্রের উত্থানের যুগে বৈশ্বিক বাজার- ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয় ভারতবর্ষের কৃষিভিত্তিক সমাজেরও। ভূমির সঙ্গে যোগ সাধিত হলো পুঁজির। তখন গ্রাম-সমাজের পুরনো জমিদার শ্রেণীর স্থানে নতুন পুঁজিপতি ক্ষমতাবান শ্রেণীর আবির্ভাব হয়। ‘আলমনগরের উপকথা’র মীর খাঁ এমনি এক মহাজন, যার একই সঙ্গে রয়েছে ভূসম্পত্তি ও বাজার- পুঁজি। ভূমিলব্ধ অর্থ সে বিনিয়োগ করে পাটকল-ব্যবসায় বাজারে যোগান দেয় স্থানীয় পণ্য।
জমিদার- মহাজনের যৌথ নিয়ন্ত্রণে শাসিত গ্রামাঞ্চলে জমিদার-পুত্র আলমগীর যাদের শ্রীহীন জীবনের দুর্গতি-মোচন কামনা করে, ‘তারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, জোঁকের কামড় খেয়ে, রোদে-বৃষ্টিতে পুড়ে… বন্যার সাথে লড়াই করে, ম্যালেরিয়া-কালাজ্বরে ভুগে ফসল ফলায় এবং সেই ফসল ‘নিজেরা উপবাসী থেকে তুলে দেয় জমিদার-মহাজনের ঘরে। সমাজ-ব্যবস্থার জাজ্বল্যমান বৈষম্য আলমগীরের চোখে স্পষ্ট :
“উৎপাদন ও বন্টনের অসম ব্যবস্থা সারা দুনিয়ার মেহনতি মানুষের দুঃখ মোচনের পথে প্রধান অন্তরায়। আলমনগরে তাহারই পুনরাবৃত্তি।’
বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের বৈষম্যমূলক সমাজ-ব্যবস্থার চিত্র রূপায়িত হয়েছে আলমনগরের প্রতীকী উপস্থাপনায় ।
আসলে বিলাত থেকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আসা উপন্যাসের নায়ক নবাবপুত্র আলমগীর ছিল গণমানুষের মর্যাদা ও প্রেমের মর্যাদায় বিশ্বাসী। সে গণমানুষকে শোষণহীন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী ছিল। তাই পারিবারিক ও শ্রেণীগত স্বার্থ-চেতনার বাইরে এসে শোষণমুক্ত জীবন গড়ার প্রত্যয়ে নবজীবন চেতনার প্রতীক নায়ক আলমগীর আপন অনুভব ও উপলব্ধিকে প্রকাশ করেছে:
“সামন্ততন্ত্র ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। কল বসিয়াছে, ধনতন্ত্র নতুন পথে শোষণের ব্যবস্থা কায়েম করিতেছে। নিজস্ব জীবনযাত্রা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গড়িয়া তুলিতে না পারিলে, যে দারিদ্র্য ও দুর্দশা এ দেশবাসীকে লড়াইয়া বহিয়াছে, তাহা হইতে মুক্তি নাই ।… এই দেশের লোক প্রধান কৃষিজীবী।
কৃষক জীবনের সহিত ধর্মের স্বাভাবিক যোগকে কোন মতেই অস্বীকার করা চলে না।… এই আস্থা জীবনানুগ । ধর্ম সেই আস্থারই প্রমাণস্বরূপ। ইহাকে ব্যাহত না করিয়াই জমির বিলি-বন্টন ও উৎপাদনকে সমতার ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রিত করিতে বাঁধা কোথায়?… আলমগীরের মনে হইতে লাগিল, এই দেশে এক নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়িয়া আদর্শ স্থাপন করা যায়।
অর্থাৎ সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে ধর্মের শ্রেয়োবোধের সমন্বয়ে এক অলীক স্বর্গরাজ্য গড়ার স্বপ্ন- এ অনুভবের মূলে আমরা সক্রিয় দেখতে পাই। ‘৪৭-এর অব্যবহিত পরবর্তী সমাজমানস বিচারে ঔপন্যাসিকের এ জাতীয় উপলব্ধি অস্বাভাবিক নয়। উপরিউক্ত উদ্ধৃতিতে উপন্যাসের নায়ক আলমগীরের উক্ত অনুভব ও উপলব্ধির মধ্য দিয়ে আসলে ঔপন্যাসিক আলোচ্য উপন্যাসের মূল বক্তব্যকেই উপস্থাপন করেছেন।
কারণ উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র কৃষক তোফেল, রতন কিংবা মফেজের মধ্যে বাংলাদেশের নিম্নবিত্ত মানুষের দুঃখক্রিষ্টতার যে চিত্র ধরা পড়েছে, তার বিচারে ঔপন্যাসিকের সমাজতন্ত্র সম্পর্কিত বক্তব্যকে সহানুভূতিপূর্ণ বলে মনে হয়। অর্থাৎ এসব বৈষম্য-অসঙ্গতিপূর্ণ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ঔপন্যাসিক একটি কল্যাণকর বিকল্পের সন্ধান করেছেন, যার বদৌলতে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠের জীবন হবে শোষণমুক্ত এবং দুঃখ-যন্ত্রণাশূন্য।
উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে আলমনগর বা ক্ষীরসায়র সম্পর্কে প্রদত্ত শামসুদদীন আবুল কালামের বক্তব্যে উক্ত তাৎপর্যের প্রতিধ্বনি খুঁজে পাই
“অতঃপর ক্ষীরসায়রে নতুন জীবনান্দোলন দানা বাঁধিয়াছে…। অবশ্য মানুষ কেবল খুঁজিতেছে মুক্তি, তাহার জীবন বিকাশের অধিকার। সেই সন্ধান অতি তীব্র, অতি কঠোর তার পথক্রমণ।’
এভাবেই ঔপন্যাসিক শামসুদ্দীন আবুল কালাম আলোচ্য উপন্যাসে শ্রেণী চেতনার প্রত্যয়কে সামনে রেখে নতুন সমাজ নির্মাণের ইঙ্গিতকে উপস্থাপন করেছেন।
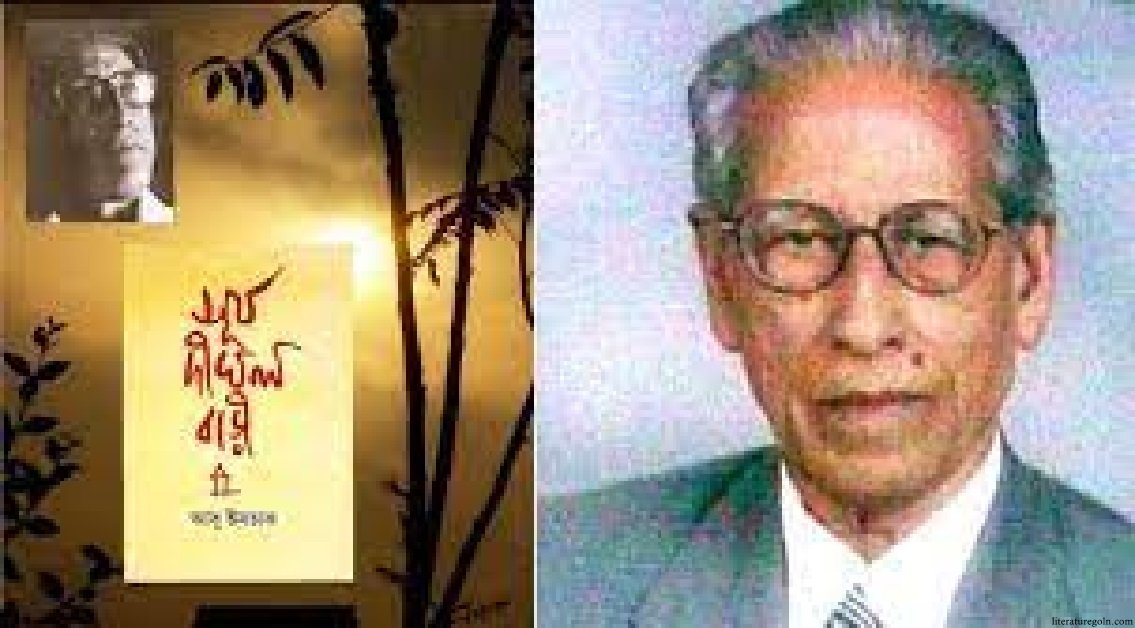
আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩)
আবু ইসহাক রচিত ‘সূর্য দীঘল বাড়ি’ (১৯৫৫) নামক একটি মাত্র উপন্যাস আলোচ্য কালপর্বের প্রতিনিধিত্ব করে। উপন্যাসটিতে লেখকের বস্তুবাদী দৃষ্টির পরিচয় মেলে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে ব্যক্তির শ্রেণী অস্তিত্ব ও সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি অংকিত হয়েছে এ উপন্যাসে। পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৩৫০/১৯৪৩) থেকে দেশ বিভাগ (১৯৪৭) এই পাঁচ বছরের সময় পরিসরে এ উপন্যাসের ঘটনাংশ বিস্তৃত।
বহমান সময়ের পটপরিসরে বাংলাদেশের বৃহত্তর গ্রামীণ জীবন ও সেই সর্বগ্রাসী পরিচয় এতে বিধৃত হয়েছে। উপন্যাসে চিত্রিত নির্দিষ্ট সময়ের বৃত্তেই ঔপন্যাসিক পূর্ববঙ্গের গ্রামে আবহমানকাল ধরে গড়ে ওঠা সংস্কার, বৈষম্য, শোষণের বাস্তবতাকে উপস্থিত করেন। দেশ বিভাগের সমকালীন বাস্ত বতাকে ছাড়িয়ে এ উপন্যাসে আমরা পাই সময়াতীত পূর্ববঙ্গের গ্রামকে।
উপন্যাসটিতে গ্রামীণ সমাজের তিনটি শ্রেণীর বিশদ চিত্র পাওয়া যায়। প্রথমতঃ গদু প্রধান, খুরশীদ মোল্লা, কাজী খলিল বক্শ প্রভৃতি জমিদার-মহাজন-কালোবাজারি, যারা গ্রামে গণ্যমান্য বলে পরিচিত। দ্বিতীয়তঃ জয়গুন, শফীর মা, জোবেদালী ফকির প্রভৃতি নিম্নবিত্ত মানুষ- এরা প্রত্যেকেই ভূমিহীন। এদের মধ্যে শফীর মা ভিক্ষুক, জয়গুন গ্রাম থেকে চাল নিয়ে বিক্রি করে নিকটস্থ মফস্বল শহরে এবং জোবেদালী ভণ্ড ফকির।
এদের মাঝামাঝি করিম বকশ স্বল্প জমির মালিক। জমির আয়ে সংসার চলে না বলে অন্যের জমিতে শ্রম খাটায়। উপন্যাসে কৃষিভিত্তিক বাংলার গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক-বৈচিত্র্যের বিশদ চিত্র আছে। তবে সামাজিক প্রতিকূলতার মধ্যে নিম্নবিত্ত মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামই এতে প্রধান। সামাজিক সম্পর্ক বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়েও মূলতঃ নিম্নশ্রেণীর মানুষের কাহিনীই মুখ্য হয়ে উঠেছে।
জয়গুনের জীবনের প্রতিকূলতার সিংহভাগ সমাজ সৃষ্ট। মন্বন্তরের সময় দুর্ভিক্ষের জ্বালা থেকে বাঁচতে প্রথমে তালাকপ্রাপ্তা এবং পরে বিধবা জয়গুন শহরে যায়, কিন্তু জীবিকান্বেষণের ব্যর্থতা নিয়ে সে গ্রামে ফেরে।
‘সূর্য দীঘল বাড়ি’ উপন্যাসের কাহিনীর সূত্রপাত হয়েছে এই মন্বন্তরের (১৯৪৩) বিবরণকে ঘিরে। অস্তিত্বের মৌল দাবি মেটাতে মন্বন্তরের সময় যে জনস্রোত চিরপরিচিত গ্রামকে পেছনে ফেলে শহরমুখী হয়েছিল, নগরজীবনের মর্মদ্ভদ অভিজ্ঞতায় রক্তাক্ত, বিপন্ন, নিঃস্ব-রিক্ত হয়ে তাদের পুনরায় গ্রামে প্রত্যাবর্তনের পটভূমিকায় ‘সূর্য দীঘল বাড়ি’ উপন্যাসের কাহিনীতে উদ্বাস্তু নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষের শোষণ বঞ্চনার প্রতিচ্ছবি অংকিত হয়েছে।
“আবার তারা গ্রামে ফিরে আসে। পেছনে রেখে আসে স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, মা-বাপ, ভাই- বোন। ভাতের লড়াইয়ে তারা হেরে গেল।
অনেক আশা, অনেক ভরসা নিয়ে গ্রাম ছেড়ে তারা শহরের বুকে পা বাড়িয়েছিল। সেখানে মজুতদারের গুদামে চালের প্রাচুর্য, হোটেলে খাবারের সমারোহ দেখে তাদের জিভ শুকিয়ে যায়। ভিরমি খেয়ে গড়াগড়ি দেয় নর্দমায়। এক মুঠো ভাতের জন্য বড়লোকের বন্ধ দরজায় ওরা মাথা ঠুকে ঠুকে পড়ে নেতিয়ে। রাস্তার কুকুরের সাথে খাবার কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়…..
যারা ফিরে আসে তারা বুকভরা আশা নিয়ে আসে বাচবার। অতীতের কান্না চেপে, চোখের জল মুছে তারা আসে। কিন্তু মানুষের চেহারা নিয়ে নয়। তাদের শির-দাড়া বেঁকে গেছে। পেট গিয়ে মিশেছে পিঠের সাথে। ধনুকের মত বাঁকা দেহ শুষ্ক ও বিবর্ণ। ”
এই উন্মলিত জনস্রোতেরই অংশ জয়গুন ও তার দুই সন্তান। বাইরের ছন্নছাড়া অসহ্য জীবন থেকে পরিত্রাণ লাভের আশায় অনেক স্বপ্ন বুকে নিয়ে জয়গুন গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে। কিন্তু দুর্ভিক্ষের মহাগ্রাসে সব সম্বল তার নিঃশেষিত হয়েছিল উপরের প্রয়োজনে। একমাত্র অবলম্বন জঙ্গলাকীর্ণ ভিটে পরিষ্কার করে সেখানেই নতুন করে আবাস গড়তে চায় জাগুন। কিন্তু গ্রাম্য বিশ্বাস ও সংস্কারে পূর্ব-পশ্চিম প্রসারী সূর্য দীঘল বাড়িটি ছিল মানব-বসতি স্থাপনের অযোগ্য।
তবুও গ্রামের অন্যান্য বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন এই ভৌতিক পরিবেশেই জয়গুন ও শফীর মাকে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে, গ্রাম্য চক্রান্ত, রিরংসা, লোভ এবং নেপথ্যচারী মানবীয় সক্রিয়তাই ‘সূর্য দীঘল বাড়ি’কে করে তুলেছে ভীতিকর ও বাস অযোগ্য। বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা জয়গুন ছেলে হাসু ও মেয়ে মায়মুনকে নিয়ে এই সূর্য দীঘল বাড়িতে নতুন করে শুরু করে তার জীবন সংগ্রাম।
পুত্র হাসুকে সঙ্গে নিয়ে তার অস্তিত্বের এই নবযাত্রা বিচিত্র প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়। জয়গুন ট্রেনে করে চাল এনে বিক্রি করে আর হাসু স্টেশনে মোট বেয়ে সামান্য আয়ে জীবন নির্বাহে উদ্যোগী হয়। জয়গুনের দ্বিতীয় স্বামী করিম বক্শ জীবিত, ‘দুর্ভিক্ষের বছর বিনা দোষে’ সে জয়গুনকে তালাক দিয়েছিল। তার গর্ভজাত সন্তান কাসুকেও নির্মমভাবে নিজের কাছে নিয়ে যায় করিম বকশ
“হাসু ও মায়মুনকে নিয়ে ভেসেই চলছিল জয়গুন। কিন্তু নিজের চেষ্টায় অকুল পাথারে কুল সে পায়। লজ্জা-শরম বিসর্জন দিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজে। তাঁকে বাঁচতে হবে, ছেলে-মেয়েদের বাঁচাতে হবে এই সংকল্প নিয়ে আকালের সাথে পাঁচ বছর সে লড়াই করে আসছে।”
ধর্মশাসিত সমাজে মেয়ে মানুষের পক্ষে কাজ করে অর্থ আয় করা অপরাধ। কিন্তু ছেলে-মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ধর্মের অনুশাসন জয়গুন ভুলে যায় এক মুহূর্তে। জীবনধারণের কাছে ধর্মের বারণ তুচ্ছ হয়ে যায়, মিথ্যে হয়ে যায়।
অমানবিক সমাজে নিজের অবস্থান সম্পর্কে জয়গুনের ভাবনা তাই দ্বিধাহীন।
“খাইট্যা খাইমু। কেউরডা চুরি কইরাও খাই না, খয়রাত নিইয়াও খাই না।
জয়গুনের এমনি নির্দ্বন্দ্ব ভাবনার মধ্যেই নিহিত রয়েছে তার জীবন সংগ্রাম, শ্রেণীগত জীবনসত্য তথা বেঁচে থাকার অর্থ। কেবল নিজের জন্য নয়, সংসারের আরো মানুষের অন্ন যোগাড় হয় তার শ্রমে। ধর্মের দোহাই দিয়ে রক্ষণশীল সমাজ তাকে ঘরে আবদ্ধ করতে চাইলেও জয়গুন সেই নির্মমতার বিরুদ্ধে প্রকাশ করে তীব্র ক্ষোভ— “তোবা আমি করতাম না। আমি কোন গোনা করি নাই।”
জয়গুন ছাড়াও ‘সূর্য দীঘল বাড়ির কৃষিজীবীরা অহোরাত্র কেবল বেঁচে থাকার চিন্তায় মগ্ন। দিনমজুর লেদুর সংলাপে আবু ইসহাক চিত্রিত গ্রাম সমাজের সেই অমানবিক চরিত্র পরিস্ফুট, যেখানে জমিদার মহাজন ও সাধারণ গ্রামবাসীর মধ্যে যোজন-যোজন ফারাক চিহ্নিত হয়ে উঠে
“তোমার গোলাভরা ধান আছে। তুমি এক সেরের বদলে দুই সের খাইলে তোমার গোলা ঠিক থাকব। কিন্তু সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলাইয়া রোজি করি পাঁচসিকা। এই ট্যাকা পেডে দিমু, কাপড় পিন্দুম, না এর তন রাজার খাজনা দিমু? ঘরে পরিবার আছে।… সারাদিন খাইট্যা সোয়াসের চাউল গামছায় বাইন্দ্যা ঘরে ফিরি। ৫১
এই নিম্নবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি যারা এক বাটি ফেনের জন্য’, ‘এক বাটি খিচুরীর জন্য মন্বন্তরের সময় দ্বারে দ্বারে ঘুরেছিল, তাদের অনেক আশা ছিল স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে। কিন্তু দেশ বিভাগকালীন স্বাধীনতা অর্জিত রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন জনজীবনে কোন গুণগত পরিবর্তন ঘটাতে ব্যর্থ হয়। নতুন রাষ্ট্রে নিম্নবিত্ত মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় সেই আশাভঙ্গের বেদনা-
“কত আশা ভসসা আছিল। স্বাধীন অইলে ভাত-কাপড় সায্য অইব। খাজনা মকুব অইব। কিন্তু কই বেবাক ফাটকি
নিম্নবিত্ত মানুষের শ্রেণীসচেতনতা এভাবে সমগ্র উপন্যাসের কাহিনীতে লক্ষ করা যায়।
উপন্যাসের শেষাংশে আমরা দেখি, সংগ্রামরত প্রতিবাদী জয়গুনের বালিকা কন্যা মায়মুনের বিবাহের কারণে ধর্মশাসিত সমাজের চাপে বাইরের কর্মক্ষেত্র থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় স্বামীগৃহ থেকে চিরদিনের জন্য মায়মুনের প্রত্যাবর্তন, গদু প্রধানের রিরংসা, আক্রোশ, জয়গুনের জীবনমূলকে বিশুদ্ধ করে তোলে। ফলে সে ধর্মের অনুশাসনকে উপেক্ষা করে অস্তিত্বকেই পরম বলে গ্রহণ করে :
“ক্ষুধার অন্ন যার নেই, তার আবার কিসের পর্দা, কিসের কি? সে বুঝেছে জীবন রক্ষা করাই ধর্মের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মূলমন্ত্র। জীবনরক্ষা করতে ধর্মের যে কোন অপ-আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সে প্রস্তুত। উদরের আগুন নিবাতে দোজখের আগুনে ঝাঁপ দিতেও তার ভয় নাই।’
এ কারণে ধর্মের শৃঙ্খল ছিন্ন করে জয়গুন পুনরায় বেরিয়ে পড়ে অস্তিত্ব রক্ষার অন্বেষণে। ফলে জয়গুনের গ্রামে বসবাস ক্রমশ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের পরোয়া না করে নিজের স্বাধীন ইচ্ছেমত চলার খেসারত তাকে দিতে হয় শেষ পর্যন্ত। রাতের অন্ধকারে গদু প্রধান তার অনুচরদের নিয়ে হত্যা করে জয়গুনের দ্বিতীয় স্বামী করিম বকশকে এবং রটিয়ে দেয় যে, করিম বকশ মারা পড়েছে সূর্য দীঘল বাড়ির ‘ভূতের’ আক্রমণে।
ফলে ‘সূর্য দীঘল বাড়ির অপর বাসিন্দা শফির মা-সহ জয়গুন তাদের সন্তানদের নিয়ে পুনরায় গ্রাম ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। বাঁচার আশা নিয়ে জয়গুন শহর থেকে ফিরে এসেছিল যে গ্রাম সমাজে, তা আসলে মানুষের বাঁচার সম্ভাবনাকে সংকুচিত করে দেয়। এটিই সত্য যে, অসুস্থ ক্লিষ্ট সমাজে জয়গুনের সুস্থ বসবাস সম্ভব নয়।
ভূ-সম্পত্তিধারী মহাজন কালোবাজারি নিয়ন্ত্রিত বিভাগোত্তর পূর্ববঙ্গের গ্রাম নিম্নজীবী মানুষের কাছে প্রসন্ন আশ্রয়ের পরিবর্তে বৈরী ভূখণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। পরিসমাপ্তিতে জয়গুনের গন্তব্য আর ঔপন্যাসিক দেখান নি। জয়গুনের অনিকেত যাত্রার বিবরণ নিম্নরূপ :
“ছেলে-মেয়েদের হাত ধরে জয়গুন ও শফীর মা বেরিয়ে পড়ে। মনে তাদের ভরসা খোদার বিশাল দুনিয়ায় মাথা গুঁজবার একটু ঠাঁই তারা পাবেই।
নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি দেশের মানুষ এভাবে পুনরায় ছিন্নমূল হয়ে যায়। এই নবযাত্রার সম্মুখ ভূমিতে মীমাংসাহীন অন্ধকার ও শূন্যতাই যেন একমাত্র সত্য হয়ে ওঠে। উপন্যাসের কাহিনী বিশ্লেষণে আমরা দেখি উক্ত নির্বিত্ত ও অসহায় ক্ষুদে দলটি শুধু নির্যাতিত ও বঞ্চিতই হয়েছে। নিপীড়ন ও অত্যাচার সম্পর্কে জয়গুন পরিবারের সচেতনতা ও গ্রামত্যাগ সব গ্রামবাসীর মধ্যে শ্রেণী চেতনা সঞ্চারিত করতে পারেনি।
এ কারণে সংগঠিত শ্রেণী সংগ্রামের ইঙ্গিত বা পরিচয় উপন্যাসটিতে নেই, তবে শোষিত নিম্নবিত্ত শ্রেণীর প্রতি সহমর্মিতা এবং অত্যাচারী শোষকদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ সঞ্চারে লেখক উপন্যাসেটিতে যথেষ্ট পরিমাণে সফল হয়েছেন। এভাবেই ‘সূর্য দীঘল বাড়ি’ উপন্যাসে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর জীবনসত্য রূপায়িত হয়েছে।
উপন্যাসের শেষোক্ত চলমানতার ফ্রেমে এক নতুন শ্রেণী অস্তিত্বের অগ্রযাত্রার সম্ভাব্য ইঙ্গিত প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। কিন্তু জয়গুন পরিবারের সংগ্রাম সমষ্টিচেতনায় জাগ্রত নয় বলেই উপন্যাসের শেষোক্ত চলমানতার ফ্রেমে নতুন শ্রেণী অস্তিত্বের অগ্রযাত্রা নির্মাণে লেখক তেমন সফল হতে পারেননি। ঔপন্যাসিক সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করলে একে সফল রূপ দিতে পারতেন বলা যায়।

আহমদ ছফা (১৯৪৩-2001)
আলোচ্য কালপর্বে শ্রেণী চেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করে আহমদ ছফা’র একটি মাত্র উপন্যাস ‘সূর্য তুমি সাথী’ (১৯৬৭)।
গ্রামীণ জীবনধারা ও সামাজিকতা, হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ ও সংস্কারাচ্ছন্নতা, নিম্নশ্রেণীর প্রতি উচ্চতর শ্রেণীর ঘৃণা ও নির্যাতন, মাতব্বরের স্বার্থপরতা ও নিপীড়ন এবং কৃষক-কর্মীদের হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণকে সংগঠিত ও শ্রেণীসচেতন করার উদ্যোগ এ সবকিছুই একটা সামগ্রিক চেতনার আলোকে সূর্য তুমি সাথী’ (১৯৬৭) উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে।
বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের এক পর্যায়ে গ্রামীণ সমাজকাঠামোতেও শ্রেণীসচেতন রাজনৈতিক ধারার সূত্রপাত হয়। মানুষকে হিন্দু কিংবা মুসলমান হিসেবে নয়, শোষক ও শোষিত শ্রেণীভুক্ত করে সমাজসত্যের তাৎপর্যময় রূপ উন্মোচন করেছেন আহমদ ছফা তাঁর সূর্য তুমি সাথী’ উপন্যাসে ।
রাষ্ট্র শোষণ, জাতি শোষণ ও শ্রেণী শোষণের ত্রিবিধ চাপে ছিন্নমূল অস্তিত্ব ‘হাসিম’ ও সমষ্টির সমগ্র রূপ অংকন করেছেন ঔপন্যাসিক। গ্রন্থের নায়ক হাসিম ধর্মান্তরিত হরিমোহনের (পরিবর্তিত নাম মুহাম্মদ ইসমাইল খান) পুত্র হাসিমের জীবনের ইতিবৃত্ত উন্মোচন সূত্রে ঔপন্যাসিক সমাজসত্যের গভীরতল স্পর্শ করেন।
হাসিম সম্ভ্রান্ত কাজী বাড়ির বাদী স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র। মর্যাদাহীন নিম্নবিত্ত হাসিম সামাজিক নির্যাতনের সার্বক্ষণিক শিকার। হাসিম কবিয়াল বা বয়াতি, সারিন্দা বাজিয়ে গান করে। ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক চেতনার ঊর্ধ্বে তার অবস্থান। ধর্মান্তরের ফলে সম্পদবঞ্চিত হরিমোহনের পুত্র হাসিম সর্বহারা শ্রেণীতে পরিণত হয়। শ্রেণী অবস্থান হাসিমের জীবনধারাকে গ্রামের অন্যান্য মানুষ থেকে স্বতন্ত্র করে দেয়।
ধর্ম বিচ্ছিন্ন, উত্তরাধিকার বিচ্ছিন্ন হাসিম নিজেকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিলেও ধর্মান্ধ মুসলমানরা তাকে ‘বান্যিয়ার পুত’ বলে গালি দেয়। সবদিক থেকে নিরাশ্রয় হাসিমের জীবনবৃত্ত উপস্থাপন সূত্রে ঔপন্যাসিক শ্রেণীগত জীবন সত্যের অনালোকিত রূপকেই উন্মোচন করেছেন।
লোকবিশ্বাস, সংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা, গ্রামীণ দলাদলি, ঈর্ষা-দ্বেষ-স্থৌলা প্রভৃতির মধ্যেও মানুষের অস্তি- ত্ব সম্মুখেই ধাবিত হয়। এই ধাবমান অস্তিত্বের আলোকবর্তিকা হিসেবে হাসিমের ক্রিয়াশীলতার ভূমিকাই মুখ্য। কৃষক সমিতির আদর্শবাদী চরিত্র, মনির আহমদ, হিমাংশু ধর ও কেরামত ভাই-এর সাহচর্য ও আদর্শবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে হাসিম কৃষক সমিতির (প্রগতিশীল কৃষক সংগঠন) কর্মী হয়ে সমাজসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করে এবং শ্রেণীসচেতন হয়ে ওঠে।
গ্রামের নির্বিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর পক্ষাবলম্বী কৃষককর্মী হাসিম স্থানীয় সমাজপতিদের অত্যাচার-অনাচারের বিরুদ্ধে সাহসী প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করে। অপরাপর চরিত্রের মধ্যে মাতবর খলু, অধর-ধর, কানা আফজল, জাহেদ বকসু- সবাই বাস্তবধর্মী শোষক শ্রেণীভূক্ত চরিত্র।
সমাজপরিত্যক্ত উচ্ছ্বলিত হাসিন কৃষক সমিতির কর্মী হবার পর সংঘশক্তির অংশ হিসেবে আবিষ্কার করে নিজেকে। মানুষ হিসেবে নিজ অস্তিত্বগত অবস্থানকে সনাক্ত করতে শেখে সে। হাসিমের আত্মজিজ্ঞাসা ও অস্তিত্ব-অভীপ্সার স্বরূপ এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত কারা যায় :
“সভার নেতারা বক্তৃতা করলেন। মনে হলো না যে, তারা দূরের মানুষ। যেন তাদেরই একান্ত আপনজন- কাছের মানুষ। দুঃখ-দুর্দশাকে সোজা ভাষায় সহজভাবে চোখের সামনে তুলে ধরলো না শুধু, কারণগুলোও বর্ণনা করলো। শ্যামল চেকন তলোয়ারের ফলার মতো আন্দোলিত শরীরের মানুষটার কথাগুলো তার চেতনায় সংগীতের মতো বাজতে থাকলো ।
এক সময় নাকি সমাজের সকলে সমান ছিলো, সকলে সমানভাবে স্বাধীন ছিলো। নাস ছিলো না কেউ কারো। সকলে সমানভাবে পরিশ্রম করতো, সমানভাবে ফলভোগ করতো। কেউ বড় কেউ ছোট ছিল না। মানুষ মানুষের মেহনত চুরি করে মানুষকে দাস বানিয়ে রেখেছে। কৃষক-শ্রমিকের বুকের খুন-ঝরা মেহনত চুরি করে ধনী হয়েছে মানুষ। মেহনতি মানুষের বুকের তাজা রক্ত। তাদের বাগানে লাল লাল গোলাপ হয়ে ফোটে।
সহস্র রকম পদ্ধতিতে তারা কৃষকের রক্ত শুষে নিয়েছে। হাসিম যেন চোখের সামনে শোষণের নলগুলো দেখতে পেল। সর্বশক্তি প্রয়োগ করে এ শোষণের পথ বন্ধ করতে হবে। সে জন্য দরকার সমিতি। ঘরে ফেরার সময় বক্তৃতার কথাগুলো হাসিমের চেতনায় বারংবার আবর্তিত হয়ে ঘোরে। পৃথিবীর সমস্ত শ্রমিকের শ্রম চুরি করে ধনীরা বালাখানা গড়েছে। হাসিম তো শ্রমিক, তারও শ্রম চুরি করেছে।
এতোক্ষণে ধরতে পেরেছে অধরবাবু, কানা আফজল আর খলুদের সঙ্গে তার মতো মানুষদের তফাৎটা কোথায়। বক্তৃতার আলোকে চেনা মানুষদের নতুন করে খুঁটিয়ে দেখে সে। তাদের শরীর থেকে যেন লাল লাল তাজা রক্ত করছে। আর অধরবাবুদের মুখে রক্তের লাল ছোপ। প্রবল উত্তেজনায় দু’হাত মুঠিবদ্ধ হয়ে এলো।
এমনিভাবে শ্রেণীসচেতন হাসিমের চেতনার সুপ্ত অবরুদ্ধ কলিগুলো দল মেলতে শুরু করে। হাসিমের চেতনা উত্থিত ভাবনা সূত্রে ঔপন্যাসিক আহমদ ছফা মানুষকে হিন্দু কিংবা মুসলমান হিসেবে নয়—-
শোষক ও শোষিত শ্রেণীভুক্ত করে সমাজসত্যের তাৎপর্যময় রূপ উন্মোচন করে দেখান। যেমন নিচের এই অংশটুকু
“ভয় শুধু হিন্দুকে? হিন্দুরা কি মরণের চাইতেও ভয়ংকর? হিন্দুদের মধ্যে কি ভাল মানুষ নেই? মুসলমানদের মধ্যে কি খারাপ মানুষ নেই? জাহেদ বকসু, খলু মাতব্বর, কানা আফজল এরা কি ভাল মানুষ?
হেডমাস্টার গিরিজাশংকর বাবু যিনি মুসলমানের ছেলের প্রাণরক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দিলেন, তিনি কি খারাপ মানুষ? হাসিমের ধারণা, কানা আফজল আর অধরবাবুরা একযোগেই তো মৃত্যুর ব্যাপার করে। ওরা হিন্দু নয়, ওরা মুসলমান নয়, ওরা একজাত- অত্যাচারী। এ সত্যটা মানুষ বোঝে না কেন? কেন বোঝে না? ভয়ানক দুঃখ হয়, যে দুঃখের কোন রূপ নেই । ৫৬
উপন্যাসের কাহিনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কৃষিভিত্তিক সমাজে শক্তিদ্বন্দ্বের প্রধান উৎস জমি। জমি সংক্রান্ত দাঙ্গায় বরগুইনীর পাড়ের পাশাপাশি দুটো গ্রামে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। কৃষক সমিতি সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করলেও গাছবাড়িয়ার খলু মাতব্বর শক্তিদন্তে সমিতির সদস্যদের তাড়িয়ে দেয়।
ফলে সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। সাতবাড়িয়ার কাদের মিয়ার সঙ্গে লড়াইয়ে খলু মাতব্বর পরাস্ত হয়। তার পক্ষেও লাঠিয়ালরাই বেশি জখম হয়। এমনিভাবে গ্রামের বিধবা মায়ের সন্তান যুবক লাঠিয়াল ‘হুদু’ জম হয়ে প্রাণ হারায়। তখন শোষকশ্রেণীর প্রতিভূ কানা আফজল ও জাহেদ বকসুর মধ্যস্থতায় ছদুর পরিবারের সাথে মুখে মুখে দু’কানি জমি দানের রফায় সব ঘটনার নিষ্পত্তি হয়ে যায়।
বহু মাতবরের উদ্দেশে পড়শি চাচা চন্দ্রকান্ত ও হাসিমের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে শ্রেণীশোষণের সেই নিষ্পেষিত ভয়াবহতারই চিত্র পাওয়া যায়
“কেন ভাইপুত, তোরে আগে কি কইলাম। বুঝিলি ছদুর জানের দাম মোডে দুই কানি জমিন না? আজিয়া দিব কালিয়া কাড়ি লৈব। বদমাইশ পোয়ারে আগে এত চেষ্টা গরিও বিয়া গড়াইত না পারে। অহন এউগ্গা তৈয়ারি বউ পাই গেল। কেন ভাইপুত রাধামাধবের লীলা তেলা মাথায় তেল, আতেলা মাথা একাই গেল’। আল্লাহ তো থল্যা আর কানা আফজল্যার, কি কস?… হ্যাঁ, আল্লাহ খলু আর কানা আফজলের।” হাসিম কথা কয় না। মনে মনে আল্লাহর কেমন বিচার উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে।

আল্লাহ তাদের না হলে অন্যের সর্বনাশ করেও কেমন করে তারা লাভবান হয়! আজ দু’কানি জমি মুখে মুখে দিলো, কাল কেড়ে নিয়ে যাবে। আনুর সঙ্গে খাদিম আলীর মেয়ের বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিল দু’বছর আগে। অনেক ভেট-বেগার বয়েও কোন ফল হয়নি। ডেট-বেগারে খাদিম আলীর মন ওঠেনি। সরল মানুষ খাদিম আলী। শত অনুরোধে খলু মাতব্বরের মতো পেঁচী মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাতে রাজি হয়নি। খাই-খাসলত ভাল দেখে ছন্দুকেই মেয়ে বিয়ে দিয়েছিল। ছদু গেছে, বউটা অল্প বয়সে রাঁড়ি হয়েছে।
এখন খলু মাতব্বরের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হতে খাদিম আলীর তরফ থেকে কোন আপত্তি ওঠার কথা নয়। কেমন জটিল আর ঘোরালো আল্লাহর কল। সে কলে গরিবেরাই বা কেন পিষে যায়! চন্দ্রকান্ত শুধু নয়, গ্রামের সকলের মনে একথা লেগেছে। কিন্তু মুখ দিয়ে বের করার সাহস নেই কারো। বুকের কথা মুখে বলতে পারে না কেন মানুষ? কেন মানুষ মুখ ফুটে অত্যাচারকে বলতে পারে না অত্যাচার? এ সকল মৌলিক প্রশ্ন হাসিমকে ভয়ানকভাবে খোঁচায়।৫৭
এভাবেই অশিক্ষিত ছিন্নমূল হাসিম সংঘ জীবনাবেগে প্রাণিত হয়ে পরিণত হয় সাহসী কর্মীপুরুষে। এক সময়ে দেখা যায়, অন্ধ ধর্মশক্তি, সমাজশক্তি ও রাষ্ট্রশক্তি কৃষক সমিতির কার্যক্রমে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। সিগারেট কোম্পানির জমি দখলের প্রতিবাদে গ্রামের কৃষকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজনে কৃষক সমিতির সংঘবদ্ধ প্রয়াসের মধ্যে শ্রেণী সংগ্রামের ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়।
কৃষক সমিতির অন্যতম সংগঠক মনির আহমদের বক্তৃতায় সেই পরিচয় প্রকাশিত
“সিগারেট কোম্পানি ফ্যাক্টরি বানাতে চায় বানাক। পাহাড়ের দিকে বিস্তর জমি খালি পড়ে আছে। কোম্পানির টাকা আছে ট্রাক্টর আনুক। পাহাড় ভেঙ্গে ময়দান করে একটা কেন, একশোটা ফ্যাক্টরি করা যায়। আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু এ বিলের জমি না হলে আমাদের চলবে না । বাঁচবো না আমরা। আট হাজার টাকাতেও এ জমি ছাড়বেন না। কেননা, এ জমি ছাড়া আমাদের অন্য কোন নির্ভর নেই।
কারো ব্যবসা নেই, চাকরি নেই, অন্য কোথাও বাড়তি জমি নেই। যাদের এ বিলে কোন স্বত্ব নেই, তাদের অনেকের এ বিলের জমি ভাগে চাষ করে, মজুর খাটে। চাকরি নওকরির টানে তারা কখনো বিদেশে যায়নি। বরগুইনির উর্বরা পলিতে কোম্পানির নজর পড়েছে। সুতরাং গ্রামের মানুষ কি নির্বিবাদে সে জমি ছেড়ে দেবে? না, না। কিছুতেই তা হতে পারে না।
“না, না” কখনো না। এটা অত্যাচার। গরিবের ওপর অত্যাচার। এ অত্যাচারে কোম্পানির সঙ্গে ইউনিয়নের মেম্বার-চেয়ারম্যান যোগ দিয়েছে। খলু মাতব্বর, জাহেদ বকসু, অধরবাবু, চেয়ারম্যান আফজল মিয়ার মতো মানুষ, যারা আপনাদের বারবার কেনাবেচা করেছে, তাদেরকে বিশ্বাস করতে পারেন কি? এবারও তারা আপনাদের বিরুদ্ধে গিয়েছে। কোম্পানি তাদের টাকা দেবে। অনেক বেশি টাকা। অতো টাকা জীবনে আপনারা কোনদিন দেখেননি। তাদের বিরুদ্ধে নিজেদের দাবির ওপর বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারবেন কি? আপনাদের একতার বল যদি অটুট থাকে কেউ জমিতে হাত বাড়াতে পারবে না। পারবেন কি আপনারা?’
‘আঁরা এক থাইকম। ক্যারে জমিনত দাগ লাগাইতম দিতাম নয়।’ (আমরা এক থাকব, কাউকে জমিতে দাগ লাগাতে দেব না)। এক সঙ্গে সমবেত জনতা সায় দিলো।
এভাবেই কৃষক আন্দোলনের নেতা মনির আহমদ গ্রামের সবার মধ্যে শ্রেণী চেতনা জাগিয়ে তোলে।
তার ফলস্বরূপ দেখা যায়, সিগারেট কোম্পানির জমি দখলের প্রতিবাদে গ্রামের কৃষকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার দায়ে মনির আহমদ সহ সমিতির অপরাপর সদস্য হিমাংশু বাবু, মান্নানকে গ্রেফতার করে পুলিশ। শ্রেণীসচেতন হাসিমের উক্তিতে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে দেখি :
“কেরামত ডাই আর কিছু ন গরিবা?” (কেরামত ভাই, আর কিছু করবে না?)।
“না ভাই, আর কিছু করার নেই বর্তমানে।” জবাব দিলো কেরামত।
“এই যে পঁচিশ জন ভালা মাইনষেরে জেয়লত লৈ গেল, তার পতিকার কি?” (এই যে পঁচিশ জন ভাল মানুষকে জেলে নিয়ে গেল, তার প্রতিকার কি?) ।
“হাসিম ভাই, প্রতিকার এতো সহজ নয়। এই তো অত্যাচারের সবেমাত্র শুরু। জালিমেরা বনের বাঘের মতো ভয়ংকর হয়ে উঠবে, আর মজলুমেরা সকলে একজোট হয়ে যতদিন না রুখে দাঁড়াচ্ছে কোন প্রতিকার নেই। মনির আহমদ কিংবা হিমাংশুবাবু তো নয় শুধু, এমনি হাজার মানুষ বিনা অপরাধে জেল খাটছে।
-কৃষক কর্মী কেরামতের উক্ত উক্তির মধ্য দিয়ে শ্রেণী চেতনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও মূল সুর ধ্বনিত হয়েছে।
এভাবেই ‘সূর্য তুমি সাথী’ উপন্যাসে সংঘবদ্ধ কৃষক আন্দোলনের সম্ভাবনা, শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতি সচেতনতার ইঙ্গিত এবং গ্রামীণ সমাজে শিল্প-কারখানার শ্রমিক জীবনের প্রতি আকর্ষণ উন্মোচিত হয়েছে। উপন্যাসের পরিশেষে হাসিম ও জহুরার গ্রাম ছেড়ে কারখানায় কাজ করতে যাওয়ার মধ্য দিয়ে সমাজ পরিবর্তনের ইঙ্গিত ব্যঞ্জিত হয়। বলা যায়, একটা হ্যাঁ অর্থক ও আশাবাদী জীবনচেতনার বিন্যাসে ‘সূর্য তুমি সাথী’ উপন্যাসে ঔপন্যাসিক আহমদ ছফা শ্রেণী চেতনা ও শ্রেণী সংগ্রামের সম্ভাবনাকে সার্থকতার সঙ্গেই রূপায়িত করেছেন।