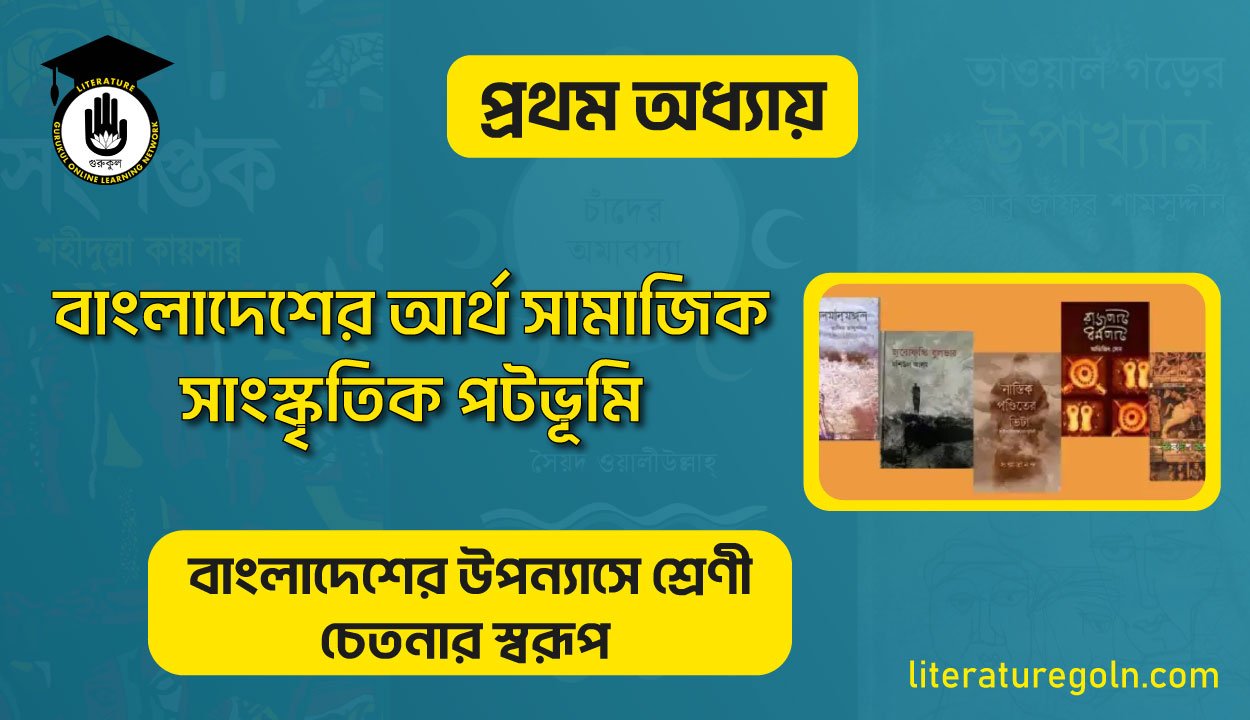আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়ঃ বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক সাংস্কৃতিক পটভূমি। যা বাংলাদেশের উপন্যাসে শ্রেণী চেতনার স্বরূপ এর অন্তর্গত।

বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক সাংস্কৃতিক পটভূমি
উপন্যাস জীবনের সমগ্রতাস্পর্শী শিল্পরূপ। উপন্যাসে বিন্যস্ত জীবন নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে বহমান। বাঙালির সৃষ্টিশীল চেতনায় সমাজজীবনের দ্বন্দ্ব জটিল বিকাশ প্রক্রিয়ার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সেকারণেই ‘বাংলাদেশের উপন্যাসে শ্রেণী-চেতনার স্বরূপ (১৯৪৭- ১৯৭১)’ শীর্ষক গবেষণাকর্মের প্রথম অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হল বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক সাংস্কৃতিক পটভূমি।
অষ্টাদশ শতাব্দীতে “ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত কলকাতা এবং মধ্যযুগের মোঘল শাসকবর্গ প্রতিষ্ঠিত ঢাকা আর্থ-সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যের কারণে জন্মলগ্ন থেকেই স্বতন্ত্র ধারায় বিকাশ লাভ করে। মোঘল সাম্রাজ্য শক্তি তাদের শাসনব্যবস্থার অনুকূলে বাংলার কৃষিভিত্তিক স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ কাঠামোকে সামন্ত সমাজে রূপান্তরিত করে।
মোঘল আমলে সৃষ্ট বঙ্গীয় সামন্ত সমাজের বিরোধী কম্প্রেডর বা মুৎসুদ্দী বাণিজ্য পুঁজিপতিদের সহায়তায় ব্রিটিশ বাণিজ্য পুঁজিপতিশক্তি ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে অধিকার করে নেয় বাংলার রাষ্ট্রক্ষমতা। ফলে সুলতানি আমলের ‘বাঙ্গালা’ আকবরের ‘সুবা বাংলা’ ব্রিটিশের উপনিবেশে পরিণত হয়।
সম্রাট জাহাঙ্গীর প্রতিষ্ঠিত বাংলার রাজধানী ঢাকা (জাহাঙ্গীরনগর) এর পরিবর্তে কলকাতায় স্থাপিত হয় ভারতের প্রথম রাজধানী। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর বাণিজ্য পুঁজি (Mercantile Capitalism) এবং শিল্প পুঁজিকেন্দ্রিক (Industrial Capitalism) শাসন প্রক্রিয়া এবং নব্যসৃষ্ট কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী সমাজগঠন ও জীবন বিন্যাসের বস্তুগত ও ভাবগত রূপান্তরকে অনিবার্য করে তোলে।”
এর ফলে ব্রিটিশ পুঁজির সহযোগী হয়ে গড়ে উঠতে থাকে ভারতীয় পুঁজি এবং উভয় পুঁজির পক্ষপুটে লালিত, বর্ধিত হয়ে গড়ে ওঠে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী। বঙ্গীয় পুঁজি ও তার সহযোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানসজাগরণই বাঙালির পুনর্জাগরণ নামে পরিচিত।
হিন্দু কলেজ, ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৭), ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি (১৮১৮) প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধেই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি চেতনায় পরিপুষ্ট এক শিক্ষিত জনশ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। ১৮৫৮ খ্রিঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এই নবোদ্ভূত শ্রেণীর জনা উন্মুক্ত করে দেয়া হয় উচ্চশিক্ষার দ্বার।
এই নাবালক শিক্ষা সংস্কৃতির ভাবধারার ইতিবাচক আলোড়নের ফলে বাংলার সমাজজীবন থেকে রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), রাধাকান্ত দেব। (১৭৮৪-১৮৬৭), দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮- ১৮৯৫) প্রমুখের মত প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বের জন্ম সম্ভব হয়। অপরপক্ষে ১৭৫৭-এর পরবর্তী সময়প্রবাহে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হৃতগৌরব ঢাকা শহর তথা পূর্ববাংলার জীবনকাঠামো ও সমাজবিন্যাসের রূপান্তর প্রক্রিয়া থাকে মন্থর ও পশ্চাৎপদ।
দেখা যায়, উনবিংশ শতাব্দীতে দ্বারকানাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ বাঙালি মনীষীর যে বিচিত্রমুখী বিকাশ সাহিত্য-শিল্প-দর্শন ও বিজ্ঞান চিন্তার মধ্য দিয়ে ক্রমপরিণতি লাভ করেছিল, বলতে গেলে, তার সম্পূর্ণ কৃতিত্বই বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের।
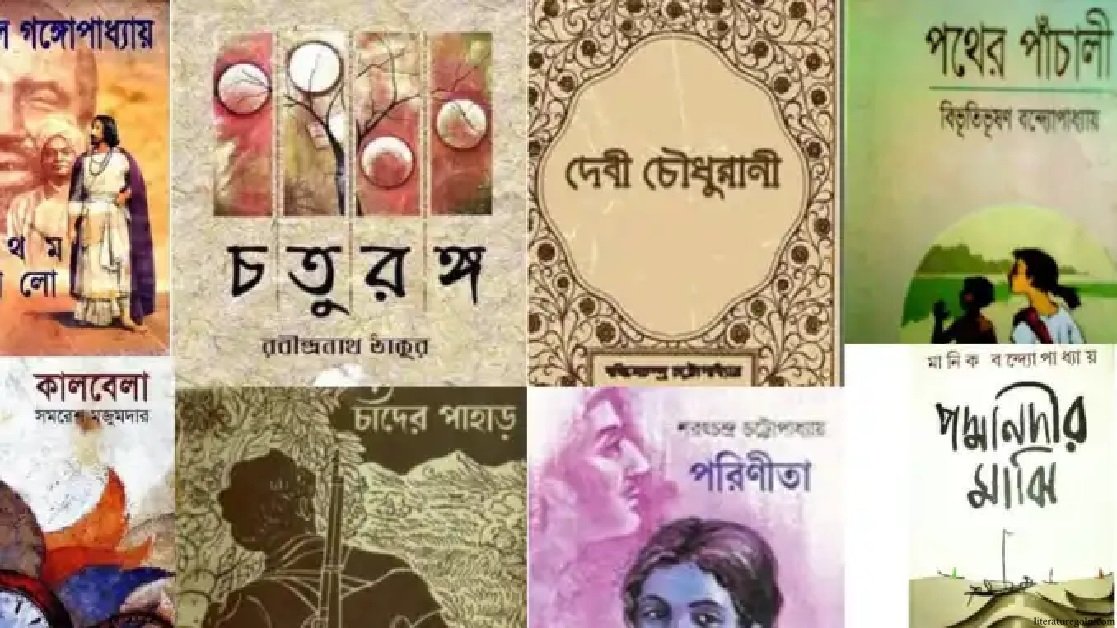
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য-সাম্রাজ্যবাদী শাসনামলে যে নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে, ক্রমান্বয়ে ব্যবসা বাণিজ্যের নেতৃত্ব, শিক্ষা সরকারি চাকুরি প্রভৃতি ক্ষেত্রে অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সেই জনস্রোতের একাংশ পরিণত হয় বণিক শ্রেণীতে। অন্যদিকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর আমকাননে সংঘটিত সিরাজ-উদ্-দৌলার পতন বাঙালি মুসলমানের কাছে নিজেদের দুর্ভাগ্যের সমান্তরাল অনুভূতিতে পর্যবসিত হয় ।
বর্তমান বিমুখতা, অতীত প্রীতি, পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি- শিল্প-দর্শন ও বিজ্ঞানকে বাঙালি হিন্দু যেখানে জাগতিক অগ্রগতি ও বৈষয়িক মুক্তির অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করে, সেখানে এক ধরনের অহংবোধ, অভিমান ও ইংরেজের প্রতি অসহযোগিতামূলক মনোভাব প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমান তা থেকে বিরত থাকে। এর ফলে কেবল তাদের বৈষয়িক অগ্রগতিই ব্যাহত হয় না, ভাব জগতেও আসে দীনতা, পশ্চাদমুখিতা। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ও তার পরিণতি মুসলমান জনশ্রেণীর মধ্যে কিছুটা আত্মসমীক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়।
কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জীবন চেতনার অঙ্গীকারে মুসলমান জনশ্রেণীর মধ্য থেকে যে নতুন মধ্যবিত্তের জন্ম সম্ভাবনা দেখা দেয়, তাকে একটি শ্রেণী চরিত্রে পরিণত হতে অপেক্ষা করতে হয় বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্ন পর্যন্ত। বাংলাদেশের এই নবোদ্ভূত মধবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ তরান্বিত হয় তিনের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার (১৯২১) মধ্য দিয়ে।
তবে অবিভক্ত বাংলার বিভাগপূর্ব আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামো সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়, দ্রুত নগরায়ণ, মধ্যবিত্তশ্রেণীর উদ্ভব এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জীবনবোধের অভিঘাতে কলকাতা নগর ও পার্শ্ববর্তী সমাজ সংগঠন ও জনজীবনে যে গতি, সংঘর্ষ ও বৈচিত্র্যকে অনিবার্য করে তোলে; তা ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গিগত বৈষম্যনীতির কারণেই ঢাকা শহর ও তার পার্শ্ববর্তী সমাজ কাঠামো ও জীবন বিন্যাসে সে রূপ বিবর্তন বিলম্বিত হয় বিংশ শতাব্দীর তিনের দশক পর্যন্ত।
ইংরেজ শাসকদের শাসনতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি যে নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টিকে অনিবার্য করে তোলে তার সমগ্র ঔজ্জ্বল্য, সুকৃতি-বিকৃতি কলকাতা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। ১৮৫৭ খ্রি: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘটনা থেকে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশগত তারতম্যের স্বরূপ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর ফলে, চিন্তায় মূল্যবোধে জীবনবিন্যাসে এবং সমাজ গঠনের স্বাতন্ত্র্যে বাঙালি জনগোষ্ঠীর বিকাশকে দুই পৃথক ধারায় প্রবাহিত হতে বাধ্য করে।
বর্তমানে বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডের জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে, মুসলমান তরুণ সম্প্রদায়ের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা ছিল দূরসঞ্চারী, ইতিবাচক প্রাণচাঞ্চল্যে গতিময়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারিত্র ছিল সাম্প্রদায়িকতা বর্জিত এবং যুদ্ধোত্তর পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনাস্পর্শী। দেশ বিভাগের নেতৃত্ব গড়ে উঠেছিলো ইংরেজের শাসন- তোষণ নীতির গর্ভে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিসমূহের মধ্য থেকে- যাঁদের শিক্ষা সম্পন্ন হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যালকাটা মাদ্রাসা কিংবা অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে পূর্ববাংলার মুসলমান তারুণ্য আলিগড়ের সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে যেমন মুক্তিলাভের সুযোগ পায়, তেমনি, প্রথাগত সামাজিক অচলায়তনের বিরুদ্ধে সজাগ ও সোচ্চার হবার শক্তি অর্জন করে।
প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ অঞ্চলের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং মুসলমান সমাজে একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবও অনিবার্য হয়ে উঠে। বিশ শতকের তৃতীয় দশকের প্রারম্ভ থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশের বিভিন্ন কলেজ- স্কুল উত্তীর্ণ নব্যশিক্ষিতের সমবায়ে ক্রমবিকশিত হচ্ছিল ঢাকা শহরকেন্দ্রিক নব্যমধ্যবিত্ত শ্রেণী।
এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইউরোপীয় বুর্জোয়া ধ্যান-ধারণা, যুক্তিবাদ-মানবতাবাদকে অঙ্গীকারকল্পে ১৯২৬ খ্রি:-এ প্রতিষ্ঠা করেন মুসলিম সাহিত্য সমাজ এবং প্রকাশ করেন উক্ত সংগঠনটির মুখপত্র ‘শিখা’। এ সাহিত্য সমাজের আদর্শ ছিলো চিন্তাচর্চা, জ্ঞানের সমন্বয় সাধন ও সংযোগ সাধন। ‘শিখা’র ভূমিকাংশে ছাপানো হতো “জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।”

শিখা সম্প্রদায়ের ভাববিপ্লবের সংঘাত তরঙ্গে পূর্ববঙ্গীয় মধ্যবিত্তের গণজাগরণের প্রবাহ হয়েছিল গতিবান। মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডলে। মুসলমান সমাজের বিচারবুদ্ধিকে অঙ্গ সংস্কার ও শাস্ত্রানুগত্য থেকে মুক্তিদানের বাসনা সংগঠনের কর্মকাণ্ডকে করেছিল বিশিষ্ট। সমকালীন শিক্ষিত তরুণ-মানসে এর আবেদন ছিল বিস্ময়কর।
দৃশ্যত এর প্রেরণা এসেছিল মুস্তফা কামালের উদ্যম থেকে, কিন্তু তার চাইতেও গুরুতর যোগ এর ছিল বাংলার বা ভারতের এ-কালের জাগরণের সঙ্গে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডলেই গড়ে উঠেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্যের গতিনির্দেশক পটভূমি।
এ-প্রসঙ্গে সুকুমার সেনের মন্তব্য উল্লেখ্যযোগ্য: “কল্লোলের বীজ বপন হইয়াছিল ঢাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের ছাত্রদের বার্ষিক পত্রিকা বাসন্তিকায় (১৯২২) ….. কাল্লোলের প্রবাহ কিছু দূর গড়াইলে পরে ইহার একটি কচি শাখা বাহির হইয়াছিল ঢাকায় প্রগতি (1829)।
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বিভেদের জটিল রাজনৈতিক প্রবাহের সমান্তরালে এ-সময়ে আরেকটি রাজনৈতিক ধারা সক্রিয় রূপ নেয়। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের তত্ত্বাবেগ কমরেড মুজাফফর আহমদের কর্মপ্রক্রিয়ায় সাংগঠনিক পর্যায়ে উপনীত হয়। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (১৯২৭-২৮) গঠনের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান সর্বাগ্রগণ্য। কৃষিভিত্তিক শোষণমূলক সমাজের তরুণমানসে প্রগতিশীল আন্দোলনের আগ্রহ সৃষ্টি হতে থাকে।
বাঙালি মুসলমানের সচেতন অংশের নেতৃত্বে প্রজা পার্টি (১৯১৪) গঠন এবং কমরেড মুজাফ্ফর আহমদ ও কাজী নজরুল ইসলামের যুগ্ম-সম্পাদনায় নবযুগ (১৯২১) পত্রিকার প্রকাশনা এই প্রগতিশীল ও মৃত্তিকামূলস্পর্শী রাজনীতিচেতনার ভিত্তি সুদৃঢ় করেছিল। ত্রিশের দশকে জাতীয় রাজনীতির অভিজ্ঞতা থেকে নব্যশিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায় ধর্মকেন্দ্রিক সামন্তবাদী, সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ-সৃষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে।
এ-সময়ে মার্কসীয় তত্ত্বে বিশ্বাসী এবং বুর্জোয়া মানবতাবাদী কিছু সংখ্যক ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী প্রতিষ্ঠা করেন প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ’ (১৯৩৯)। চল্লিশের দশকে এই সংগঠনের কার্যক্রম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসরে বিস্তার লাভ করে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মুসলিম সাহিত্য সমাজ, প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা ও প্রতিক্রিয়ায় যে নব্যশিক্ষিত, প্রগতিশীল ও বুর্জোয়া মানবতাবাদে আস্থাশীল মধ্যবিত্তের উদ্ভব ও বিকাশ সাধিত হয়, তা সংঘবদ্ধ শ্রেণীচরিত্রে রূপ নেওয়ার পূর্বেই কার্যকর হয় ভারত বিভাগ (১৯৪৭)।
নয়া-উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদী আদর্শবাহী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রের সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রই যে দেশবিভাগের নেপথ্যে বিদ্যমান ছিলো, তা এখন স্বীকৃত সত্যে পর্যবসিত। অসমবিকশিত সমাজের শ্রেণী-অস্তিত্বের অসংগঠিত অবস্থা এবং দ্বন্দু জটিল ও রক্তাক্ত অভিজ্ঞতাপুঞ্জ পাকিস্তান আন্দোলনের তীব্রতায় যেমন বিভ্রান্ত হয়েছিল; তেমনি, স্বাধীনতার আকর্ষণেও অভিভূত হয়েছিল।
উল্লিখিত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপট নিরিখে বলতে পারি, জাতীয় ইতিহাসের যে বৈপ্লবিক ধারা দুই বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা এবং রক্তাক্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটি স্বাধীন, শোষণমুক্ত ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পটভূমি প্রস্তুত করেছিল। ১৯৪৭ এর ভারত বিভাগ ও তার অব্যবহিত ঘটনাপ্রবাহ সেই ধারাকে করে তোলে অবরুদ্ধ, দ্বন্দুরক্তিম ও দ্বিধাযুক্ত।
প্রায় দু’শ বছরের শাসনামলে ব্রিটিশ রাজশক্তি তাদের বৈষম্যমূলক শোষণের প্রয়োজনে যে দ্বিজাতিতত্ত্বের বীজ বপন করেছিল, ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগ ছিল সেই সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রেরই বিষময় ফল। মূলত “সেই মধ্যরাত্রির স্বাধীনতা ছিল খণ্ডিত, অশ্রুসিক্ত ও শোণিতলিপ্ত। সে স্বাধীনতা ছিল একই সঙ্গে আমাদের “Triumph s Tragedy” সেই শোণিতলিপ্ত ঘটনা পরম্পরার সর্বাপেক্ষা বিয়োগান্তক পর্যায়ে ছিল, বাংলাদেশ ভূখণ্ডের পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তি।
আর্থ-উৎপাদন কাঠামো এবং ভৌগোলিক ও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের পূর্বাঞ্চল ও তার জনগোষ্ঠীর জন্য এ রাজনৈতিক মীমাংসা হল অসঙ্গত ও একেবারে ঐতিহাসিক ধারার পরিপন্থী। ফলে দেশ বিভাগের পর পূর্ববঙ্গ নতুন রাষ্ট্রীয় পরিচয় পেল বটে; কিন্তু আরেক নতুন উপনিবেশের কবলে গিয়ে পড়লো। এক সর্বগ্রাসী লুণ্ঠন প্রক্রিয়ায় পূর্ববঙ্গের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যেতে থাকে।
পূর্ববঙ্গের মানুষের দুর্দশা ক্রমাগত বেড়ে চলে; অন্যদিকে পূর্ববঙ্গের কৃষকদের শ্রম নিংড়ানো অর্থের বিনিময়ে মজবুত হতে থাকে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতি। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, কল-কারখানা সবকিছু গড়ে উঠতে থাকে পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ববঙ্গ সর্বক্ষেত্রেই থেকে যায় বঞ্চিত-অবহেলিত। বস্তুত রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক- শ্রেণীর হাতে থাকায় অর্থনৈতিক শোষণও তারা চালাতে থাকে অবাধে।

সমাজবিজ্ঞানী অনুপম সেন তাঁর “বাংলাদেশ: রাষ্ট্র ও সমাজ’ গ্রন্থে দেখান, পঞ্চাশের দশকে কৃষিভিত্তিক রাষ্ট্র পূর্ববঙ্গ পাট উৎপাদনের মাধ্যমে বিশ্ববাজার থেকে যে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে, তার প্রায় সম্পূর্ণটাই আত্মসাৎ করে পশ্চিম পাকিস্তানের বণিক শ্রেণী। তিনি লিখেছেন- “এভাবে পূর্ববঙ্গের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে সঞ্চিত হয়। এবং তা বিনিয়োগ করেই পশ্চিম পাকিস্তানে শিলে পান্নয়নের সূচনা হয়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের এ শিলে পান্নয়নে পূর্ববঙ্গের কোনো লাভ-ই হয়নি।
অধিকন্তু পূর্ববঙ্গকে পশ্চিম পাকিস্তানের উৎপাদিত দ্রব্যের একচেটিয়া বাজারে পরিণত করা হয়। পূর্ববঙ্গের গরিব জনসাধারণ বাধ্য হয় বিশ্বের খোলা বাজারে যে জিনিসের দাম এক টাকা, সেটা দু’টাকা অথবা তিন টাকায় এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাঁচ টাকায় কিনতে। এভাবে পূর্ববঙ্গকে পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত করা হয়। উক্ত উদ্ধৃতিতে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ এ পুরো সময়ের একটা সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন পাওয়া যায়। ব্রিটিশ উপনিবেশের হাত থেকে পূর্ববঙ্গ চাল যায় পাকিস্তানি উপনিবেশের অধীনে।
এ-অবস্হা শোচনীয়তর হয় ১৯৫৮-এর সামরিক শাসনের ফলে। সামরিক শাসনে ব্যক্তির বাক-স্বাধীনতা ও অন্যতর অধিকারসমূহ থেকে সে বঞ্চিত হয়। ঔপনিবেশিক শোষণের প্রেক্ষাপটে পূর্ববঙ্গের কৃষকের অবস্থা হতে থাকে সবচাইতে খারাপ। যে উৎপাদন ব্যবস্থায় নিয়োজিত থেকে পূর্ববঙ্গের কৃষক রাষ্ট্রের যোগান নিশ্চিত করে যায়, তা ছিল দুর্দশাগ্রস্ত, প্রাক-পুঁজিবাদী ধরনের; এবং এরকম পশ্চাৎপদ অবস্হায় কৃষকের উৎপাদন-ক্ষমতাও হয় ক্রমক্ষীয়মান।
যেহেতু পশ্চিম পাকিস্তানের পাশাপাশি পূর্ববঙ্গে শিল্পায়ন গড়ে উঠেনি, সেহেতু কৃষির ওপর চাপ ক্রমশ বেড়েছে। শিপরিকাশহীন সমাজে উপরন্তু ছিল বাড়তি জনসংখ্যার জন্য খাদ্য সরবরাহের দায়। এভাবেই নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনে দারিদ্রোর উত্তরোত্তর আগ্রাসন অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে।
অর্থনৈতিক-সামাজিক জীবনের এই গুণগত পরিবর্তনহীনতা এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির পশ্চাৎপদতার ফলে দেখা গেল বৃহত্তর জনজীবনে পাকিস্তানি প্রশাসন তার জন্মলগ্নেই মোহভঙ্গের কারণ হয়ে উঠলো। ধর্মাদর্শনির্ভর রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার নামে পাকিস্তানি শাসকবর্গ বাংলাদেশে জাতিশোষণ, শ্রেণীশোষণ ও সাংস্কৃতিক অবরোধ সৃষ্টিতে হলো তৎপর। এর বিরুদ্ধে বিশ শতকের ক্রমবর্ধমান বাঙালি বেনিয়া পুঁজিবাদী এবং স্ফীতকায় বুর্জোয়া মানবতাবাদী ও মার্কসবাদী মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রতিবাদ করে ১৯৪৮-এ।
বৃহত্তর জনজীবন-বিচ্ছিন্ন ঢাকায় নগরকেন্দ্রিক শিক্ষিত মধ্যবিত্তের এই প্রতিবাদ ততোটা তীব্র না হলেও এর মধ্যে থেকেই অঙ্কুরিত হলো গণজাগরণ ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বীজ।
বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করায় পাকিস্তানি শাসকবর্গের অব্যাহত চক্রান্তের প্রতিবাদে এ- দেশের সচেতন ছাত্রসমাজ সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলে। গঠিত হয় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ (৩০ জানুয়ারি, ১৯৫২)। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২-এ রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা প্রতিষ্ঠার দাবিতে ২১ ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী এক সাধারণ ধর্মঘটের আহবান জানানো হয়।
গণশক্তির ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে এক মাসের জন্য ঢাকা জেলার সর্বত্র ধর্মঘট, সভা, শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করে। ঐক্যবদ্ধ ছাত্রসমাজ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে স্লোগানের বিক্ষুব্ধ মিছিল নিয়ে অগ্রসর হতে থাকলে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য পুলিশ ছাত্র মিছিলে গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই শহীদ হন আব্দুল জব্বার ও রফিকউদ্দিন আহমদ। গুরুতর আহত হন সতের জন। হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় তাদেরকে। তাঁদের মধ্যে আবুল বরকত মৃত্যুবরণ করেন রাত আটটায়।
রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রচণ্ড দমন, নির্যাতন ও গ্রেফতার সত্ত্বেও ২১ ফেব্রুয়ারি, রক্তদানের প্রতিক্রিয়ায় বৃহত্তর জনজীবনে পাকিস্তানি শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে ক্ষোভ তীব্ররূপ ধারণ করে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, মুষ্টিমেয় ছাত্র শিক্ষক বুদ্ধিজীবীর আন্দোলন ছিল না, তা শুধু শিক্ষাগত অথবা সাংস্কৃতিক আন্দোলনও ছিল না। বস্তুতপক্ষে তা ছিল পূর্ব বাংলার ওপর সাম্রাজ্যবাদের তাবেদার পাকিস্তানি শাসক-শোষক শ্রেণীর জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে এক বিরাট ও ব্যাপক গণআন্দোলন।
ভাষা আন্দোলন পরবর্তীকালে বাংলাদেশের মানবতাবাদী, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তি রূপে সমাজজীবনের বৃহত্তর পরিসরে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়। পাকিস্তানি মুত্সুদ্দী পুঁজি ও সামন্তশক্তির সঙ্গে বাংলাদেশের আত্মনিয়ন্ত্রণ-প্রত্যাশী পুঁজির সংঘাত হয়ে ওঠে তীব্রতর। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তানি বেনিয়া পুঁজি ও প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তশক্তির ধারক মুসলিম লীগের সর্ববিধ প্রয়াস সত্ত্বেও অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল শক্তি যুক্তফ্রন্ট বিজয় লাভে সমর্থ হয়।
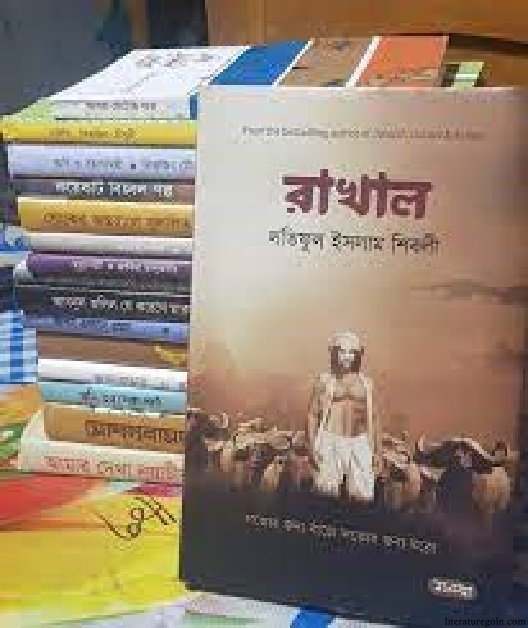
৫৪’র নির্বাচনের ফলাফলের মধ্য দিয়েই প্রথম সূচিত হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদের গণতান্ত্রিক বিজয় ১৯৫২ পরবর্তীকালে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ রূপান্তর সাধিত হয়। বাঙালি বেনিয়া পুঁজি, পাকিস্তানি পুঁজির সহযোগী হিসেবে গড়ে উঠতে থাকে।
সাধারণ নির্বাচনের পর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে আমদানি বাণিজ্যে পূর্বাঞ্চলের নবাগতদের প্রবেশাধিকারের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং বৈদেশিক মুদ্রা বন্টন ব্যাপারেও দুই প্রদেশের মধ্যে সমতারক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এভাবেই প্রস্তুত হয় বাঙালি জাতীয় পুঁজি বিকাশের পটভূমি।
সংগ্রাম, রক্তপাত ও উজ্জীবনের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭-১৯৫৭ কালপর্বে বাঙালি জীবনের প্রায় প্রতিটি স্তরেই ইতিবাচক রূপান্তরের সূত্রপাত হয়। রাজনৈতিক পরিস্থিতির অস্থিরতা-বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড মানবতাবাদ, গণতন্ত্র ও প্রগতিশীল চেতনায় সমৃদ্ধি অর্জন করে। পাকিস্তানি পুঁজিবাদী শক্তির ষড়যন্ত্রের ফলে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা হয় ক্ষণস্থায়ী। ১৯৫৪ সালের মে মাসে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা বাতিল করা হয়।
এটা ছিল বাংলাদেশের সামন্তপ্রথাভিত্তিক গণতন্ত্রের উপর পুঁজিবাদীদের প্রথম আঘাত; কিন্তু মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করলেও ১৯৫৯-এর পূর্বে পুঁজিবাদ জয়যুক্ত হতে পারেনি। ১৯৫৮ সালের সামরিক অভ্যুত্থান ছিল সামন্ত প্রথাভিত্তিক গণতন্ত্রের উপর শেষ ও চরম আঘাত। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতনের পর ১৯৫৮ সালের আগস্ট পর্যন্ত কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক ষড়যন্ত্রের ফলস্বরূপ বারবার মন্ত্রিসভার পতন পাকিস্তানি সামরিক জান্তার ক্ষমতা দখলের পথ সুগম করে দেয়।
আইয়ুব খানের সামরিক শাসন প্রবর্তন (৭ অক্টোবর, ১৯৫৮) পাকিস্তানি নয়া উপনিবেশবাদী শাসননীতির অন্তর্ঘাতক চরিত্রেরই বহিঃপ্রকাশ। বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার সংগ্রামশীল অগ্রযাত্রার পটভূমিতে পাকিস্তানি সামরিকতন্ত্র উদ্ভূত মৌলিক গণতন্ত্রের শৃঙ্খল জাতিকে গভীর সংকটে নিক্ষেপ করে। যে সমস্ত মূল্যবোধ, ধর্মমোহ ও সাম্প্রদায়িক চেতনা এক দশকের অভিজ্ঞতা (১৯৫২-১৯৫৮) ও সংগ্রামে জাতিসত্তার কাছে পরিবর্জিত প্রায় শক্তিতে পরিণত হয়েছিল, আইয়ুবী দশকের সূচনায় তাকেই ব্যবহার করা হয় নব আঙ্গিকে।
ফলস্বরূপ দেখা যায়, সামরিক শাসন প্রবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী চেতনাকে অবরাদ্ধ করার চেষ্টা চলে। তারই কৌশল রূপে সংগ্রামী নেতৃবর্গকে করা হয় কারারুদ্ধ। জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশের গতিও এর ফলে বাধাগ্রস্ত হয়।
দেখা গেল, পাঞ্জাবি বেনিয়া পুঁজিবাদী শক্তি তাদের শাসন এবং শোষণকে দৃঢ়মূল করার লক্ষ্যে কেবল রাজনীতি ক্ষেত্রেই নানামুখী পদক্ষেপ নিল না, সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রেও তারা সুদূরপ্রসারী বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে বি.এন.আর প্রেস ট্রাস্ট, পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড (পূর্বাঞ্চল শাখা) ইত্যাদি সংস্থা যেমন প্রতিষ্ঠা করা হয়, তেমনি আদমজী, দাউ্দ ও অন্যান্য পুরস্কার প্রবর্তন এবং উপাধি বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। এর মাধ্যমে সচেতন- বুদ্ধিজীবী ও শিল্পী-সাহিত্যিকদের শৃঙ্খলিত ও চেতনাদাসে পরিণত করার প্রচেষ্টায় পাকিস্তানি সামরিক সরকার অনেকাংশে সাফল্যও অর্জন করে।
চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে উদ্ভূত অধিকাংশ ঔপন্যাসিকই জীবনবোধের ক্ষেত্রে পূর্বপ্রতিশ্রুতিভ্রষ্ট হয়ে পড়েন। সময় মার্কসবাদী সাহিত্যিকদেরও পরিবর্তন ঘটে। তারা জীবিকার উন্নতি ও নিরাপত্তার সঙ্গে সৎভাবেই সাহিত্যভাবনা এবং শিল্পশরীরের রূপান্তর করলেন। কেউ হলেন ফ্রয়েডে আশ্রয়ী কেউ-বা স্বল্পভাষী, কেউ-বা আত্মগোপন করলেন রোমান্টিক স্বপ্নলোকে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে।
সে কারণে, শাসকবর্গের প্রতিরোধ সত্ত্বেও এ-পর্যায়ের উপন্যাসে রোমান্টিকতা, সংক্ষোভ, প্রতিবাদ, ইতিহাস- অন্বেষা, আত্ম-আবিষ্কারের প্রচেষ্টা প্রভৃতি যেমন বিদ্যমান, তেমনি স্বপ্নময় জীবনকল্পনা এবং ভাবলোক-বহুলোকের দ্বন্দ্ব-সংঘাত উদ্ভূত স্ববিরোধ থেকে আত্মমুক্তির আকাঙ্ক্ষার পলায়নবৃত্ত রচনার প্রবণতাও হল সুস্পষ্ট। বায়ান্নর রক্তাক্ত উজ্জীবন যে-সব ঔপন্যাসিকের চেতনার সংরক্ত আবেদন নিয়ে প্রকাশ পেয়েছিলো আয়ুরী দশকের সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ে তাঁদের অধিকাংশের মধ্যেই সৃষ্টি হয় আত্মমুখী প্রবাহ স্রোত।
১৯৬২-র ছাত্র আন্দোলন, পাক-ভারত যুদ্ধ (১৯৬৫), ছয়দফা কর্মসূচি, তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান প্রভৃতি ঘটনা জাতীয় জীবনে নবউদ্দীপনা সঞ্চারে সক্ষ হয়। ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন অংশত ও সাময়িক সাফল্য অর্জন করলেও স্বাধিকারকামী বাঙালি তারুণ্য গোড়া থেকেই পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে ।

ছাত্রসমাজের অগ্রগামী ভূমিকা প্রতিটি আন্দোলনকেই ইতিবাচক লক্ষ্যের দিকে ধাবিত করে। অপরপক্ষে, ১৯৪৮ ও ১৯৫২-র প্রতিবাদী মধ্যবিত্ত এ-পর্যায়ে অনেক বেশি সচেতন ও সংঘবদ্ধ ছিল। পাকিস্তানি জাতিশোষণ ও শ্রেণীশোষণের স্বরূপ তাদের কাছে অধিকতর স্পষ্ট ছিল। নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব বাংলা পশ্চাৎপদ হলেও শিক্ষার প্রসারের ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল বহুগুণে।
বাঙালি স্বাধীন পুঁজি বিকাশের ধারণাটিও এ পর্যায়ে একটি জাতীয় ইস্যুতে পরিণত হয়েছিল। পাঞ্জাবি বেনিয়া পুঁজিবাদী শক্তির সঙ্গে নবোদ্ভূত বাঙালি পুঁজির দ্বন্দু ১৯৫৪ সালে প্রথম গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রকাশ পেলেও, শ্রেণীগত দিক থেকে অশক্ত ও রাজনৈতিকভাবে অসংবন্ধ থাকার ফলে তার সাফল্য হয় বাধাগ্রস্ত। ছয়দফা কর্মসূচি জাতির স্বাধিকারের ব্যাপারটিকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ করে, তেমনি, বাঙালির স্বাধীন বিকাশের স্বরূপ প্রসঙ্গেও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করে।
১৯৬৯-এর গণ- অভ্যুত্থান পাকিস্তানের শাসনযন্ত্রের ভিত্তিকে যেমন দুর্বল করে দেয়, তেমনি প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক সংগঠন স্বাধীনতার ধারণাকে বস্তুনিষ্ঠ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পর্যায়ে নিয়ে আসে। ছাত্রসমাজের ১১-দফা আন্দোলন বাঙালির স্বাধীনতার সংগ্রামে সঞ্চার করে গতিশীল প্রাণাবেগ। ১৯৭০-এর গণতান্ত্রিক সাফল্য একটি স্বাধীন জাতিসত্তার অভ্যুদয়কে অনিবার্য লক্ষ্যের দিকে চালিত করে।
১৯৫৮-৬৮ কালপর্বে সামরিক একনায়কতন্ত্রের ভয়াল নখর আসলে শিল্পীর স্বাধীনতার জন্য যে পূর্বশর্ত, সেই স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে সর্বাংশে ধ্বংস করতে চেয়েছিল দমন পীড়ন ও অত্যাচানের মাধ্যমে। ১৯৬৯-এ গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেই আগ্রাসী একনায়কতন্ত্রের ভিত্তিই কেবল বিপর্যস্ত হলো না, নব্য-উপনিবেশবাদের জাতিক আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের স্বরূপও উন্মোচিত হয়েছিল জাতীয় চৈতন্যে। উপনিবেশ, সামরিক শাসন ও গণতন্ত্র যে একসঙ্গে চলতে পারে না, সত্তরের গণতান্ত্রিক বিজয় ও একাত্তর সালে সংঘটিত ঘটনাপুঞ্জ তার জ্বলন্ত প্রমাণ।
১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধ বাঙালির জাতীয় জীবনে অপরিমেয় ত্যাগ, প্রতিবাদ, বিক্ষোভ ও সাফল্যের সূর্যোদয়ে গৌরবময়। ইতিহাসের যে দ্বন্দুময় ও গতিশীল ধারা পলাশীর বিপর্যয় (১৯৫৭), সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭), কংগ্রেস-মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বিভেদের রাজনীতি, পাকিস্তান আন্দোলন, ১৯৪৭-এর অসঙ্গত রাজনৈতিক মীমাংসা, ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান প্রভৃতি ঘটনাক্রমের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ছিল সেই ঐতিহাসিক নিয়মেরই চরম পরীক্ষা।
জাতির সামগ্রিক অস্তিত্বের প্রশ্নে জনগোষ্ঠী এক বিন্দুতে মিলিত হয়েছিল এই যুদ্ধে। এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি আর্থ- সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে করতলগত করে। সুদীর্ঘকালের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ ও নিপীড়নের ফলে জাতির সৃষ্টিশীল চেতনায় যে ক্ষোভ, প্রতিবাদ, সংগ্রামশীল জীবনদৃষ্টি এবং ভবিষ্যতস্পর্শী কল্পনার জন্ম হয়েছিল, যুদ্ধের রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা ও সাফল্যে তার গঠনমূলক রূপান্তরের পথ সুপ্রশস্ত হয়েছিল।
স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধোত্তরকালে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক কাঠামোতে গুণগত পরিবর্তন প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু সেক্ষেত্রে রক্তাক্ত যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ জাতীয় জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তনের গতি অল্প কিছুকালের মধ্যেই হয়ে পড়ে অবরুদ্ধ।
স্বাধীনতা উত্তরকালে কেবল পরিমাণগত পার্থক্য ছাড়া বাংলাদেশের সমাজ-কাঠামোতে তেমন কোন গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়নি। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতা জাতির চিন্তা-চেতনায়, মন ও মননে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাদের প্রত্যাশার দিগন্তকে করেছিল সুবিস্তৃত। কিন্তু যুদ্ধোত্তর কয়েক বছরের মধ্যেই জাতীয় চৈতন্যে পরাজয় ক্লিষ্টতা প্রকাশ পেতে থাকে।
মূল্যবোধের স্তম্ভগুলো যেন খসে পড়তে থাকে। গণতন্ত্র হয়ে ওঠে সমরাস্ত্র শাসিত; জাতিশোষণ রূপান্তরিত হয় শ্রেণীশোষণে। সহস্র কোটিপতির রসদ সরবরাহে আমাদের অস্তিত্বমূল শুকিয়ে যায়। রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হয় ছিন্নমূল সব ভাড়াটে কুশীলবের দল। তাদের ছদ্মবেশের আড়ালে দেখা যায় অতীত কংকাল। জাতীয় অস্তিত্বের এই বিবর্ণ পটভূমিতে, ঔপন্যাসিকের চেতনালোক হয়ে পড়ে রক্তাক্ত। এই রক্ত রঞ্জিত, হতাশায় ব্যর্থতায় ক্ষতবিক্ষত এবং সংগ্রামশীল জীবনদৃষ্টিতে প্রত্যাবর্তন ১৯৪৭-১৯৭১ পর্যন্ত ও ‘৭১ পরবর্তী বাংলাদেশের উপন্যাসে লক্ষ করা যায়।
বস্তুত বিভাগোত্তর বাংলাদেশ ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত হবার ফলে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র 3 মানবতাকামী চৈতন্য নিক্ষিপ্ত হয় এক অন্ধকার সমাজ গহ্বরে, যেখানে ধর্মাদর্শের প্রশ্ন তুলে বাংলাদেশকে শৃঙ্খলিত করা হয় পাকিস্তানের নয়া ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামোতে। সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণ রূপান্তরিত হয় জাতিশোষণ ও শ্রেণীশোষণের জটিল প্রক্রিয়ায়। জাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও মানবীয় সম্পর্ক বিষয়ে নতুন ব্যাখ্যাদানেরও চেষ্টা হয়।
ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক বিকাশসূত্রে যে গুণগত পরিবর্তন প্রত্যাশিত ছিল, বাঙালি জীবনে তার প্রতিষ্ঠা হয় বাধাগ্রস্ত। দাঙ্গা, মহামারী, দারিদ্র্য, উদ্বাস্তু সমস্যা, নিপীড়ন, সংস্কৃতি বিলোপের চেষ্টা প্রভৃতি বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীকে নিক্ষেপ করে গভীর সংকটাবর্তে। উক্ত আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাস্তবতায় রাষ্ট্র ও সমাজ বিন্যাসের নতুন রূপ এবং অস্তিত্বের নবতর জিজ্ঞাসায় বিভাগোত্তর বাংলাদেশের উপন্যাসের বিষয় উৎস এক স্বতন্ত্রমাত্রা লাভ করে।
তাই বিভাগোত্তর উপন্যাস থেকে আমরা বাংলাদেশের সমাজ- মানস ও ব্যক্তিমানসের বৈচিত্র্য ও গভীরতাকে স্পর্শ করতে পারি। যেখানে জাতিশোষণের তীব্র সংঘাত ও সংগ্রামের পাশাপাশি শ্রেণীশোষণের পরিচয় তীব্র হয়ে উঠেছে। ফলে সমাজ ও জীবনের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে উপন্যাসের উপকরণ ও বিষয় চেতনায় তার স্বরূপ প্রতিফলিত হয়েছে।