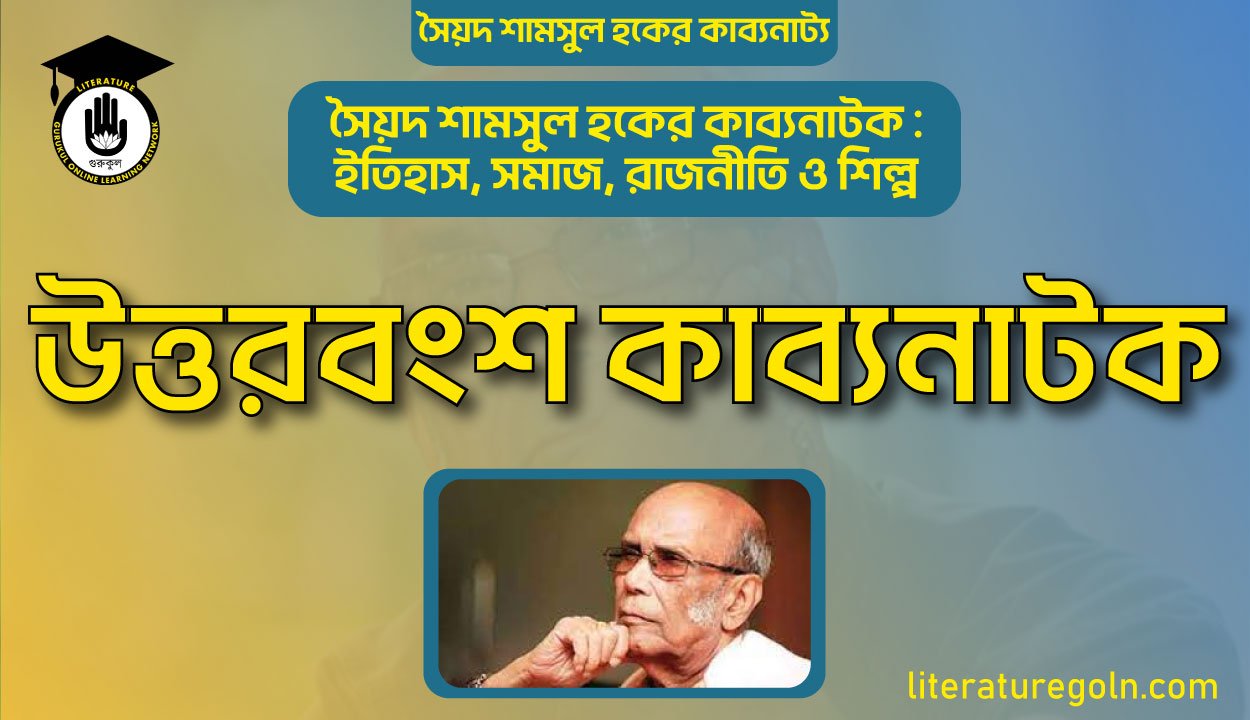আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়ঃ উত্তরবংশ কাব্যনাটক। যা সৈয়দ শামসুল হকের রাজনীতি আশ্রিত কাব্যনাটক এর অন্তর্গত।

উত্তরবংশ কাব্যনাটক
শক্তিমান কবি-নাট্যকার-কথাসাহিত্যিক সৈয়দ শামসুল হক একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক, কলম-যোদ্ধা। দেশের যেকোনো সংকটে তাঁর নির্ভীক লেখনী জাতিকে সাহস ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। রাষ্ট্রযন্ত্রের চোখরাঙানি, জঙ্গিবাদী গোষ্ঠীর হুমকি, নেতিবাচক সমালোচনা, নিন্দা কিছুই তাঁকে সত্য ও সুন্দরের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। তিনি কখনো কোনোকিছুর বিনিময়ে তাঁর বিবেচনাবোধ ও শৈল্পিক নিষ্ঠার সঙ্গে আপস করেননি।
একারণেই তাঁর সমগ্র কাব্যনাটকে মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ, রাজাকারদের ভূমিকা, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড, সুবিধাবাদী স্বৈরশাসক, অসাধু রাজনীতিক প্রসঙ্গ বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। এসবের প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর সর্বশেষ কাব্যনাটক উত্তরবংশে (২০০৮)। এখানে তিনি সমকালীন রাজনীতি, সমাজনীতি, মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ উপস্থাপনের সমান্তরালে ১৯৭১ সালের মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গটি অত্যন্ত স্পষ্টাকারে শিল্পরূপ দিয়েছেন ।
তিনি যে সময়পরিসরে এই নাটক লিখেছেন, সে-সময় এদেশের রাজনীতিতে চলছে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক শক্তির দাপট; রাষ্ট্রযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করছে সমরশক্তি, চলছে ছদ্ম সামরিক শাসন। এর পূর্বে চারদলীয় জোট সরকারের আমলে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তি মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হয়ে বীরদর্পে তাদের গাড়িতে উড়িয়েছে লাল-সবুজের পতাকা।
একদিকে জঙ্গিবাদের উত্থান, বাক-স্বাধীনতা হরণ, সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন, প্রগতিশীল রাজনীতিকদের দমন-পীড়ন-গ্রেফতার, বোমা-গ্রেনেড হামলা, অন্যদিকে মানবতাবিরোধী রাজাকার- আলবদরদের বিচারহীনতার সংস্কৃতি সমাজকে অন্ধকার ও হতাশার দিকে ঠেলে দিয়েছে। সেই মজ্জমান, অবরুদ্ধ রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক দৃঢ় কণ্ঠে একাত্তরের ঘাতক দালালদের বিচার চেয়েছেন।
জনগণকে তাদের অতীত ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার আহবান জানিয়েছেন তিনি। ‘দেশমাতা আর মাতৃভাষার প্রতি নিবিড় শ্রদ্ধাশীল এই শিল্পী-প্রতিভা বরাবরই সত্য আর বর্তমানের জিজ্ঞাসা রূপায়ণে নিষ্ঠাবান। ইতিহাস-ঐতিহ্য তাঁর সাহিত্যবোধের একটি প্রধান অনুষঙ্গও।
উনিশশ’ একাত্তর, পাকিস্তান-বাংলাদেশ প্রসঙ্গ, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব অর্জনের সংগ্রাম, প্রতিকূলতা-অনতিকূলতা, বিপরীত স্রোতের মানুষ, সৃজনশীল সমাজের প্রত্যাশা-প্রচেষ্টা, বিবর্ণতা আর আনন্দ- বিষণ্নতার গল্প সৈয়দ শামসুল হকের কবিতানাট্য উত্তরবংশ। […] একজন নাট্যকার, তার কন্যা, আর তার এক রাজনীতিক বন্ধুকে ঘিরে মূলত আবর্তিত হয়েছে উত্তরবংশ কাব্যনাট্যের ক্যানভাস।
তাদের আলাপচারিতায় নির্মিতি লাভ করেছে স্বাধীনতা-পরবর্তী বর্তমান বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি, আমাদের প্রকৃত অর্জন, সাফল্য ব্যর্থতা। পাশাপাশি লেখক-উপস্থাপন করতে চেষ্টা করেছেন ব্যর্থতার কারণ আর বাতলে দিয়েছেন এ থেকে উত্তরণের পথ।
বস্তুত, ‘আবহমান বাংলা ও বাঙালির অন্যতম সেরা ভাষাশিল্পী, সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক। […] চিরকাল মানুষকে তিনি স্থান দিয়েছেন আর সবকিছুর উপরে। বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধ ও দেশের ইতিহাস তিনি ধারণ করেছেন মর্মে মর্মে। তাঁর শিল্পিমানসের এই বৈশিষ্ট্যই প্রতিফলিত হয়েছে উত্তরবংশ নাটকে। এ-প্রসঙ্গে উত্তরবংশ নাটকের নির্দেশক গোলাম সারোয়ার বলেছেন :
মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী দেশের সব মানুষ আরেক যুদ্ধ করে চলেছে বাংলাদেশের ভেতরে যুদ্ধাপরাধী ও মানবতাবিরোধীদের বিচারের দাবি নিয়ে। কালের পরিক্রমায় এই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে এগিয়ে আসে নতুন প্রজন্ম। এমনই একটি বিষয়ের উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার তাঁর উত্তরবংশে।

সৈয়দ শামসুল হক বর্তমান প্রজন্মের মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধাপরাধের গুরুত্ব অনুধাবন যে কতটা জরুরি সে প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করেছিলেন একটি সাক্ষাৎকারে । তিনি এক সাক্ষাৎকারে এ প্রসঙ্গে বলেছেন :
এই যে বাংলাদেশ যুদ্ধের ভেতর দিয়ে এসেছে। গণতন্ত্র বিকৃত হয়েছে এখানে। আবার গণতন্ত্র ফেরত এসেছে, আবার বিকৃত হয়েছে। এই যে সময়কাল, এর ভেতর মানুষের প্রতিক্রিয়া পাল্টেছে। এই পাল্টানোর মাঝে একটা সাধারণ প্রবণতা আছে। এর মাধ্যমে মানুষের মূল্যবোধ পরীক্ষিত হয়। সত্য কথা বলা উচিত, সত্য পথে চলা উচিত – এটা আগেও যেমন সত্য ছিল, এখনও আছে। কিন্তু রিঅ্যাকশন পাল্টাচ্ছে সময়ের উপর নির্ভর করে।’
মূলত, যুদ্ধাপরাধী এবং মানবতাবিরোধী অপরাধীদের প্রশ্নে নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক বরাবরই আপসহীন এবং সোচ্চার ছিলেন। ২০০৬ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধসংকলন কথাসামান্যই-এর ‘না’ প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন :
একাত্তরে পাকিস্তানি বাহিনীর কৃত বাংলার মাটিতে নৃশংসতম গণহত্যার বিরুদ্ধে বাঙালি বলে উঠেছিল না না না, জন্ম নিয়েছিল মুক্তিযোদ্ধা। বাংলার এই মাটিকে তারা মুক্ত করেছিল পাকিস্তানের দ্বিজাতিতত্ত্বের বুকে লাথি মেরে, ধর্মের ভিত্তিতে মানুষ বিচারকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, শোষণের বিরুদ্ধে উত্থানের দেহ ধরে।
সেই বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধের জাতক সেই আমাদের বাংলা, তিরিশ লাখ শহীদ আর বঙ্গবন্ধুর বুকের রক্তভেজা বাংলা, এই বাংলায় আমরা কি আরেকবার বলে উঠব না? – না না! না, আমরা ইতিহাস বিকৃতি মেনে নেবো – না। না, আমরা গণতন্ত্রের নামে না-গণতন্ত্র মেনে নেব না। শাসনের নামে না-শাসন আর সইব না। বিচারের নামে প্রহসন আর চলতে দেব না। অধিকারের নামে অধিকার হরণ আর চলবে না। ধর্মের নামে মানুষকে ভয় দেখানো চলবে না। ধর্মের ভিত্তিতে মানুষকে ভাগ করা চলবে না।
মানুষকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করা চলবে না। রাজাকারকে বাংলার মন্ত্রী বানানো আর হতে দেব না। রাজাকারের গাড়িতে বাংলাদেশের রক্তসূর্য খচিত পতাকা আর উড়তে দেব না। একাত্তরের যুদ্ধাপরাধের বিচার ভিন্ন আমরা শান্ত হব না।`
বলা যায়, সৈয়দ শামসুল হক তাঁর সর্বশেষ কাব্যনাটক উত্তরবংশ রচনা করেছেন একটি বিশেষ সময়ের প্রেক্ষাপটে, বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। স্বাধীনতার দীর্ঘকাল পরেও যখন এদেশের মাটিতে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের উপযুক্ত বিচার সম্ভব হচ্ছিল না, বরং একাত্তরের কালোশক্তি এদেশের কিছু প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থান্ধগোষ্ঠী দ্বারা পুর্নবাসিত হয়ে রাষ্ট্রক্ষমতায় চড়ে বসেছিল, দেশবাসীর অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধকে হরণ করে ধর্মান্ধতা চাপিয়ে দিচ্ছিল, তখন সৈয়দ শামসুল হক নাটকটি রচনার মাধ্যমে একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিকের মতোই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন।
এখানে যেমন তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংস অত্যাচারের কাহিনি বর্ণনা করেছেন, তেমনি রাজাকার-আলবদর-আলশামস বাহিনীর ঘৃণ্য ভূমিকার চিত্রাঙ্কন ইতিহাস-বিকৃতির মধ্যে বেড়ে ওঠা নবীন প্রজন্মকে সঠিক ইতিহাস জানাতে চেয়েছেন। তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাধ্যমে স্বপ্ন দেখেছেন এদেশে মানবতাবিরোধী অপরাধীদের উপযুক্ত বিচার হবে, বিচার হবে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের।
একথা সত্য যে, সৈয়দ শামসুল হকের জীবদ্দশায় তরুণপ্রজন্মের আন্দোলনের মাধ্যমে এ দুটি স্বপ্ন সত্যি হয়েছে।
এদেশের আদালত যখন একাত্তরের রাজাকার কাদের মোল্লার ঘৃণ্য অপরাধের বিচারে মাত্র যাবজ্জীবন শাস্তি দিয়েছে, তখন এদেশের তরুণ ছাত্র সমাজ ক্ষোভে, দ্রোহে ফেটে পড়েছে। তারা গণজাগরণ মঞ্চ নির্মাণ করে এ রায়ের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে।
নব্বইয়ের দশকে শহীদজননী জাহানারা ইমাম যে আন্দোলন শুরু করেও রাষ্ট্রিক বিরোধিতার যাঁতাকলে পড়ে থেমে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, এবারের উত্তরপ্রজন্ম আর থেমে থাকেনি; তাদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত নতুন করে রায় বিবেচনা করেছে; পৃথক ট্রাইবুনাল গঠন করে দেশের সর্বোচ্চ আদালত কাদের মোল্লাসহ অন্যান্য যুদ্ধাপরাধীর ফাঁসির রায় প্রদান করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে জাতির জনকের খুনীদেরও বিচার করা সম্ভব হয়েছে। দেশ হয়েছে পিতৃহত্যার কলঙ্ক থেকে মুক্ত।
২০০৮ সালে উত্তরবংশ নাটকের মাধ্যমে সৈয়দ শামসুল হক যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, অনতিকাল পরেই সেটি সত্যে পরিণত হয়েছে। একজন ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা শিল্পীর মতোই সৈয়দ শামসুল হক যেন এই ভবিষ্যৎ দেখতে পেরেছিলেন। নাটকের নামকরণ থেকেই সুষ্পষ্ট হয় – অতীতে পূর্বপুরুষের কৃত ভুলের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসার এবং উত্তরপ্রজন্মকে সচেতন করে তুলতেই তিনি উত্তরবংশ নাটক রচনা করেছেন। উদাত্ত কণ্ঠে তিনি আহবান করেছেন :
ক্ষমা নেই, ক্ষমা নেই ঘাতকের।
ক্ষমা নেই দালালের।
ক্ষমা নেই ধর্ষকের।
[…] যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার করো ।
সভ্যতা তোমাদের ডাক দিচ্ছে।
ইতিহাস তোমাদের আহবান করছে।
দেশমাতৃকা তাকিয়ে আছে।
আর কতকাল তোমরা নিষ্ক্রিয় নীরব থাকবে?
[…] আর কতকাল আমাদের অপেক্ষা করতে হবে –
একটি বিচারের জন্যে ? | কাব্যনাট্যসমগ্র (৬০৫)
মুক্তিযুদ্ধকে অবলম্বন করে সব্যসাচী লেখক সৈয়দ হক অসংখ্য সাহিত্য রচনা করেছেন। কিন্তু তিনি যখনই কোন বিশেষ বক্তব্যের সঙ্গে একটি বৃহৎজনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করতে চেয়েছেন তখনই কাব্যনাটকের আশ্রয় নিয়েছেন। পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়, নূরলদীনের সারাজীবন নাটকে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে প্রান্তিক মানুষকে সম্পৃক্ত করা।
যে কারণে এ-দুটি নাটক শহুরে শিক্ষিত শ্রেণির দর্শককে ছাপিয়ে গণমানুষের নাটকে পরিণত হতে পেরেছে। সৈয়দ শামসুল হক যখন মনে করলেন একাত্তরের ঘাতক- দালালদের বিচারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারছে না; বরং প্রগতিশীল কণ্ঠকে রুদ্ধ করে দিতে সমাজে মৌলবাদের উত্থান ঘটছে, জঙ্গিবাদ, বোমাহামলা, মুক্তচিন্তকের ওপর আঘাত বেড়ে চলছে, এবং এ বিষয়ে নেতা-বুদ্ধিজীবীরা যখন উপযুক্ত আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হচ্ছে, তখন মানবতা বিরোধীদের সঠিক বিচারের নিমিত্তে উত্তর প্রজন্মকে এর সঙ্গে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। আর সে কারণেই প্রথমত তাদের প্রয়োজন মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানা।
কেননা পঁচাত্তর-উত্তর সময়ে এদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত হতে হতে একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে। এ নাটকের উদ্বোধনী প্রদর্শনীতে দেয়া এক বক্তব্যে সৈয়দ শামসুল হক নাটকটির বিষয়বস্তু নিয়ে নিম্নরূপ মন্তব্য করেন :
পাঁচ বছর আগে যখন এই নাটকটি লিখি, তখন এর বিষয়বস্তু যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তেমনি এখনো সমান গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধাপরাধী ও মানবতাবিরোধীদের বিচারের দাবী নিয়েই এই নাটক।’
উত্তরবংশ কাব্যনাটকের বিশাল একটি অংশজুড়ে রয়েছে বীরাঙ্গনা নারীকে অশ্রদ্ধার মাধ্যমে প্রগতিশীল সমাজকে হেয় করার হীন রাজনৈতিক চক্রান্তের চিত্র। সেইসঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে ১৯৭১ সালের প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ প্রসঙ্গ। এমনকি নাটকের মূল ঘটনাটিই নারী নির্যাতনের বাস্তব ঘটনাকেন্দ্রিক।
নাটকের অন্যতম নেপথ্য চরিত্র নাট্যকারের স্ত্রী ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদারদের লালসার শিকার হয়ে দীর্ঘকাল ক্যাম্পবন্দি ছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর হানাদারদের ক্যাম্প থেকে মুক্তি পেলেও আত্মগ্লানি ও বিবেক দংশন থেকে তিনি এখনও মুক্ত হতে পারেননি। ফলে ক্যাম্প থেকে ফিরে নাট্যকারের সঙ্গে স্বাভাবিক দাম্পত্যসম্পর্ক তৈরিতে প্রতিমুহূর্তে জটিলতার মুখোমুখি হতে হয়েছে তাঁকে।

তবে নাট্যকারের দুর্মর ভালোবাসা আর অকুণ্ঠ সমর্থন তাকে কিছুটা স্বাভাবিক জীবন এনে দেয়। যার ফলে তাদের কোল জুড়ে আসে পরির মতো কন্যা সন্তান। অতঃপর দিনবদলের সঙেগ সঙ্গে রাষ্ট্রের অবস্থাও বদলে যেতে শুরু করেছে। যে আশা ও উদ্দেশ্য নিয়ে এদেশের লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সেই আশা-আকাঙ্ক্ষাও ফিকে হতে শুরু করেছে।
১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকের বুলেটে বঙ্গবন্ধুর ক্ষতবিক্ষত শরীরের মতোই ঝাঁঝরা হতে শুরু করেছে রাষ্ট্রের শরীর। রাষ্ট্রপরিচালনায় ততদিনে গণতন্ত্রের স্থানে জায়গা করে নিয়েছে স্বৈরতন্ত্র। রাষ্ট্রের চার মূলনীতিকে বৃদ্ধাঙ্গলি দেখিয়ে দেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দেশময় চর্চা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে জাতিসত্তার পরিচয়জ্ঞাপক অনুষঙ্গরূপে বেছে নেয়া হয়েছে। সমাজে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অরাজকতার প্রসার ঘটে চলেছে।
অন্যদিকে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব করে প্রকৃতপক্ষে জনগণের মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকেই গলাটিপে হত্যা করা হয়েছে। সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে তখন, যখন এদেশে সশস্ত্র স্বাধীনতাবিরোধীদের ফিরিয়ে এনে নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়েছে। যারা বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছে, তাদের হাতে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।
রাষ্ট্রের সর্বপর্যায়ে এই বিপর্যয় প্রত্যক্ষ করে নাট্যকারের স্ত্রী হয়ে পড়ছেন বিস্ময়ে বিমূঢ়, তীব্রভাবে হতাশাগ্রস্ত। তাঁর মানসলোকে ভেসে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি হানাদারদের ক্যাম্পে নির্যাতিত হওয়ার সেই দুঃসহ স্মৃতি। নাট্যকারের স্ত্রীর হৃদয়ে ক্যাম্পে নির্যাতিত হওয়ার পুরাতন ক্ষত বার বার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তিনি নিজের সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়েও অত্যন্ত শংকিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। তাঁর উদ্বিগ্ন অবস্থাসূত্রে নাট্যকার তাঁর মেয়েকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন :
ততদিনে জাতির জনক নিহত,
মানুষের হাত থেকে ছিনতাই হয়ে গেছে রাষ্ট্রের ক্ষমতা,
শুরু হয়েছে স্বৈরশাসন, রাজাকারের পুনর্বাসন।
ঘাতকদের দালাল দোসরদের ডেকে আনা হলো –
অভয় দেয়া হলো তাদের। তারা জাঁকিয়ে বসলো মাঠ।
আমাদের যুদ্ধের ইতিহাসকে তারা মুছে দিলো ।
আমাদের সংবিধানকে তারা হত্যা করলো।
একাত্তরের বিজয় পরিণত হয়ে গেলো পরাজয়ে।
তোকে কোলে পেয়ে আরো অস্থির হয়ে পড়লো তোর মা
আতংক তার মনের মধ্যে লাফিয়ে উঠলো দ্বিগুণ দশগুণ ।
একেক রাতে কোল থেকে তোকে আছাড় দিয়ে ফেলে
তোর মা চিৎকার করে উঠতো – […]
এই শিশুকেও একদিন ছিঁড়ে খাবে! […]
কিছুতেই ভুলতে পারতেন না বাংকারেরর সেই দোজখ। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৬০০ )
পরিবর্তিত সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পরিস্থিতি নাট্যকারের স্ত্রীকে এতটাই বিধ্বস্ত ও এলোমেলো করে দেয় যে, তিনি নিজের তিন বছরের শিশু কন্যাকে রেখে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহননের পথ বেছে নেন তিনি। নাট্যকার মুক্তিযুদ্ধকালে নারী নির্যাতন প্রসঙ্গটি তাঁর প্রথম কাব্যনাটক পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়-এও উল্লেখ করেছিলেন।
সে কাব্যনাটকের প্রধান নারী চরিত্র মাতবরের মেয়েটিও পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন কর্তৃক ধর্ষিত হয়ে আত্নগ্লানি আর হতাশায় জনসম্মুখে বিষপানে আত্নহত্যা করে। নাট্যকারের স্ত্রীর শঙ্কা যে অমূলক ছিল না তা পঁচাত্তর-উত্তর বাংলাদেশে বার বার প্রমাণিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যখনই এদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে, তখনই ঘটেছে নারী নির্যাতনের মতো অপ্রত্যাশিত ঘৃণ্য ঘটনা।
১৯৯১ সালে অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে চট্টগ্রামে ব্যাপক নারী নির্যাতনের চিত্র দেখে বঙ্গবন্ধু কন্যা যে মন্তব্য করেছিলেন, তাতে উত্তরবংশের নারী চরিত্রের শংকাকে সত্যভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে। ১৯৯১ সালে লেখা ব্যক্তিগত দিনলিপিতে তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা লিখেছিলেন :
১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার সেনাবাহিনী মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বিভিন্ন ক্যাম্পে বাঙালি মেয়েদের বন্দি করে রেখেছিল এবং তাদের উপর নির্যাতন চালাত। […] ১৬ ডিসেম্বর মিত্রবাহিনীর কাছে হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে যখন সেই নারীদের উদ্ধার করা হয়েছিল, তখন তাদের যে চেহারা আমরা দেখেছিলাম, আমার আজকের চট্টগ্রামকে দেখে সেই ধর্ষিতা বিবস্ত্রা নারীদের কথাই বারবার মনে পড়ছে। একমাত্র তাদের সাথেই আজ চট্টগ্রামের তুলনা করা চলে।’
১৯৭১ সালে যে-সকল মা বোন ধর্ষিত হয়ে আত্মগ্লানিতে ভুগে আত্মহত্যা করেছেন, তাদের মর্মান্তিক পরিণতির মতোই যন্ত্রণাদায়ক ছিল যারা বেঁচে থেকে ক্রমাগত নিজের সঙ্গে যুদ্ধে নেমেছিলেন বেঁচে থাকার লড়াইয়ে। তাদের প্রত্যাশা করেছিলেন স্বাধীন রাষ্ট্রে এই ধর্ষকদের বিচার হবে। কিন্তু তারা অত্যন্ত আশাহত চিত্তে দেখেছেন যে, রাষ্ট্র এই অপরাধীদের বিচার করার পরিবর্তে ডেকে এনে রাষ্ট্রক্ষমতায় বসিয়েছে।

স্বাধীন দেশে বীরাঙ্গনাদের প্রকৃত সম্মান দেওয়া হয়নি; বরং তাদের নামের তালিকা মুছে ফেলা হয়েছিল এই ভেবে যে, তাদের আলাদা কোনো পরিচয় না থাকাই তাদের জন্য মঙ্গলজনক। অত্যন্ত গোপনে, নিভৃতে এসকল বীরাঙ্গনারা অতীত স্মৃতি বুকে চেপে দিনাতিপাত করে গেছেন।
নীরবতা ভেঙে যদি দু-একজন নিজের অত্যাচারের কাহিনি বর্ণনা করে সমাজে এসকল অপরাধীর বিচার চেয়েছেন, তারাই হয়েছেন ধিকৃত, হাসিঠাট্টার পাত্র। নব্বইয়ের দশকে যখন জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে জনতার আদালতে রাজাকারদের প্রতীকী বিচারকার্য পরিচালিত হয়, তখন প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে দুজন নির্যাতিত নারী এসেছিলেন একাত্তরের মানবতাবিরোধীদের বিচার চেয়ে সাক্ষ্য দিতে।
এরপর তারা যখন নিজ ঠিকানায় প্রত্যাবর্তন করেছেন, তখন তাদের সামাজিক ভাবে হেনস্থা হতে হয়েছে। সে-সময়ে গণআদালতের একজন উদ্যোক্তা, শাহরিয়ার কবির সেই ঘটনা সম্পর্কে এক লেখায় জানিয়েছেন :
শহীদ জননী জাহানারা ইমামেন নেতৃত্বে “৯২-এর ২৬ মার্চ যখন গণআদালতে যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের বিচার হয় – কুষ্টিয়া থেকে তিনজন বীরাঙ্গনা ঢাকা এসেছিলেন সাক্ষ্য দিতে। তখন বিভিন্ন দৈনিকে তাঁদের কথা লেখা হয়। এঁরা তিনজন গ্রামে ফিরে নিজেদের আবিষ্কার করেন একরকম একঘরে অবস্থায়। লোকজন তাদের বিভিন্নভাবে বিদ্রূপ করেছে। তাঁদের জীবনে নেমে এসেছে আরেক বিড়ম্বনা।
একাত্তরের নির্মম ক্ষত আবার তাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণের কারণ হয়েছে। তারা যতদিন বেঁচে থাকবেন এ রক্তক্ষরণ বন্ধ হবে না। তাঁদের একজন ক্ষেভের সঙ্গে বলেছেন, বিচারের আশায় অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে ঢাকায় ছুটে এসেছিলেন। আজ অবধি তাঁরা বিচার পাননি অথচ প্রতিনিয়ত গঞ্জনার শিকার হচ্ছেন।
সৈয়দ শামসুল হক তাঁর উত্তরবংশ নাটকে ১৯৭১ সালে বেঁচে যাওয়া ধর্ষিত নারীর যে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক নিগ্রহ ও রক্তমোক্ষণের তীব্র যন্ত্রণা তা নাট্যকারের স্ত্রীর যন্ত্রণার সঙ্গে সমীকৃত করে এ-নাটকে নাট্যরূপ দিয়েছেন। নাট্যকারের বন্ধু, জনৈক নেতা যখন নাট্যকারের স্ত্রীর হতাশা ও প্রাক-আত্মহন পর্বের তীব্র মানসিক দহনের কথা উল্লেখ করে বলেন – তোমার স্ত্রী বেঁচে ছিলেন তারপরও বারোটি বছর – / একবার মনে করে দ্যাখো কতটা আগুন নিয়ে দিন কেটেছে তাঁর’ – তখন তার প্রত্যুত্তরে নাট্যকার জানান : –
সেই বন্দীশালা থেকে তার ফিরে আসবার পরে,
আমি জানি, চোখেই আমি দেখেছি কী তার দহন!
আর আমার অবিরাম চেষ্টা তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফেরাতে।
ফেরাতে যে পারিনি – প্রমাণ তার আত্মহত্যা। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৭২)
সৈয়দ শামসুল হক তাঁর প্রথম কাব্যনাটক পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়-এ বিনষ্ট রাজনীতির কবলে-পাড়া জনগণের দুর্দশার চিত্র এঁকেছিলেন। সেখানে গ্রামবাসী প্রশ্ন করেছিল, ‘খুনি কে?’ ১৯৭৫ সালে নাট্যকারের লেখা এই প্রশ্নের জবাব সৈয়দ শামসুল হক তাঁর সর্বশেষ কাব্যনাটকে এসে যেন দিয়ে দিলেন। এখানে নেতা অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন – রাষ্ট্রিক ও সামাজিক এই বিপর্যয়ে কালোশক্তির সক্রিয়তা যেমন দায়ী, তেমনি সমান দায় আছে এদেশের জনগণ, , বিশেষত রাজনীতিবিদদের।
কেননা যে প্রবল বিক্রমে এদেশের প্রগতিশীল রাজনীতিবিদগণ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, নেতৃত্ব দিয়েছিলেন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে, তারাই পরবর্তী সময়ে নিজেদের আদর্শ, নীতি ব্যক্তিগত স্বার্থের কাছে জলাঞ্জলি দিয়েছেন। এদের কেউ কেউ অপশক্তির সঙ্গে জোট বেঁধে ক্ষমতায় বসার পাঁয়তারা করেছেন, আবার কেউবা নির্লিপ্ত থেকে সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যথাযথ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছেন।
অন্যদিকে জনগণও স্রোতের মুখে গা ভাসিয়ে দিয়ে নিশ্চুপ থেকেছেন; ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তায় মগ্ন জনগণ রাষ্ট্রিক বিনষ্টি ও অধোগতির কথা একবারও ভাবেননি। স্ত্রীর নির্মম মৃত্যুর পরও নির্লিপ্ত থাকায় নাট্যকারকে উদ্দেশ্য করে নেতার উত্তর তাই — ধর্ষিত স্ত্রীর খুনী আসলে তারা নিজেরাই। – তারাই নীরব থেকে অন্যায়কে সমর্থন দিয়ে গেছে। অর্থাৎ এ জাতিই এ জাতির প্রকৃত হত্যাকারী। এ প্রসঙ্গে নেতার সংলাপ :
ব্যক্তিগত শোক আর দেশের জন্যে শোক – আমি আলাদা করে দেখি না ।
তুমি যদি জীবনসঙ্গী হারিয়েছো, দেশ তার রাষ্ট্রস্বপ্ন হারিয়েছে।
তুমি যদি আগুনে দেখেছো তাঁকে আত্মহত্যা করতে –
আমি এই আমাদেরই দেখছি আদর্শকে বলি দিতে। […]
আর দেশটাকে আমরা হাসতে হাসতে পঁচাপাঁকে পুঁতে ফেলেছি।
আমরাই আমাদের খুনি। আমরাই আত্মহত্যাকারী। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৮৬)
নাট্যকার পিতার মুখে নিজ মায়ের এমন করুণ ও দুঃখজনক ইতিহাস শ্রবণ করে প্রোহে-প্রতিবাদে ফেটে পড়ে নাট্যকারের মেয়ে। সে পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে, এত কিছু হয়ে যাবার পরও পিতা কেন রাষ্ট্রযন্ত্রের অন্যায়ের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রতিবাদ করেনি; বরং মাকেই বলেছে মেনে নিতে, সব কিছু ভুলে যেতে।
নিজের ঘরেই যখন সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করে আপস করার কথা বলেছে, অন্যদের মতো ভুলে যেতে চেয়েছে, সেখানে সে কীভাবে লেখনীর মাধ্যমে জনগণকে দেশপ্রেমের গান শুনিয়েছে। দেশের শিল্পী-বুদ্ধিজীবী চরিত্রের এই দ্বিমুখী ভূমিকার কারণেই এদেশে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ঘাতক-দালালরা প্রশ্রয় পেয়েছে। তারা সংঘবন্ধ হয়ে বারবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আহমদ ছফা এই দ্বিধাগ্রস্ত পোশাকি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণি সম্পর্কে এক বলেছিলেন :
যাঁরা মৌলবাদী তারা শতকরা একশো ভাগ মৌলবাদী। কিন্তু যাঁরা প্রগতিশীল বলে দাবী করে থাকেন তাদের কেউ কেউ দশ ভাগ প্রগতিশীল, পঞ্চাশ ভাগ সুবিধাবাদী, পনেরো ভাগ কাপুরুষ, পাঁচ ভাগ একেবারে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন । […] দিনে দিনে প্রতিক্রিয়ার শক্তি যে হারে সংহত হচ্ছে এবং মৌলবাদের প্রতাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তথাকথিত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা তার বিরুদ্ধে কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধ রচনাই করতে পারেননি। ১
আলোচ্য নাটকে নাট্যকারের মেয়েও ঠিক তার লেখক-পিতার দিকে একই অভিযোগ তুলে বলেছে :
বাবা, বাড়িতে সংসারে, তুমি সেই কথাই বলেছো তোমার স্ত্রীকে
যে কথা আজ শত্রুরা দিনের পর দিন বলছে।
অথচ বাইরে তুমি – এই তুমি – কলমের তুমি – সভামঞ্চের তুমি
পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় আগুন ধরিয়ে, মানুষের রক্তকে চঞ্চল করে
বক্তৃতায় মাইক ফাটিয়ে অবিরাম বলে গেছো ভুলো না, স্বদেশ!
এই তোমার আশ্চর্য বিপরীত এক দেখছি, আমি বিস্মিত হচ্ছি। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৬০১ )

নাট্যকারের মেয়ের মুখে এমন সুস্পষ্ট প্রতিবাদ আর সাহস দেখে নাট্যকারও নতুন করে প্রেরণা ফিরে পান। তাঁর অন্তসত্তায় জেগে ওঠে অনুশোচনা আর অনুতাপ। তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারেন। মেয়ে যখন তাঁকে পরামর্শ দেয়, রাষ্ট্রিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে আর লোক-দেখানো প্রতিবাদ নয়, জাতিকে এবার জেগে উঠতে হবে সত্যিকার ভাবে।
রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে ক্ষমতায় আসীন মুক্তিযুদ্ধবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী কিংবা বাংলাদেশের অলিতে গলিতে লুকিয়ে থাকা মানবতাবিরোধী অপরাধীর বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তাদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। একাত্তরে যুদ্ধ হয়েছিল দেশের সার্বিক মুক্তির, দেশ স্বাধীন হবার পর এখন নতুন করে যুদ্ধে নামতে হবে মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিরুদ্ধে। দেশকে করতে হবে কলঙ্কমুক্ত।
বস্তুত, মানবতাবিরোধী অপরাধের বিষয়টি সমগ্র বিশ্বের জন্যই একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়। যখনই বিশ্বের কোথাও যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তখনই শাসকগোষ্ঠী কিংবা অধিকতর শক্তিশালী রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত রাষ্ট্রের জনসাধারণের উপর নির্যাতন পরিচালিত হয়েছে; অসংখ্য নিরপরাধ ব্যক্তি খুন হয়েছে, অসংখ্য নারী বীভৎস উপায়ে হয়েছে ধর্ষিত। মানবতার এই লঙ্ঘনই বিশ্বজুড়ে মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ নামে পরিচিত।
ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্টের সংবিধি অনুসারে বলা হয়েছে যুদ্ধকালীন প্রেক্ষাপটে ধর্ষণ, যৌন নির্যাতন, শ্রমে বাধ্যকরা প্রভৃতি মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে নাৎসি বাহিনী কর্তৃক যে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত হয়, তার বিচারের জন্য বিশ্বে প্রথমবারের মতো বিচারিক আদালত নুরেমবার্গ ট্রায়াল গঠিত হয়।
নুরেমবার্গ ট্রায়ালে অভিযোগকারীরা বিচারের প্রয়োজনীয়তার প্রশ্নে এ কথাই বলেছিলেন যে, ভবিষ্যৎ নিরাপদ পৃথিবীর জন্যই যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার প্রয়োজন। এদের অপরাধের তালিকা করে এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে যে, ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের অপরাধ সংঘটনের কথা কেউই না ভাবে। বস্তুত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করাটাই একটি মানবিক অপরাধ; অন্যায়কারীকে সমর্থন দিয়ে আরও অপরাধ সংঘটনের সুযোগ করে দেয়ার নামান্তর।
বাংলাদেশে যখনই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা বলা হয়, তখনই একটি গোষ্ঠী তৎপর হয়ে ওঠে এই বলে যে — ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধাপরাধীদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। ফলে যারা রাষ্ট্রকর্তৃক পূর্বেই ক্ষমাপ্রাপ্ত, তাদের নতুন করে বিচারের প্রশ্নই ওঠে না। বস্তুত, যুদ্ধাপরাধীদের এই ক্ষমা করার বিষয়টি একটি ধোঁয়াশাপূর্ণ অসত্য প্রচারণা।
কেননা, ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। যার ধারাবাহিকতায় তিনি সে বছরই দেশীয় অপরাধীদের শান্তির আওতায় আনার জন্য ‘দালাল আইন-১৯৭২’ পবর্তন করেন। তাঁর শাসনামলেই পাকিস্তানি বাহিনীর ভেতরকার অপরাধীদের মধ্য থেকে গুরুত্বের বিচারে প্রায় পাঁচশত অপরাধীর একটি তালিকা করা হয়, যা পরবর্তীকালে কাটছাঁট করে দুশো জনে নামিয়ে আনা হয়।
কিন্তু পাকিস্তানি সেনাদের বিচারের ক্ষেত্রে ছিল আন্তর্জাতিক। এছাড়া তৎকালীন পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোও অনমনীয় মনোভাব পোষণ করে জানান – বাংলাদেশ সরকার যদি আত্মসমর্পণকৃত বিরানব্বই হাজার পাকিস্তানি সেনার একজনকেও যুদ্ধাপরাধের বিচারে শাস্তি প্রদান করে, তবে তিনি যুদ্ধকালীন সময়ে পাকিস্তানে আটকে পড়া পাঁচ লক্ষের অধিক বাঙালির একজনকেও ফেরত দেবেন না।
এছাড়া ছিল আন্তর্জাতিক বিশ্ব, বিশেষত ইসলামি বিশ্বের চাপ। এত কিছু সামলে নবগঠিত একটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষে সেসময় পাকিস্তানি অপরাধীদের বিচার করা সম্ভব হয়নি। তবে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সহযোগী এদেশীয় দালাল, রাজাকার, আলবদর, আলশামস, যারা প্রধানত জামায়েতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামী প্রভৃতি দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল, তাদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের বিচারের প্রয়োজনে ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসেই ‘দালাল আইন’ প্রণয়ন করা হয়। এবং এতে বলা হয় :
যে বা যারা ব্যক্তিগতভাবে অথবা সংগঠিতভাবে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, নারী পুরুষ শিশু নির্বিশেষে নির্যাতন, সম্পদহানি, ধ্বংসযজ্ঞে সমর্থন দিয়েছে বা সহযোহিতা করেছে বা নিজেরা এতে অংশগ্রহণ করেছে কিংবা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দখলদার বাহিনীর যুদ্ধ এবং তাদের অবৈধ দখলদারিত্বকে সমর্থন দিয়েছে, তাদের বিচারের জন্য এই নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।’
কিন্তু ‘দালাল আইন’ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বেশকিছু সমস্যা দেখা দিয়েছিল সে সময়। লোকস্বল্পতার কারণের অভিযুক্ত দালালদের বিরুদ্ধে তদন্ত করা যায়নি। থানার একজন ওসির পক্ষে নির্ধারিত দায়িত্ব পালনের পরও অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে এত সংখ্যক লোকের বিরুদ্ধে তদন্ত করে রিপোর্ট প্রদান অসম্ভব ছিল।
১৯৭২ সালের ২৩ জুলাই দৈনিক বাংলার বাণীর একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল দালাল আইন সম্পর্কে কিছু মন্তব্য রয়েছে আইন বিশেষজ্ঞদের। তাঁরা বলেছেন, দালাল আইন করা হয়েছে একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে সংঘটিত অপরাধের বিচার করার জন্য।
কাজেই সে অপরাধ প্রমাণের জন্যে থাকতে হবে সাক্ষ্য প্রমাণের বিশেষ ধরন। কিন্তু বর্তমান আইনে সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য অনুসরণ করতে হয় একশ বছরের পুরনো ‘এভিডেন্স এ্যাক্ট। এই এ্যাক্ট হয়েছে বিশেষ পরিস্থিতিতে সংঘটিত অপরাধের বিচারের জন্য। কাজেই বিশেষ পরিস্থিতির অপরাধ প্রমাণের জন্য প্রণীত এভিডেন্স অ্যাক্ট অনুসরণ করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে নানা জটিলতা। ফলে অপরাধ প্রমাণ করা হয়ে উঠছে অনেক ক্ষেত্রে দুঃসাধ্য।
এসব কারণে ৩০ নভেম্বর ১৯৭৩ সালে এক সরকারি প্রেসনোটের মাধ্যমে এই বিপুল সংখ্যক প্ৰমাণ না থাকা সাধারণ যুদ্ধাপরাধীকে সাধারণ ক্ষমাপ্রদান করা হয়। তবে পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধী ও তাদের প্রধান সহযোগী গোলাম আযমসহ অন্যান্য কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধীদের কখনোই ক্ষমা করা হয়নি।

পঁচাত্তর-পরবর্তীকালে সেনা-সমর্থিত সরকারগুলোর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে দেশে মানবতাবিরোধীদের বিচারের পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়। আইন করে নাগরিকত্ব প্রদান করা, দেশের রাজনীতিতে এমনকি নির্বাচনেও তাদের অংশগ্রহণ করার সুযোগ করে দেয়া হয়। চালু হয় ধর্মভিত্তিক রাজনীতি। এই সুযোগে একাত্তরের পরাজিত শক্তি ক্ষমতার কাছাকাছি যাবার সুযোগ পায়। সৈয়দ হক এ বিষয়টি তাঁর নাটকে উল্লেখ করতে ভোলেননি :
ক্ষমতার লোভে তারা
সেদিনের শত্রুদের যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার করেনি।
একাত্তর ভুলে গিয়ে ঘাতকের হাত তারা চুম্বন করেছে।
অপরাধ – রয়ে গেছে অপরাধ। অন্যায়, অন্যায়। (কাব্যনাট্যসমগ্র: ৬০২)
১৯৯১ সালের ২৮ ডিসেম্বর জামায়াতে ইসলামী তাদের সংগঠনের আমির হিসেবে অধ্যাপক গোলাম আজমের নাম ঘোষণা করে; যিনি স্বাধীনতার পর পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। গোলাম আজমকে আমির ঘোষণা করায় প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠন, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বিশেষ করে আওয়ামী লীগ ১৯৯২ সালের ৮ জানুয়ারি জাতীয় সংসদের অধিবেশনে গোলাম আজমের বহিষ্কার ও শাস্তি দাবি করে। উত্তরবংশ নাটকে সৈয়দ হক নাট্যকারের মেয়ে চরিত্রটির মাধ্যমে মৌলবাদী গোষ্ঠীর ক্রমশ এদেশে জেঁকে বসার চিত্র অত্যন্ত আক্ষেপের সঙ্গে তুলে ধরেছেন :
তোমরা ওদের বিচার না করে ভুল করেছিলে।
বিচার না করবার কারণেই ওরা সুযোগ পেয়ে যায় –
ফিরে আসে, ক্রমে মিশে যেতে থাকে সমাজে,
কিছুদিন মাথা নিচু করে থাকে – তারপর সংঘবদ্ধ হতে থাকে –
তারপর আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে – মদদ জোগায় ভ্রষ্ট রাষ্ট্রপতিরা,
–
প্রকাশ্যেই রাজনীতি শুরু করে – উত্থান ঘটে মৌলবাদের –
–
সশস্ত্র হামলা চলতে থাকে তোমাদেরই বিরুদ্ধে – তোমরা যারা
মানুষের জন্যে কলম ধরেছিলে, রাজনীতি করেছিলে। (কাব্যনাট্যসমগ্র: ৬০৪)
১৯৭১ সালের অনেক মুক্তিযোদ্ধা রাজনৈতিক কারণে বা ব্যক্তিস্বার্থে নীতিভ্রষ্ট হয়ে রাজাকার আলবদরের সাথে সখ্যভাব গড়ে তুলেছে। তবে একাত্তরের শহিদ পরিবার কিংবা নির্যাতিত পরিবারগুলোর মনে এদের প্রতি ছিল তীব্র ঘৃণা। যে কারণে শহীদ জননী জাহানারা ইমাম নতুন করে এই ঘাতক দালালদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন, এবং দেশের প্রগতিশীল ব্যক্তি, লেখক, বুদ্ধিজীবী শহীদ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে গঠন করেন ‘একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি’।
তৎকালীন প্রধান বিরোধীদল আওয়ামী লীগও এদের নীতিগত সমর্থন দেয়। ১০১ সদস্যের কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় যে, সোহরাওয়ার্দী ময়দানে গোলাম আজমসহ একাত্তরের মানবতাবিরোধীদের বিপক্ষে গণ আদালত প্রতিষ্ঠা করা হবে। সৈয়দ শামসুল হকও উক্ত আদালতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সে-সময়ের স্মৃতিচারণ করে এক লেখায় বলেন :
আলোচনার পরে স্থির হলো, গণ-আদালতে অভিযোগকারী হবো আমরা তিনজন : বাঙালি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে গোলাম আযমের ভূমিকা সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করবেন সৈয়দ শামসুল হক; মুক্তিযুদ্ধকালে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করবে বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর; আর বাংলাদেশ-প্রতিষ্ঠার পর পৃথিবীর নানাদেশে তাঁর বাংলাদেশবিরোধী ভূমিকা সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করবো আমি। গণ-আদালতে গোলাম আযমের বিচার হবে – এমন একটি সংবাদ ছড়িয়ে পড়ামাত্র মানুষের অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেল।’
নব্বইয়ের দশকে মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচারের এ আন্দোলন প্রসঙ্গে ইঙ্গিত রয়েছে আলোচ্য নাটকে। নেতার প্রতি অভিযোগ করে নাট্যকার চরিত্রটি যখন বলে – আমাদের কবিতা রাজনীতির মঞ্চে ব্যবহার করে তোমরা রাষ্ট্রক্ষমতায় পৌঁছে যাও; কিন্তু ক্ষমতায় বসেই আমেেদর ভুলে যাও তোমরা। যেহেতু আলোচ্য নাটকের নেতা চরিত্রটি একটি সৎ, কর্মপরায়ণ ও নীতিনিষ্ঠ চরিত্র, সেহেতু তিনি রাজনীতিতে শিল্পী-কবি- সাহিত্যিকের অবদান অনায়াসে স্বীকার করেছেন।
এ পর্যায়ে আলাপ প্রসঙ্গে তিনি মানবতাবিরোধী অপরাধ আন্দোলনের ইতিহাস টেনে বলেছেন, সাধারণ মানুষ যখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চেয়ে আন্দোলনের মাঠে নেমেছে, তখন তাদের দল সাগ্রহে এ নৈতিক দাবির পক্ষে সমর্থন জানিয়েছে। কিন্তু সেসময়ে ক্ষমতাসীন দলের বিরোধিতার কারণে বিচারপ্রক্রিয়া অগ্রসর হয়নি। তবে তিনি অত্যন্ত আশাবাদী যে, বাংলার মাটিতে একদিন দেশদ্রোহী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে। নেতার বলিষ্ঠ উচ্চারণ :
বিশেষ করে যখন যুদ্ধপরাধীদের বিচার চেয়ে
রমনার সবুজ বিশাল মাঠে তোমরা দাঁড়ালে – তখন
রাজনীতির মাঠে আমরাও জোরেশোরে সমর্থন দিয়েছি।
তখনই যদি – তখনই যদি বিচারটা শুরু করা যেতো,
তবে কবেই উদ্যত ওদের হাত গুঁড়ো হয়ে যেতো। …..
হাওয়া লেগেছিলো পালে, মাস্তুলে উড়ছিলো নিশান।
মনে পড়ে তোমার সেদিনের সেই কবিতা।
একাত্তরের যুদ্ধে আমার অস্ত্র হাতে ছিলো –
এবার হাতে অস্ত্র আমার সত্য প্রতিষ্ঠার –
যাদের হাত আমার দেশের রক্তে ভিজেছিলো –
কাঠগড়াতে তুলবো তাদের দণ্ড দেবো তার।’ (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৮৫)
এরপর নাট্যকার চরিত্রটিও স্বপ্ন দেখছেন, একজন দেশনেতা এসে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার প্রক্রিয়া ও আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবেন। সে আলো-ঝলমল নেতৃত্বের প্রত্যাশা করে তিনি বলেছেন :
মন্থনে মন্থনে জাগিয়ে তোলো চেতনা। জন্ম দাও নেতা।
রাতের আঁধার ভেঙে জন্ম নিক সূর্যের মতো সে মানুষ। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৬০৩)
তখন নাট্যকারের মেয়ে উত্তরবংশের প্রতিনিধি হয়ে তাদের আশ্বস্ত করেছে এই বলে যে, একদিন পূর্বপ্রজন্ম যে বিচার করতে পারেনি উত্তরপ্রজন্ম সেই বিচার অবশ্যই সম্পন্ন করবে। সে শপথ করে বলেছে :
তোমরা শান্ত হও, শান্ত হও, হে অশান্ত আত্মা,
আমার মা, আমার বোন, আমার ভাই, আমার পূর্বপুরুষেরা,
আমি উত্তরবংশের মেয়ে, আমরাই করবো বিচার।
বাবা, আমি তোমার উত্তরপ্রজন্ম – তোমরা যেখানে ব্যর্থ,
আমরা সেখানে হতে চাই সফল। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৬০৫)
যারা ১৯৭১ সালের দেশ স্বাধীন হবার প্রাকপর্যায়ে বেছে বেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাংবাদিক, শিক্ষক, সাহিত্যিকদের রাতের আঁধারে নিজ বাসভবন থেকে চোখ বেঁধে তুলে নিয়ে নির্মম অত্যাচার করে হত্যা করেছিল, তারাই পঁচাত্তর-উত্তর সময়ে ধর্মীয় মৌলবাদের ক্রম-উত্থানের সুযোগে পুনর্বার প্রগতিশীল লেখক, কলামিস্ট, বুদ্ধিজীবীদের হত্যার মিশনে নেমেছে।
এদেশের বুক থেকে চিরতরে মুক্তবুদ্ধি চর্চার পথ রুদ্ধ করতে তারা জঙ্গিবাদি তৎপরতা নিয়ে মাঠে নেমেছে, আদালতে বোমা হামলা চালিয়েছে, নিষ্ঠুর কায়দায় প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিকদের হত্যার মিশনে নেমেছে। সৈয়দ হক লেখক-বুদ্ধিজীবীদের ওপর এই জঙ্গিবাদী তৎপরতার তুলনা করেছেন ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বরের বুদ্ধিজীবী হত্যার সঙ্গে :
কখন ওরা কলমটা আমার কেড়ে নেয়।
কখন ফুসফুস থেকে কেড়ে নেয় নিঃশ্বাস।
কখন কব্জি কেটে দেয়, কখন চোখ উপড়ে নেয়।
আমাদের সেই বিজয়ের মাত্র, দু’দিন আগে যেমন –
বাড়ি থেকে না তুলে নেয় আমাকে, চোখে কাপড় বেঁধে দেয়,
জীপের পাটাতনে না আমার মাথা ঠেসে ধরে চেপে নিয়ে যায় –
বধ্যভূমিতে। তারপর – তোকে না একদিন যেতে হয় লাশ খুঁজতে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৬১)
সমকালীন রাষ্ট্রিক ব্যবস্থায় মুক্তবুদ্ধিচর্চাকে কীভাবে দমিয়ে রাখা হয়েছে, কীভাবে ধর্মকে ব্যবহার করে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করা হয়েছে, সেটিও নাট্যকার সমান দক্ষতায় উপস্থাপন করেছেন আলোচ্য নাটকে। তিনি দেখেছেন, সমকালীন মূলধারার পত্রিকাগুলো কীভাবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সরকারের মৌলবাদপ্রীতি বাস্তবায়ন করতো, অথবা সরকারের তাবৎ অন্যায় ঢেকে মিথ্যে প্রশংসা করতে বাধ্য হতো।

কোনো লেখক যদি সরকারের নীতি-বিরোধী, জনকল্যাণকর লেখা পত্রিকায় প্রকাশ করতে চাইতো – তবে তা প্রচুর সম্পাদনার পর প্রকাশের ব্যবস্থা হতো।
নাট্যকার যেটিকে বলেছেন ইঁদুরের দাঁতেকাটা ক্ষত-বিক্ষত রচনা। বস্তুত, ২০০১ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক জনকন্ঠসহ একাধিক পত্রিকা সরকারের রোষানলে ছিল। তুচ্ছ কারণে পত্রিকার সম্পাদকদের ডেকে নিয়ে মামলা হামলার ভয় প্রদান করা হতো; অজ্ঞাত অবস্থান থেকে লেখকদের দেয়া হতো প্রাণনাশের হুমকি। সৈয়দ শামসুল হক এসব বিষয় তুলে ধরেছেন নাট্যকার চরিত্রটির নিম্নোক্ত সংলাপে :
রাজনীতি থেকে কেন ধর্ম আলাদা রাখা দরকার –
কেন ধার্মিক আর ধর্মব্যবসায়ীদের ভেতরে তফাত করা চাই –
[…] এ সব যে লিখেছিলাম স্বাধীনতা দিবসের জন্যে আমি এক প্রবন্ধে –
আমাদের পত্রিকার প্রগতিশীল আর নির্ভিক সেই সম্পাদক –
আমার লেখাটা তিনি এতখানি কেটেকুটে ছাপলেন –
[…] তাঁর হাতে আমার লেখাটা হয়ে দাঁড়ালো ইঁদুরের দাঁতে কাটা।
সম্পাদকের প্রাণ ও তাঁর পত্রিকা বাঁচলো বটে – আপাতত ।
কিন্তু সত্যের ও রাষ্ট্রের ক্রন্দন কেউ শুনতে পেলো না ।
[…] আসতে লাগলো আমার কাছে ফোন- মধ্যরাতে হঠাৎ ঝনঝন –
অনামা গলা – কর্কশ উচ্চারণ পাঠাচ্ছি কাফন ! (কাব্যনাট্যসমগ্র: ৫৬২)
পঁচাত্তর-উত্তর সময়ের সেনাশাসিত সরকার কিংবা মৌলবাদ-সমর্থিত সরকারের শাসনামলে মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন চরমভাবে অবহেলিত। প্রগতিশীল রাজনীতিবিদরা ছিলেন অসহায়। সেই বঞ্চনাময় অসহায়তার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে নাট্যকারের মেয়ের সংলাপে :
দেশ-মানুষের পক্ষে এতকাল যারা করেছে রাজনীতি
মুক্তিযুদ্ধে ছিলো সম্মুখের সারিতে যারা –
তারাই যে ক্রমে এখন হয়ে পড়েছে কোণঠাসা! (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৬৪)
যেসব রাজনীতিবিদ দেশের পরিবর্তে আত্মস্বার্থকে বড়ো করে দেখেন, তারাই সমকালীন রাজনীতির মাঠে দাপটের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত। এসব রাজনীতিবিদ মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানকে আড়াল করে স্বার্থোদ্ধারে মগ্ন। এদের পৃষ্ঠপোষকতায় দিনের পর দিন তোষামুদে লেখকেরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করেছে। এই ইতিহাসবিকৃতি প্রসঙ্গে ড. মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী এক নিবন্ধে লিখেছেন :
যেহেতু বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিকাংশ সময়ই মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দলের চাইতে সামরিক, আধা- সামরিক ও তাদের প্রতিষ্ঠিত দলই বেশি সময় অধিষ্ঠিত ছিল, তাই এ সব সরকার মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে বাদ দিয়ে কোনো কোনো ব্যক্তির ভূমিকাকে প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করেছে। ফলে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক স্তরেও যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয়নি।
[…] ১৯৯৬ সালে পাঠ্যপুস্তকসমূহে এ সংক্রান্ত ত্রুটি যেটুকু সংশোধন করা হয়েছিলো ২০০১ সালে তা শুধু বাতিলই করা হয়নি, প্রাথমিক স্তরের বেশকিছু পাঠ্যপুস্তকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার জনগণ ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের আন্দোলন ও ভূমিকাকে ইচ্ছেমতো লেখা হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট, প্রধান ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্বের ভূমিকাকে গুরুত্বহীনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে ।
সৈয়দ হক তাঁর উত্তরবংশ নাটকে এই ইতিহাসবিকৃতির প্রসঙ্গটি উপস্থাপন করতে ভোলেননি। তিনি নাট্যকার চরিত্রটির মাধ্যমে বলেছেন:
হত্যার মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে একদা পরাজিত ওই ওরা
ইতিহাসকে ওদের পক্ষে লিখিয়েছে – বীরকে স্থবির দেখিয়েছে,
কলমকে ছিন্ন করেছে তলোয়ারে, মুক্তিকে দাসত্ব বলেছে,
আমাদের হাজার বছরের পরিচয় নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে ওরা –
জাতির গায়ে ভুল মার্কা ও নতুন লেবেল সেঁটে দিয়েছে।
[…] নতুন প্রজন্ম বেড়ে উঠেছে আবৃত ইতিহাসের অন্ধকারে।
বিকৃত ইতিহাস আর ধর্মলোপের জুজু যখন জাপটে ধরে জাতিকে –
তখন বিশ্লেষণ করবার অবকাশ আর মানুষ পাবে কী করে ? (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৯৬)
নাট্যকার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতির এই নিদারুণ বাস্তবতা উপস্থাপনের পাশাপাশি প্রগতিশীল রাজনীতিকদের প্রতিবাদী সত্তায় আত্মপ্রকাশের আহবান জানিয়েছেন, এবং প্রগতিশীল লেখক-কলামিস্ট- বুদ্ধিজীবীদের আহ্বান করেছেন দেশ, মানুষ ও মুক্তিযুদ্ধের বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস রচনার
এমন রাজনীতিও দেশে আছে দেশ বা মানুষ যার লক্ষ্য নয় –
ইতিহাস তাদের বিষয় নয়।
সেই ইতিহাসটা কতভাবেই না বিকৃত করে চলেছে
ওই ভ্রষ্ট রাজনীতিকের দল।
আজ তাদেরই বিপরীতে সক্রিয় হতে হবে আমাদের –
দেশটাকে বাঁচাবার স্বার্থে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৬৫)
আবার, ২১শে আগস্ট ২০০৪ সালে তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার ওপর গ্রেনেড হামলাসহ অন্যান্য হামলার প্রসঙ্গ একটি মঞ্চনির্দেশনার মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার। নাটকের অষ্টম দৃশ্যটি রচিত হয়েছে কেবল গ্রেনেড হামলার বাস্তবচিত্রসংবলিত মঞ্চনির্দেশের ওপর ভিত্তি করে :
অবিলম্বে শূন্য মঞ্চস্থানে বিপরীত মানুষেরা আসে। এবার তাদের টানটান শাদা জামা পাজামা। মুখের অর্ধেকটা কালো কাপড়ে ঢাকা। তারা নিঃশব্দে সতর্ক পায়ে আসে। এদিক ওদিক তাকিয়ে কোমর থেকে গ্রেনেড হাতে নিয়ে তাক করে ছুঁড়ে মারে। এবং মুহূর্তে পালিয়ে যায়। মঞ্চে বিস্ফোরণ ঘটে। তীব্র আলোর ঝলকানি। তারপর আলো নিভে যায়। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৭৪)
বস্তুত, বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামোয় অবৈধ উপায়ে দীর্ঘকালব্যাপী সমাসীন সমরশাসন, এবং মৌলবাদ-সমর্থিত জোট সরকারের আমলে যে মাৎস্যানায়ের রাজত্ব চলছিল, যে কালাকানুন প্রগতির পথ রুদ্ধ করে রেখেছিল, লুপ্ত হতে চলেছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, তা উত্তরপ্রজন্মকে জানানোই শুধু নয়, তার ন্যায্য প্রতিকারের প্রয়োজন থেকেই রচিত হয়েছে উত্তরবংশ নাটক।
একদিন উত্তরপ্রজন্ম প্রতিক্রিয়াশীলতার তিমির হনন করে এ জাতিকে আলোর মুখ দেখাবে; বিচার হবে যুদ্ধাপরাধীর, বিচার হবে পঁচাত্তরের ঘাতকদের, গ্রেনেড হামলার। নাট্যকারের প্রত্যাশা – জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প সরিয়ে উত্তরপ্রজন্ম বাংলাদেশ নামক এই বদ্বীপকে মুক্ত ও শুদ্ধ – করতে নিশ্চয়ই সক্ষম হবে।